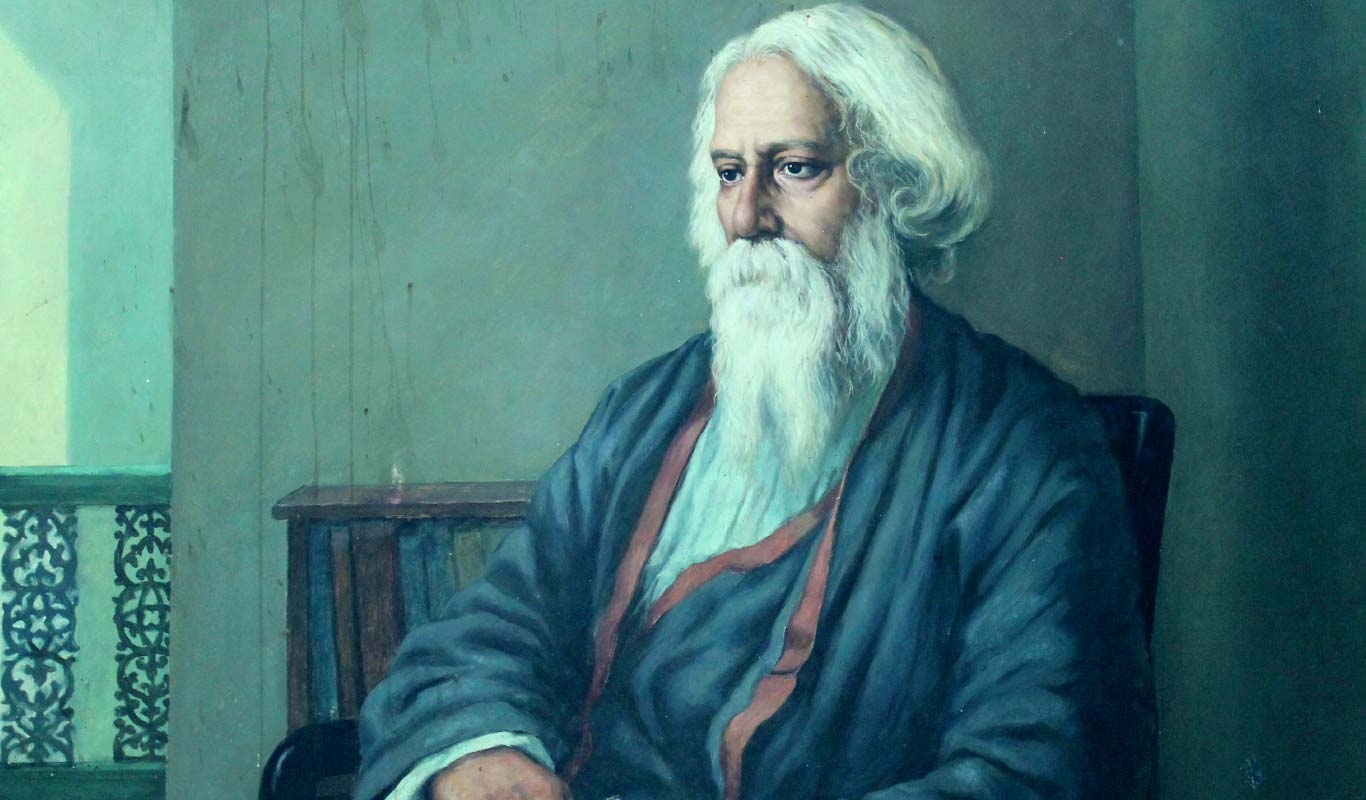Ó”óÓ”ŠÓ”ĢÓ”Š Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”¼Ó”¼Ó”┐Ó””Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓Ó¦¤ Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć ŌĆśÓ”«Ó¦ŗÓ”╣Ó”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”«Ó”” Ó”«Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦üÓ”£Ó¦ŹÓ”£Ó”«Ó”ŠÓ”© Ó”ĖÓ¦ŹÓ”«Ó”ŠÓ”░Ó”Ģ Ó”¼Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ¦āÓ”żÓ”ŠŌĆÖ Ó””Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”ĪÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”¬Ó”░Ó¦ć Ó”£Ó¦ćÓ”©Ó¦ćÓ”øÓ”┐ Ó”ÅÓ”ć Ó”¼Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ¦āÓ”żÓ”Š Ó”Å-Ó”¼Ó”øÓ”░Ó”ć Ó”ČÓ¦üÓ”░Ó¦ü Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć Ó”ō Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĘÓ”┐Ó”Ģ Ó”¼Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ¦āÓ”żÓ”ŠÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”« Ó”¼Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”Š Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ćÓ”ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░Ó”Š Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”ĪÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż
Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”£Ó”ŠÓ”©Ó”┐ Ó”ÅÓ”ć Ó”¦Ó”░Ó”ŻÓ¦ćÓ”░ Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ćÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ćÓ”øÓ”©Ó¦ć Ó”ÅÓ”ć Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”ĢÓ”░Ó¦ŹÓ”«Ó”ĖÓ¦éÓ”ÜÓ”┐ Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”ÜÓ”ĢÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ČÓ”Š Ó”ĢÓ”ŠÓ”£ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓźż Ó”©Ó”ŠÓ”©Ó”Š Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”ŁÓ¦ćÓ”¼Ó¦ćÓ”ÜÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ćÓ”ć Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”«Ó”ż Ó”¼Ó”┐Ó”░Ó¦ŗÓ”¦Ó”┐Ó”żÓ”Š Ó”ēÓ¦ÄÓ”░Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”░Ó”Š Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”ĖÓ”┐Ó””Ó¦ŹÓ”¦Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ć Ó”¬Ó¦īÓ”üÓ”øÓ”©Óźż Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░ Ó”ÅÓ”« Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”¼Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ¦āÓ”żÓ”ŠÓ”ĖÓ¦éÓ”ÜÓ”┐ Ó”ČÓ¦üÓ”░Ó¦ü Ó”ĢÓ”░Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤ Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”ÜÓ”ĢÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ČÓ”ŠÓ¦¤ Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”Ģ Ó”¤Ó”ŠÓ”¤Ó”ĢÓ”Š Ó”«Ó”żÓ”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”źÓ”ĢÓ¦ŹÓ”»Ó”ō Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć, Ó”żÓ¦ĆÓ”¼Ó¦ŹÓ”░ Ó”«Ó”żÓ¦łÓ”ĢÓ¦ŹÓ”»Ó”ō Ó”ŚÓ¦£Ó¦ć Ó”ēÓ”ĀÓ¦ć Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”ģÓ”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ””Ó”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”¤ Ó”ŁÓ”░Ó”ĖÓ”Š Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ćÓźż
Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”óÓ”ŠÓ”ĢÓ”Š Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”¼Ó”¼Ó”┐Ó””Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓Ó¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”źÓ”«Ó”┐Ó”Ģ Ó”©Ó”┐Ó”«Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó”Ż Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”©Ó”Š Ó”ŁÓ¦ćÓ”¼Ó¦ćÓ”ć Ó”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”╣Ó”Ż Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”½Ó¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”øÓ”┐, Ó”»Ó¦ćÓ”╣Ó¦ćÓ”żÓ¦ü Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”Č Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”┐Ó”ż Ó”»Ó¦ć-Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó¦ćÓ”ć Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”ēÓ¦ÄÓ”ĖÓ”ŠÓ”╣ Ó”åÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”ĢÓźż Ó”¬Ó”░Ó¦ć Ó”»Ó”¢Ó”© Ó”£Ó”ŠÓ”©Ó”▓Ó”ŠÓ”« Ó”ÅÓ”¤Ó”ŠÓ”ć Ó”╣Ó”¼Ó¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”« ŌĆśÓ”«Ó¦ŗÓ”╣Ó”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”«Ó”” Ó”«Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦üÓ”£Ó¦ŹÓ”£Ó”ŠÓ”«Ó”ŠÓ”© Ó”ĖÓ¦ŹÓ”«Ó”ŠÓ”░Ó”ĢÓ”¼Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ¦āÓ”żÓ”ŠŌĆÖ, Ó”żÓ”¢Ó”©Ó”ć Ó”ŁÓ¦ćÓ”¼Ó¦ćÓ”øÓ”┐ Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”żÓ¦ÄÓ”¬Ó”░ Ó”░Ó”ŠÓ”£Ó”┐ Ó”╣Ó”ōÓ¦¤Ó”ŠÓ”¤Ó”Š Ó”ĀÓ”┐Ó”Ģ Ó”╣Ó¦¤Ó”©Ó”┐ Ó”¼Ó¦ŗÓ”¦ Ó”╣Ó¦¤Óźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”¼Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ¦āÓ”żÓ”ŠÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ¦üÓ”żÓ”┐Ó”░ Ó”£Ó”©Ó¦ŹÓ”» Ó”«Ó¦ŗÓ”╣Ó”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”«Ó”” Ó”«Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦üÓ”£Ó¦ŹÓ”£Ó”ŠÓ”«Ó”ŠÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”©Ó”┐Ó”£Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”¬Ó¦£Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó¦£Ó”żÓ¦ć Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”©Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó”ż Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ŚÓ¦ćÓ”▓Ó”ŠÓ”« Ó”»Ó¦ć, Ó”¬Ó”ŠÓ”▓Ó”ŠÓ”©Ó¦ŗ Ó”øÓ”ŠÓ¦£Ó”Š Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”ŠÓ”üÓ”ÜÓ”ŠÓ”░ Ó”¬Ó”ź Ó”©Ó¦ćÓ”ć Ó”ģÓ”źÓ”Ü Ó”¬Ó”ŠÓ”▓Ó”ŠÓ”©Ó¦ŗÓ”░ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”© Ó”¬Ó”ź Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó”©Ó¦ć-Ó”¬Ó¦ćÓ”øÓ”©Ó¦ć-Ó”¬Ó”ŠÓ”ČÓ¦ć Ó”ÜÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ¦üÓ”Ę Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ČÓ¦üÓ”░Ó¦üÓ”żÓ¦ćÓ”ć Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”¤Ó”Š Ó”¼Ó”▓Ó”żÓ¦ć Ó”ÜÓ”ŠÓ”ć Ó”«Ó¦ŗÓ”╣Ó”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”«Ó”” Ó”«Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦üÓ”£Ó¦ŹÓ”£Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó”ć Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ¦āÓ”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ÅÓ”ć Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó”¤Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”ĢÓ¦Ć Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”¬Ó¦īÓ”üÓ”øÓ¦ć Ó””Ó”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©Óźż
Ó”©Ó”Š, Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”┐ Ó”¼Ó”Š Ó”ŚÓ”¼Ó¦ćÓ”ĘÓ”ŻÓ”Š Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ĖÓ”éÓ”ĢÓ¦ćÓ”ż Ó”¬Ó”ŠÓ”ćÓ”©Ó”┐, Ó”»Ó””Ó”┐Ó”ō Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”»Ó¦ć Ó”żÓ”źÓ¦ŹÓ”»Ó”©Ó”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”Š Ó”ō Ó”ĖÓ”┐Ó””Ó¦ŹÓ”¦Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ćÓ”░ Ó”½Ó”▓Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĖÓ¦é Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”©Ó”ŠÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”«Ó”ŠÓ”Ż Ó”åÓ”øÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”ĢÓ¦ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”£Ó”© Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”åÓ””Ó”░Ó¦ŹÓ”Č Ó”ŚÓ”¼Ó¦ćÓ”ĘÓ”Ģ Ó”¼Ó”▓Ó¦ć Ó”ĖÓ”╣Ó”£Ó¦ćÓ”ć Ó”«Ó”©Ó¦ć Ó”╣Ó”¼Ó¦ć Ó”»Ó¦ć-Ó”åÓ””Ó”░Ó¦ŹÓ”Č Ó”ŚÓ”¼Ó¦ćÓ”ĘÓ”Ģ Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”ĖÓ”¼ Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”ć Ó””Ó¦üÓ”░Ó¦ŹÓ”▓Ó”ŁÓźż Ó”ŚÓ”¼Ó¦ćÓ”ĘÓ”ŻÓ”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”åÓ””Ó”░Ó¦ŹÓ”Č Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”Č Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”Š Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”¼Ó¦£Ó”ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦¤Ó¦ŗÓ”£Ó”© Ó”øÓ”┐Ó”▓ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ēÓ””Ó¦ŹÓ”»Ó”«Óźż Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”░Óźż Ó”¼Ó¦£Ó”ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦¤Ó¦ŗÓ”£Ó”© Ó”øÓ”┐Ó”▓ Ó”ŚÓ”¼Ó¦ćÓ”ĘÓ”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”©Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¬Ó¦āÓ”╣Ó”żÓ”ŠÓźż Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ŚÓ”¼Ó¦ćÓ”ĘÓ”ŻÓ”Š Ó”øÓ”┐Ó”▓ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó””Ó”░Ó¦ŹÓ”ČÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”░Ó¦ŹÓ”ŚÓ”żÓźż Ó”żÓ”ŠÓ”ć Ó”żÓ¦ŗ Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”Š Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”Š Ó”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”¼Ó”ĢÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ŚÓ”¼Ó¦ćÓ”ĘÓ”ŻÓ”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤ Ó”╣Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ””Ó”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”¤ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ÜÓ”┐Ó”╣Ó¦ŹÓ”©Ó”┐Ó”ż Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤ Ó”©Ó”ŠÓźż
Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤ Ó”ÜÓ”┐Ó”╣Ó¦ŹÓ”©Ó”┐Ó”żÓźż Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”»Ó¦ćÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”źÓ”«Ó”┐Ó”Ģ Ó”ČÓ”░Ó¦ŹÓ”ż- Ó”øÓ”©Ó¦ŹÓ””, Ó”ēÓ”¬Ó”«Ó”ŠÓ””Ó”┐, Ó”ģÓ”▓Ó”éÓ”ĢÓ”ŠÓ”░, Ó”ÜÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬ Ó”ō Ó”¤Ó”┐.Ó”ÅÓ”Ė.Ó”ÅÓ”▓Ó”┐Ó¦¤Ó”¤ Ó”»Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”© Ó”ćÓ”ēÓ”©Ó”┐Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖÓ”ŠÓ”▓Ó”ŠÓ”ćÓ”£Ó¦ćÓ”ČÓ”©, Ó”ĖÓ¦ć Ó”ĖÓ”¼ Ó”ŚÓ¦üÓ”Ż Ó”åÓ¦¤Ó”żÓ¦ŹÓ”ż Ó”ĢÓ”░Ó”ŠÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”«Ó”ŠÓ”Ż Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ¦¤ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¬Ó”ĘÓ¦ŹÓ”¤Óźż Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”Š Ó”żÓ¦ŗ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”«Ó”ż Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”ĖÓ”«Ó¦¤Ó”ĖÓ¦ŹÓ”░Ó¦ŗÓ”żÓ¦ćÓ”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░ Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”¼Ó”▓Ó”ŠÓźż Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”ćÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ”┐Ó”ż Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć, Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”śÓ¦üÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó”▓Ó”Š Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć, Ó”»Ó¦ćÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”ōÓ”ć Ó”ĖÓ”«Ó¦¤Ó”ĖÓ¦ŹÓ”░Ó¦ŗÓ”żÓ¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”┐Ó”ż Ó”¬Ó”ŠÓ”ĀÓ”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”øÓ¦ćÓ”ć Ó”ĢÓ¦ćÓ”¼Ó”▓ Ó”©Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ¦¤Ó”żÓ”Š Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”¬Ó¦ćÓ¦ŚÓ”üÓ”øÓ¦¤Óźż Ó”¼Ó”╣Ó¦ü Ó”ĖÓ”«Ó¦¤ Ó”¼Ó¦¤Ó¦ć Ó”ŚÓ¦ćÓ”▓Ó¦ć Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ģÓ”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦¤Ó¦ŗÓ”£Ó”© Ó”åÓ”░ Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”«Ó¦ŗÓ”╣Ó”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”«Ó”” Ó”«Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦üÓ”£Ó¦ŹÓ”£Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░ Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”żÓ”żÓ”¤Ó”Š Ó”ĖÓ”«Ó¦¤ Ó”ÅÓ”¢Ó”©Ó”ō Ó”¼Ó¦¤Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ¦¤Ó”©Ó”┐, Ó”»Ó”Š Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”«Ó”ż Ó””Ó¦éÓ”░Ó”¼Ó”░Ó¦ŹÓ”żÓ¦Ć Ó”¼Ó”┐Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦Ć Ó”¬Ó”ŠÓ”ĀÓ”ĢÓ”ĢÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”©Ó¦ŹÓ”¦Ó”ŠÓ”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”Š Ó”¼Ó¦üÓ”ØÓ”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó””Ó¦ćÓ¦¤Óźż Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”Š Ó”żÓ¦ŗ Ó”ĖÓ”©Ó¦ŹÓ”¦Ó”ŠÓ”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”ŠÓ”żÓ¦ćÓ”ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Óźż Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐, Ó”»Ó”Š Ó”¬Ó¦£Ó¦ćÓ”øÓ”┐, Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”åÓ”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”¤ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”ĖÓ¦ć Ó”åÓ”¼Ó¦ćÓ”Č Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ćÓ”ō Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ŁÓ¦éÓ”«Ó”┐ Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”¬Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ¦ć Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”żÓ¦ŗÓ”▓Ó”Š Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”ŁÓ”¼ Ó”╣Ó¦¤Ó”©Ó”┐ Ó”»Ó”ŠÓ”░ Ó”¼Ó¦ćÓ”¦ Ó”åÓ”øÓ¦ć, Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”åÓ”øÓ¦ć, Ó”żÓ”▓Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ć Ó”åÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”¼Ó¦ćÓ”¦-Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė-Ó”żÓ”▓ Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”åÓ”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó”┐Ó”©Ó”┐ Ó”ÅÓ”ĢÓ”«Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”ÅÓ”ć Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”ŻÓ¦ć Ó”»Ó¦ć, Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”Š Ó”ĖÓ”¼ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤Ó”ć Ó””Ó¦üÓ”░Ó¦ŹÓ”ŚÓ”« Ó”ō Ó””Ó¦üÓ”░Ó¦éÓ”╣Óźż
Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”ŚÓ”ŠÓ”© Ó”øÓ”ŠÓ”¬Ó”ŠÓ”░ Ó”╣Ó”░Ó”½Ó¦ć Ó”¬Ó¦£Ó¦ćÓ”øÓ”┐- Ó”ĖÓ¦üÓ”░Ó”╣Ó¦ĆÓ”©Óźż Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”ŚÓ”ŠÓ”© Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”ŁÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”åÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó¦Ć ŌĆśÓ”ĖÓ¦ŹÓ”«Ó¦āÓ”żÓ”┐ Ó”»Ó¦ć Ó”ģÓ”ÜÓ”×Ó¦ŹÓ”ÜÓ”▓Ó”ŠŌĆÖ-Ó”żÓ¦ć Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”¢Ó¦üÓ”¼ Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ””Ó¦ć Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”©Ó”©Ó”┐, Ó”¢Ó¦üÓ”¼ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¬Ó”ĘÓ¦ŹÓ”¤ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”ō Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”©Ó”©Ó”┐, Ó”ČÓ¦üÓ”¦Ó¦ü Ó”ēÓ”▓Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ćÓ”¢ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”ŚÓ¦ĆÓ”żÓ”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”╣Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”©Ó”ŠÓ”« Ó”ō Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”«Ó¦üÓ”¢ Ó”¬Ó”ŠÓ”Ģ-Ó”¼Ó”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”©Ó¦ĆÓ”░ Ó”╣Ó”ŠÓ”ż Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”åÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”░Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”ĢÓ¦ćÓ”«Ó”© Ó”ĢÓ”ĀÓ”┐Ó”© Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”żÓ¦üÓ”▓Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Óźż
Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”żÓ¦ŗ Ó”ĖÓ”ŠÓ”░Ó”ŠÓ”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”© Ó”ČÓ¦üÓ”¦Ó¦ü Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬-Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”ć Ó”¼Ó”ŠÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ”┐Óźż Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬-Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”¼Ó”ŠÓ”©Ó”ŠÓ”©Ó¦ŗÓ”░ Ó”ÅÓ”ć Ó”ÅÓ”Ģ Ó”«Ó”£Ó”Š Ó”»Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”øÓ¦üÓ”żÓ¦ŗ Ó”¦Ó”░Ó¦ć Ó”ģÓ”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”¼Ó¦ćÓ”░, Ó”¼Ó”Š, Ó”¼Ó”▓Ó”Š Ó”ŁÓ”ŠÓ”▓, Ó”ģÓ”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”«Ó”ŠÓ”ŻÓ”┐Ó”żÓ¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”£Ó”ŚÓ¦Ä Ó”¼Ó”ŠÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”żÓ¦üÓ”▓Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ÜÓ”ŠÓ”ćÓ”żÓ¦ćÓ”ō Ó”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”¼Ó”żÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”«Ó”ŠÓ”Ż Ó”ĢÓ”░Ó”ŠÓźż
Ó”«Ó¦ŗÓ”╣Ó”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”«Ó”” Ó”«Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦üÓ”£Ó¦ŹÓ”£Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”óÓ”ŠÓ”ĢÓ”ŠÓ¦¤ Ó”åÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”ŚÓ¦ŗÓ”¬Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”śÓ”¤Ó”©Ó”Š Ó”¬Ó¦£Ó”żÓ¦ć-Ó”¬Ó¦£Ó”żÓ¦ć Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”«Ó”©Ó¦ć Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓- Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”ĢÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”©Ó”┐Ó”£Ó¦ćÓ”░Ó”ć Ó”ĢÓ”ŠÓ”ø Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŗÓ”żÓ¦ć Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”»Ó¦ćÓ”╣Ó¦ćÓ”żÓ¦ü Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”«Ó¦üÓ”¢ Ó”¼Ó”╣Ó¦üÓ””Ó¦āÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤, Ó”»Ó¦ćÓ”╣Ó¦ćÓ”żÓ¦ü Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”ŚÓ”ŠÓ”© Ó”¼Ó”╣Ó¦üÓ”ŚÓ¦ĆÓ”ż Ó”ō Ó”»Ó¦ćÓ”╣Ó¦ćÓ”żÓ¦ü Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”©Ó”ŠÓ”« Ó”¼Ó”╣Ó¦üÓ”ČÓ¦ŹÓ”░Ó¦üÓ”ż Ó”żÓ”ŠÓ”ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”åÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”ŚÓ¦ŗÓ”¬Ó”© Ó”ÅÓ”ż Ó”ĢÓ”ĀÓ”┐Ó”©Óźż Ó”ÅÓ”¤Ó”ŠÓ”ć, Ó”ÅÓ”ć Ó”ĖÓ”éÓ”ĢÓ”¤Ó”¤Ó”ŠÓ”ć Ó”żÓ¦ŗ Ó”╣Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”ÅÓ”¢Ó”©Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė, Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ģÓ”▓Ó”┐Ó”¢Ó”┐Ó”ż Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”©Ó”ŠÓ¦¤Ó”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó”»Ó”ŠÓ”¬Ó”© Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”«Ó¦ŗÓ”╣Ó”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”«Ó”” Ó”«Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦üÓ”£Ó¦ŹÓ”£Ó”«Ó”ŠÓ”© Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”åÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”╣Ó¦ŗÓ””Ó”░ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ēÓ”ĀÓ”▓Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”£Ó¦ŹÓ”¼Ó”░Ó¦ŗ Ó”øÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”£Ó¦ŹÓ”¼Ó”░ Ó””Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”ŠÓ¦¤ Ó”©Ó¦ćÓ”ć Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”Ż Ó”żÓ”ŠÓ”╣Ó”▓Ó¦ć Ó”åÓ”▓Ó¦ŗ Ó”£Ó¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”▓Ó”żÓ¦ć Ó”╣Ó”¼Ó¦ćÓźż Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”░Ó¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”ĢÓ”½Ó¦īÓ”£Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó”ŠÓ¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ”ōÓ¦¤Ó”ŠÓ”£Óźż Ó”ĖÓ”ĢÓ”ŠÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”ĢÓ¦āÓ”żÓ”┐Ó”Ģ Ó”åÓ”▓Ó¦ŗ, Ó”ĖÓ¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░, Ó”»Ó¦ćÓ”© Ó”śÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”£Ó”ŠÓ”©Ó”▓Ó”ŠÓ”░ Ó”ÜÓ”┐Ó”▓Ó”żÓ¦ć Ó”½Ó”ŠÓ”üÓ”Ģ Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”śÓ”░Ó¦ć Ó”óÓ¦üÓ”ĢÓ”żÓ¦ć Ó”©Ó”Š Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć, Ó”ĖÓ¦ćÓ”£Ó”©Ó¦ŹÓ”» Ó”ĢÓ”ŠÓ”¬Ó¦£ Ó”ŚÓ¦üÓ”üÓ”£Ó¦ć Ó”ĖÓ¦ćÓ”ĖÓ”¼ Ó”½Ó”ŠÓ”üÓ”Ģ Ó”¼Ó”©Ó¦ŹÓ”¦ Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”╣Ó¦¤Óźż Ó”ÅÓ”«Ó”©Ó”ć Ó”ÅÓ”Ģ Ó”åÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”ŚÓ¦ŗÓ”¬Ó”©Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”øÓ¦ćÓ”▓Ó¦ć Ó”╣Ó”ĀÓ”ŠÓ¦Ä Ó”¬Ó¦ŗÓ”ĘÓ”Š Ó”¤Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”¬Ó”ŠÓ”¢Ó”┐Ó”░ Ó”£Ó”©Ó¦ŹÓ”» Ó”ĢÓ”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”©Ó”Š Ó”£Ó¦ŗÓ¦£Ó¦ćÓźż Ó”åÓ”░ Ó”«Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦üÓ”£Ó¦ŹÓ”£Ó”«Ó”ŠÓ”© Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”«Ó”░Ó”Ż-Ó”ČÓ”╣Ó”░Ó¦ćÓ”░ Ó”░Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”Š Ó”¼Ó¦ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”ÜÓ”▓Ó¦ćÓ”© Ó”ģÓ”▓Ó”┐Ó”ŚÓ”▓Ó”┐Ó”¬Ó”ź Ó”¼Ó¦ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦üÓ”░Ó”©Ó¦ŗ Ó”¼Ó”ŠÓ¦£Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”øÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”¤Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”¬Ó”ŠÓ”¢Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”üÓ”ÜÓ”ŠÓ”żÓ¦ćÓźż ӔŠӔżÓ¦ŗ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”«Ó”╣Ó¦Ä Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”śÓ”¤Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”¬Ó”ŠÓ”ĢÓ”½Ó¦īÓ”£ Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”ĢÓ¦ćÓ”ō Ó”¢Ó¦üÓ”üÓ”£Ó”øÓ¦ć Ó”ō Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”ĢÓ¦ć Ó”¬Ó¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”ć Ó”╣Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó”¼Ó¦ćÓźż Ó”åÓ”░ Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”ÜÓ”▓Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”øÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŗÓ”ĘÓ”Š Ó”¤Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”Ż Ó”¼Ó”ŠÓ”üÓ”ÜÓ”ŠÓ”żÓ¦ćÓźż Ó”¬Ó”ŠÓ”ĢÓ”½Ó¦īÓ”£ Ó”ĖÓ”░Ó¦ŹÓ”¼ Ó”ČÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐ Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó”░Ó”ŠÓ”ŁÓ¦éÓ”ż Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”ÜÓ”ŠÓ”ćÓ”øÓ¦ć Ó”åÓ”░ Ó”«Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦üÓ”£Ó¦ŹÓ”£Ó”«Ó”ŠÓ”© Ó”ĖÓ”░Ó¦ŹÓ”¼Ó”ČÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐ Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó””Ó¦üÓ”¤Ó”┐ Ó”¬Ó”ŠÓ”¢Ó”┐Ó”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”©Ó”ĢÓ¦ć Ó”░Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”Š Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”ō Ó”żÓ”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”¦Ó¦ĆÓ”©Ó”żÓ”Š Ó””Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”ÜÓ”▓Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż
Ó”żÓ”ŠÓ”░Ó”¬Ó”░ Ó”óÓ”ŠÓ”ĢÓ”Š Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó¦ćÓ”░Ó¦ŗÓ”©Ó¦ŗÓ”░ Ó”ģÓ”ŁÓ”┐Ó”»Ó”ŠÓ”©Óźż Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó¦Ć Ó”ō Ó”øÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”«Ó¦ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”óÓ”ŠÓ”ĢÓ”ŠÓ”żÓ¦ćÓ”ć Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ”¼Ó¦ć Ó”ÅÓ”«Ó”©Ó”ć Ó”ĀÓ”┐Ó”Ģ Ó”øÓ”┐Ó”▓Óźż Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤ Ó””Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”ŚÓ¦ćÓ”▓ Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó¦Ć Ó”░Ó”ČÓ”┐Ó””Ó”Š, Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”øÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”«Ó¦ćÓ¦¤Ó¦ćÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦üÓ””Ó¦ŹÓ””Ó¦ćÓ”ČÓ”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦Ć Ó”╣Ó”▓Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”©Ó¦ĆÓ”░Ó”¼Ó”żÓ”Š Ó”ÅÓ”Ģ Ó”«Ó”╣Ó”ŠÓ”ĢÓ”ŠÓ”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”┐Ó”Ģ Ó”©Ó¦łÓ”āÓ”ČÓ”¼Ó¦ŹÓ””Ó¦ŹÓ”»Óźż Ó”ĪÓ¦ćÓ”«Ó”░Ó”Š Ó”śÓ”ŠÓ”¤Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó”źÓ¦ć Ó”øÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ĢÓ¦ŗÓ”▓Ó¦ć Ó”¼Ó”ĖÓ”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”øÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ¦£Ó”ŠÓ”▓Ó¦ć Ó”©Ó”┐Ó”£Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó¦üÓ”¢ Ó”ŚÓ¦ŗÓ”¬Ó”© Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”╣Ó¦¤Óźż Ó”ĪÓ¦ćÓ”«Ó”░Ó”Š Ó”śÓ”ŠÓ”¤Ó¦ć Ó”żÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ Ó”¼Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”Č Ó”½Ó”ŠÓ¦¤Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ČÓ”¼Ó””Ó¦ćÓ”╣Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĖÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ģÓ”ż Ó”«Ó¦āÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ü Ó”»Ó¦ćÓ”© Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”ŻÓ¦ćÓ”░ Ó”£Ó”©Ó¦ŹÓ”» Ó”£Ó”ŠÓ¦¤Ó”ŚÓ”ŠÓ”¤Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”½Ó¦īÓ”£Ó”┐ Ó”¬Ó¦üÓ”©Ó”░Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”«Ó”Ż Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”░Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”Š Ó”ĢÓ”░Ó”øÓ”┐Ó”▓Óźż Ó”░Ó”ĖÓ¦üÓ”▓Ó¦ŹÓ”▓Ó”ŠÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó””Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó”Š, Ó”©Ó””Ó¦Ć Ó”¬Ó”źÓ¦ć, Ó”åÓ”░ Ó”ÅÓ”Ģ-Ó”ÅÓ”¬Ó”┐Ó”Ģ Ó”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó”ŠÓźż Ó”░Ó”ĖÓ¦üÓ”▓Ó¦ŹÓ”▓Ó”ŠÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ć Ó”¬Ó”░Ó”┐Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó””Ó¦üÓ”ć Ó”ĢÓ”┐Ó”ČÓ¦ŗÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”¼Ó”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”©Ó¦ĆÓ”żÓ¦ć Ó”»Ó¦ŗÓ”Ś Ó””Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”ÜÓ”▓Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”ōÓ¦¤Ó”Š Ó”åÓ”░ Ó”ŚÓ”ŠÓ”øÓ”żÓ”▓Ó”ŠÓ¦¤ Ó””Ó”ŠÓ”üÓ¦£Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”░Ó”ČÓ”┐Ó””Ó”ŠÓ”░ Ó”▓Ó¦ŗÓ”Ģ Ó”¦Ó”░Ó¦ć-Ó”¦Ó”░Ó¦ć Ó”£Ó”┐Ó”£Ó¦ŹÓ”×Ó”ŠÓ”ĖÓ”Š- Ó”żÓ”ŠÓ”░Ó”Š Ó”ĢÓ”┐ Ó”░Ó¦ŗÓ”ŚÓ”Š, Ó”▓Ó”«Ó¦ŹÓ”¼Ó”Š Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”øÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó¦āÓ”żÓ””Ó¦ćÓ”╣ Ó””Ó¦ćÓ”¢Ó¦ćÓ”øÓ¦ć? Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ć Ó”«Ó¦āÓ”żÓ””Ó¦ćÓ”╣Ó”ć Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”ĖÓ”¼Ó”ÜÓ¦ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”ĖÓ”╣Ó”£ Ó””Ó¦āÓ”ČÓ¦ŹÓ”»Óźż ŌĆśÓ”«Ó”╣Ó”ŠÓ”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”żŌĆÖ-ӔŠӔĢÓ¦üÓ”░Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ¦ćÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó”»Ó¦üÓ””Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó”░ Ó”«Ó¦ćÓ¦¤Ó¦ćÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”«Ó¦ĆÓ”¬Ó¦üÓ”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”ĖÓ”©Ó¦ŹÓ”¦Ó”ŠÓ”© Ó”ÅÓ”Ģ Ó”ÜÓ”┐Ó”░Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ”© Ó”¼Ó”┐Ó”¼Ó”░Ó”ŻÓźż Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”Č Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć ŌĆśÓ”«Ó”╣Ó”ŠÓ”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”żŌĆÖ-Ó”ÅÓ”░ Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó”»Ó”ŠÓ”¬Ó”© Ó”ĢÓ”░Ó”øÓ”┐Ó”▓ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó””Ó”┐Ó”©, Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”¤Ó”┐ Ó”«Ó¦üÓ”╣Ó¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”żÓźż
Ó”«Ó¦ŗÓ”╣Ó”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”«Ó”” Ó”«Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦üÓ”£Ó¦ŹÓ”£Ó”«Ó”ŠÓ”© Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó”©Ó¦ć Ó””Ó”ŠÓ”üÓ¦£ Ó”ĢÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó””Ó”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”»Ó¦ć Ó”ÅÓ”¬Ó”┐Ó”Ģ Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”© Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”Č Ó”»Ó”ŠÓ”¬Ó”© Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”ō Ó”ĢÓ”░Ó”øÓ¦ć Ó”ÅÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ, Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ÅÓ”¬Ó”┐Ó”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó””Ó”ŠÓ”üÓ¦£Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”¬Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ¦ć Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”» Ó”ĢÓ¦ŗÓ”© Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤ Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”©Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó”ŠÓ”ō Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”ŁÓ”¼ Ó”╣Ó”▓ Ó”©Ó”ŠÓźż
Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”▓Ó”żÓ¦ć Ó”╣Ó”¼Ó¦ć Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó””Ó”ŠÓ¦¤, Ó””Ó”ŠÓ¦¤Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”¼Ó”Š Ó”¼Ó”ŠÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”żÓ”Š Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓźż Ó”»Ó¦ć-Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”¬Ó”ŠÓ”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”» Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó””Ó¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”░Ó”Š Ó”ČÓ”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”ż Ó”©Ó¦¤Óźż Ó”»Ó¦ć Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”© Ó”«Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦üÓ”£Ó¦ŹÓ”£Ó”«Ó”ŠÓ”© Ó”ō Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”«Ó”ż Ó”ĢÓ”ż Ó”ĖÓ”╣Ó”ĖÓ¦ŹÓ”░ Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”Ę Ó”»Ó”ŠÓ”¬Ó”© Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”½Ó”┐Ó”░Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĖÓ¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”Č Ó”░Ó”ÜÓ”©Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£Ó¦ć -Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó””Ó¦üÓ”ć Ó”¤Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”¬Ó”ŠÓ”¢Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”«Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐ Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”ż- Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ĖÓ¦āÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”┐Ó”ČÓ¦ĆÓ”▓Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ĆÓ”ĢÓ¦āÓ”żÓ”┐Ó”żÓ¦ćÓ”ć Ó”åÓ”£ Ó”åÓ”«Ó”┐ ŌĆśÓ”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”éÓ”ĢÓ”¤ŌĆÖ Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó”▓Ó”¼ Ó”ō Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”ŻÓ¦ćÓ”░ Ó”©Ó¦ćÓ”¬Ó”źÓ¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”ĖÓ”¼ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤Ó”ć Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ”¼Ó¦ć Ó”«Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦üÓ”£Ó¦ŹÓ”£Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”ĖÓ¦ŹÓ”źÓ”┐Ó”żÓ”┐Óźż
Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”ĢÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”▓Ó¦ć Ó”ō Ó”ĢÓ¦ŗÓ”© Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”¦Ó”░Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó¦ć Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”╣Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćŌĆö Ó”ÅÓ”ć Ó””Ó¦üÓ”¤Ó”┐ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ČÓ¦ŹÓ”© Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”ĖÓ”░Ó¦ŹÓ”¼Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”«Ó”ż Ó”ŁÓ¦üÓ”▓ Ó”ĖÓ”┐Ó””Ó¦ŹÓ”¦Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”ż Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ćÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”░Ó¦ŹÓ”ŁÓ¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ż Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ŚÓ¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ĖÓ”░Ó¦ŹÓ”¼Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”«Ó”żÓ”┐ Ó”ō Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”░Ó¦ŹÓ”ŁÓ¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”Ż Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”ŠÓ”ćŌĆö Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ČÓ¦ŹÓ”©Ó””Ó¦üÓ”¤Ó”┐ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ČÓ¦ŹÓ”© Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”ĘÓ¦ć Ó”»Ó”żÓ”¤Ó”Š Ó”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”╣Ó¦ŹÓ”», Ó”ÅÓ”░ Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░Ó”¤Ó”Š Ó”żÓ”żÓ”ć Ó”ģÓ”«Ó¦ĆÓ”«Ó”ŠÓ”éÓ”ĖÓ”┐Ó”ż Ó”╣Ó”żÓ¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Óźż Ó”»Ó¦ć-Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ČÓ¦ŹÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐Ó”«Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░ Ó”╣Ó¦¤ Ó”©Ó”Š, Ó”╣Ó”ōÓ¦¤Ó”Š Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”ŁÓ”¼ Ó”©Ó¦¤, Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ČÓ¦ŹÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”»Ó¦ć-Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”«Ó”ż Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”ōÓ¦¤Ó”ŠÓ”¤Ó”Š Ó”╣Ó”ŠÓ”żÓ¦ćÓ”░ Ó”©Ó”ŠÓ”ŚÓ”ŠÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£ Ó”ÜÓ”ŠÓ”▓Ó”ŠÓ”©Ó¦ŗÓ”░ Ó”¬Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ¦ć Ó”©Ó¦ćÓ”╣Ó”ŠÓ¦Ä Ó””Ó”░Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”┐Óźż Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”ĘÓ¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó”┐Ó”Ģ Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”Č Ó”ō Ó”ģÓ”░Ó¦ŹÓ”źÓ”©Ó¦łÓ”żÓ”┐Ó”Ģ Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ¦ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”£Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”ŠÓ””Ó¦Ć Ó”¼Ó”Š Ó”åÓ”¦Ó”┐Ó”¬Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”ČÓ¦ĆÓ”▓ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó”Š Ó”ō Ó”¬Ó””Ó¦ŹÓ”¦Ó”żÓ”┐Ó”░ Ó”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”¼, Ó”»Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”åÓ”«Ó”░Ó”Š Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”£Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”ŠÓ””Ó¦Ć Ó”¼Ó”Š Ó”öÓ”¬Ó”©Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ”┐Ó”Ģ Ó”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”¼Ó”ć Ó”¼Ó”▓Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó”┐, Ó”«Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”░ Ó””Ó¦ü-Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”Č Ó”¼Ó”øÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦üÓ”░Ó”©Ó¦ŗ, Ó”åÓ”░-Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó¦ü Ó”¼Ó”ŠÓ¦£Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”©Ó”Š Ó”╣Ó¦¤ Ó”ÜÓ”ŠÓ”░-Ó”¬Ó”ŠÓ”üÓ”ÜÓ”Č Ó”¼Ó”øÓ”░Ó”ć Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤ Ó”¼Ó¦£ Ó”£Ó¦ŗÓ”░, Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ”┐ Ó”żÓ¦ŗ Ó”©Ó¦¤Óźż Ó”ģÓ”źÓ”Ü Ó”»Ó¦ćÓ”╣Ó¦ćÓ”żÓ¦ü Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”¼Ó¦ć Ó”¬Ó¦āÓ”źÓ”┐Ó”¼Ó¦ĆÓ”░ Ó”ĖÓ”¼ Ó””Ó¦ćÓ”Č Ó”¬Ó”░Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”øÓ”ŠÓ”ĢÓ”ŠÓ”øÓ”┐ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”Ģ Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ”┐, Ó”żÓ”ŠÓ”ć Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”ŚÓ”ż Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ČÓ¦ŹÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░Ó”ō Ó”ÅÓ”ć Ó”åÓ”¦Ó”┐Ó”¬Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”ŠÓ””Ó¦Ć Ó”ÜÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”░ Ó”£Ó”¼Ó”░Ó””Ó”¢Ó”▓ Ó”ÜÓ”ŠÓ”▓Ó¦üÓ”ć Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”»Ó”ŠÓ¦¤, ӔŠӔ©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”¼Ó”ŠÓ”” Ó”¼Ó¦£ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”╣Ó¦¤ Ó”©Ó”ŠÓźż
Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬-Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”ĢÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”▓Ó¦ć Ó”ō Ó”ĢÓ¦ŗÓ”© Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”¦Ó”░Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó¦ć Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”╣Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćŌĆö Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ČÓ¦ŹÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░Ó¦ć Ó”»Ó¦ć Ó”ĖÓ”░Ó¦ŹÓ”¼Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”«Ó”żÓ”┐ Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”ŁÓ¦ŹÓ”»Ó”ĖÓ¦ŹÓ”ż Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ŚÓ¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”ŻÓ”¤Ó”Š Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó¦ü Ó”¼Ó”┐Ó””Ó¦ŹÓ”śÓ¦üÓ”¤Ó¦ćÓźż Ó”ÅÓ”ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ČÓ¦ŹÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░Ó¦ć Ó”¦Ó”©Ó”żÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó¦ć Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ¦Ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”¼Ó”┐Ó””Ó”░Ó”Š Ó”ō Ó”«Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĖÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ć Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ¦Ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”¼Ó”┐Ó””Ó”░Ó”Š Ó”ÅÓ”ĢÓ”«Ó”ż Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ŚÓ¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”Ģ Ó””Ó”┐Ó”©, Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ¦¤ Ó”«Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ŹÓ”Ė-Ó”ÅÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ćÓ”ćÓźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”«Ó”żÓ¦łÓ”ĢÓ¦ŹÓ”»Ó”¤Ó”Š Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć Ó”ÅÓ”ćŌĆö Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”╣Ó¦¤ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó¦ć, Ó”»Ó¦ć-Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó¦ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¦Ó”ŠÓ”© Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ōÓ”ĀÓ¦ćÓźż Ó”ÅÓ”ĢÓ”£Ó”© Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”ĘÓ¦ćÓ”░ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”©Ó¦ĆÓ”ć Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”ČÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŹÓ”«Ó¦üÓ”¢ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”░ Ó”åÓ”ĢÓ”ŠÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤ Ó”╣Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”¼Ó¦ćÓ”Č Ó”¼Ó¦£Ó”ĖÓ¦£ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”£Ó”«Ó”┐Ó””Ó”ŠÓ”░Ó”┐Ó”░ Ó”«Ó”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”Ģ Ó”╣Ó”ōÓ¦¤Ó”Š, Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”ŻÓ¦ć Ó”ĖÓ¦ć Ó”żÓ¦ćÓ”«Ó”© Ó”£Ó”«Ó”┐Ó””Ó”ŠÓ”░Ó”┐Ó”░ Ó”£Ó”©Ó¦ŹÓ”» Ó”ģÓ”¬Ó”░Ó”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”» Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó¦ĆÓ”żÓ””Ó”ŠÓ”Ė Ó”ĖÓ”éÓ”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”╣ Ó”ĢÓ”░Ó”▓Ó¦ć Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓźż Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”£Ó¦ŗÓ”░ Ó”©Ó”Š Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ”ŠÓ¦¤ Ó”ĖÓ¦ć Ó”śÓ¦üÓ”░Ó¦ć-Ó”śÓ¦üÓ”░Ó¦ć Ó”¼Ó¦£-Ó”¼Ó¦£ Ó”£Ó”«Ó”┐Ó””Ó”ŠÓ”░Ó””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”ø Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”░Ó”Š-Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó¦ĆÓ”żÓ””Ó”ŠÓ”ĖÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”©Ó”ŠÓ”«Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ć Ó”¼Ó¦ćÓ¦£Ó”ŠÓ¦¤Óźż Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”Ģ Ó”£Ó”«Ó”┐Ó””Ó”ŠÓ”░ Ó”©Ó”ŠÓ”«Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó””Ó¦ćÓ¦¤ Ó”¼Ó”¤Ó¦ć Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó””Ó”ŠÓ”« Ó”©Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ćÓ”£Ó¦ŹÓ”£Ó”żÓ¦ć Ó”▓Ó”ŠÓ”ŚÓ¦ćÓźż Ó”ÅÓ”ć Ó”▓Ó¦ŗÓ”ĢÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”ČÓ”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ¦¤ Ó”£Ó”«Ó”┐Ó””Ó”ŠÓ”░ Ó”╣Ó”ōÓ¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”ŚÓ”ż Ó”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ”©Ó”Š Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ¦¤ Ó”»Ó¦ćÓ”© Ó”¬Ó¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”Ż Ó”╣Ó¦¤Óźż Ó”ŚÓ¦ŗÓ”ŚÓ¦ŗÓ”▓-Ó”ÅÓ”░ ŌĆśÓ”ĪÓ¦ćÓ”ĪÓ”ĖÓ¦ŗÓ”▓Ó”ĖŌĆÖ Ó”¼Ó”Š, Ó”ÅÓ”ĢÓ”£Ó”© Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”ĘÓ¦ćÓ”░ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”ĢÓ¦éÓ”▓ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó¦ć Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”«Ó¦ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”øÓ”░ Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¼Ó¦āÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”┐ Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć, Ó”¬Ó”ŠÓ”üÓ”ÜÓ”¼Ó”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćŌĆö Ó”ÅÓ”ĢÓ”¼Ó”ŠÓ”░ Ó”©Ó”┐Ó”£Ó¦ćÓ”░ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ćÓ”ĢÓ¦ć, Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŗ┬ĀÓ”¼Ó”øÓ”░ Ó”¦Ó”░Ó¦ć Ó”ÜÓ¦üÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”»Ó¦ćÓ”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć, Ó”ÜÓ¦īÓ”░Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó¦āÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”ć Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”¬Ó¦ćÓ”ČÓ”Š, Ó”åÓ”¤ Ó”¼Ó”øÓ”░ Ó”ģÓ”¬Ó”░Ó”ŠÓ”¦Ó¦Ć Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ”©Ó””Ó”ŻÓ¦ŹÓ”Ī┬ĀÓ”ŁÓ¦ŗÓ”Ś Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć, Ó”ČÓ¦ćÓ”ĘÓ¦ć Ó”¼Ó¦£Ó”▓Ó¦ŗÓ”Ģ Ó”╣Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć, Ó”ŁÓ”ŠÓ”▓Ó¦ŗ┬ĀÓ”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”Ę Ó”╣Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”ō Ó”«Ó¦āÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦üÓ”░ Ó”åÓ”ŚÓ¦ć Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”żÓ”¬Ó¦ŹÓ”żÓ”ō Ó”╣Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓźż Ó”ĪÓ¦ćÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”▓ Ó”ĪÓ”┐Ó”½Ó¦ŗ-Ó”░ ŌĆśÓ”«Ó”▓ Ó”½Ó¦ŹÓ”▓Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”ĪÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖŌĆÖ (Ó¦¦Ó¦ŁÓ¦©Ó¦©)Óźż Ó”¼Ó”Š, Ó”żÓ¦ćÓ”«Ó”© Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó”ŠÓ”ŻÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”« Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó¦ć Ó”ÅÓ”Ģ Ó”¼Ó¦£ Ó”ģÓ”«Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó¦ī Ó”¤Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”©Ó¦ć Ó””Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć-Ó”»Ó”ŠÓ”ōÓ¦¤Ó”Š Ó”ÅÓ”Ģ Ó”øÓ¦ŗÓ”ĢÓ”░Ó”ŠÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”«Ó¦ć Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”¬Ó¦£Ó¦ć Ó”»Ó¦ćÓ”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”»Ó¦ć Ó”śÓ”░-Ó”ĖÓ”éÓ”ĖÓ”ŠÓ”░ Ó”øÓ¦ćÓ¦£Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”øÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”ŠÓ”ō Ó”╣Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”ō Ó”ČÓ¦ćÓ”ĘÓ¦ć Ó”ÅÓ”Ģ Ó”¤Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ÜÓ”ŠÓ”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”żÓ”▓Ó”ŠÓ¦¤ Ó”ØÓ”ŠÓ”üÓ”¬ Ó””Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓźż Ó”żÓ”▓Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ¦¤-Ó”ÅÓ”░ Ó”åÓ”©Ó”Š Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”©Ó”┐Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ĢÓ”┐Ó”éÓ”¼Ó”Š Ó”åÓ”░-Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”«Ó¦ćÓ¦¤Ó¦ć, Ó”ĢÓ”ŠÓ”¬Ó”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó”żÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó”ĖÓ¦ĆÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ”┐Ó”©Ó¦ĆÓ””Ó”ČÓ”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”©Ó¦ŹÓ””Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ÅÓ”Ģ Ó”åÓ”ÜÓ”«Ó”ĢÓ”Š Ó””Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”¬Ó¦üÓ”░Ó¦üÓ”ĘÓ¦ćÓ”░Ó”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”£Ó”©Ó”¬Ó””Ó¦ć Ó”åÓ”ĖÓ¦ć Ó”¼Ó”¤Ó¦ć Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”¬Ó¦üÓ”░Ó¦üÓ”ĘÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”ĖÓ”¼ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ČÓ¦ŹÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦ć Ó”¼Ó¦üÓ”ØÓ”żÓ¦ć Ó”©Ó”Š Ó”¬Ó¦ćÓ”░Ó¦ć Ó”ŚÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ”ŠÓ¦¤ Ó”ŁÓ¦ćÓ”ĖÓ¦ć Ó”»Ó”ŠÓ¦¤Óźż Ó”¼Ó”ÖÓ¦ŹÓ”ĢÓ”┐Ó”«Ó”ÜÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”░ ŌĆśÓ”ĢÓ”¬Ó”ŠÓ”▓Ó”ĢÓ¦üÓ”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ”▓Ó”ŠŌĆÖÓźż Ó”¼Ó”Š, Ó”ÅÓ”Ģ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ŚÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”ĘÓ¦Ć Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”Ę Ó”ĢÓ¦ŗÓ”żÓ¦ŹÓ”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”ŚÓ”ŠÓ”¦Ó”ŠÓ”░ Ó”ÜÓ”ŠÓ”«Ó¦£Ó”Š Ó”¬Ó¦ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ¦¤ Ó”ÅÓ”ć Ó”ČÓ”░Ó¦ŹÓ”żÓ¦ć Ó”»Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”¼ Ó”ēÓ”ÜÓ¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ”ĢÓ”ŠÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”ŠÓ”ć┬ĀÓ”«Ó”┐Ó”¤Ó”¼Ó¦ć Ó”¼Ó”¤Ó¦ć Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”ÜÓ”ŠÓ”«Ó¦£Ó”ŠÓ”¤Ó”Š Ó”øÓ¦ŗÓ”¤ Ó”╣Ó”żÓ¦ć-Ó”╣Ó”żÓ¦ć Ó”ĖÓ¦ć Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”»Ó”©Ó¦ŹÓ”ż Ó”«Ó”░Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”¼Ó¦ćÓźż Ó”¼Ó”ŠÓ”▓Ó”£Ó”ŠÓ”Ģ-Ó”ÅÓ”░ ŌĆśÓ”«Ó”░Ó”Š Ó”ŚÓ”ŠÓ”¦Ó”ŠÓ”░ Ó”ÜÓ”ŠÓ”«Ó¦£Ó”ŠŌĆÖ Ó”¼Ó”Š, Ó”ĖÓ”┐Ó”¬Ó”ŠÓ”╣Ó”┐ Ó”¼Ó”┐Ó””Ó¦ŹÓ”░Ó¦ŗÓ”╣Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”¬Ó”źÓ¦ć Ó”¬Ó¦£Ó¦ć Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ”Š Ó”ČÓ”┐Ó”ČÓ¦ü Ó”ŚÓ¦ćÓ”ŠÓ”üÓ¦£Ó”Š Ó”¼Ó”ŠÓ”«Ó¦üÓ”© Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó¦£ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ōÓ”ĀÓ¦ć Ó”ō Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”ĖÓ”éÓ”ĢÓ”¤Ó¦ć Ó”©Ó”┐Ó”£Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”åÓ””Ó”┐ Ó”¬Ó”░Ó”┐Ó”ÜÓ¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó¦üÓ”¢Ó¦ŗÓ”«Ó¦üÓ”¢Ó”┐ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ¦¤, Ó”ĖÓ¦ć Ó”żÓ¦ŗ Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”żÓ¦ĆÓ¦¤Ó”ć Ó”©Ó¦¤, Ó”¼Ó”ŠÓ”«Ó¦üÓ”© Ó”żÓ¦ŗ Ó””Ó¦éÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓźż Ó”░Ó”¼Ó¦ĆÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó¦ŹÓ”░Ó”©Ó”ŠÓ”źÓ¦ćÓ”░ ŌĆśÓ”ŚÓ¦ŗÓ”░Ó”ŠŌĆÖÓźż Ó”¼Ó”Š, Ó”ĖÓ¦üÓ”ćÓ”£Ó”ŠÓ”░Ó”▓Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”ĪÓ¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó”ŠÓ”¤Ó¦ŗÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”«Ó¦ć Ó”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ¦ŹÓ”«Ó”ŠÓ”░Ó¦ŗÓ”ŚÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”ż Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”Ę Ó”ČÓ¦üÓ”¦Ó¦ü Ó”żÓ”░Ó¦ŹÓ”Ģ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ¦¤ Ó”śÓ”©Ó”ŠÓ¦¤Ó”«Ó”ŠÓ”© Ó”½Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”¼Ó”ŠÓ”” Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓźż Ó”ĢÓ”źÓ”Š, Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”åÓ”░ Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗÓ”ĢÓ¦ć Ó”øÓ¦ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”½Ó¦ćÓ”▓Ó¦ćÓźż Ó”¤Ó”«Ó”ŠÓ”Ė Ó”«Ó”ŠÓ”©-Ó”ÅÓ”░ ŌĆśÓ”«Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”£Ó”┐Ó”Ģ Ó”«Ó”ŠÓ”ēÓ”©Ó¦ŹÓ”¤Ó¦ćÓ”©ŌĆÖÓźż Ó”¼Ó”Š, Ó”«Ó¦āÓ”ŚÓ¦ĆÓ”░Ó¦ŗÓ”ŚÓ¦ćÓ”░ Ó”ÜÓ”┐Ó”ĢÓ”┐Ó¦ÄÓ”ĖÓ”ŠÓ¦¤ Ó”©Ó”┐Ó”£Ó¦ćÓ”░ Ó”»Ó¦īÓ”¼Ó”©Ó”ĢÓ”ŠÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ć Ó”ĢÓ”ŠÓ”¤Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”░Ó”ŠÓ”ČÓ”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”½Ó”┐Ó”░Ó¦ć-Ó”åÓ”ĖÓ”Š Ó”ÅÓ”Ģ Ó”ĢÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ””Ó”ĢÓ”╣Ó¦ĆÓ”© Ó”øÓ¦ŗÓ”ĢÓ”░Ó”Š, Ó”»Ó¦ć Ó”©Ó”ŠÓ”ĢÓ”┐ Ó”ÅÓ”ĢÓ”ć Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”£Ó”© Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”ĖÓ”ō Ó”¼Ó”¤Ó¦ć Ó”ō Ó”ÅÓ”ĢÓ”£Ó”© Ó”ćÓ”ĪÓ”┐Ó¦¤Ó”¤Ó”ō Ó”¼Ó”¤Ó¦ć Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ōÓ”ĀÓ¦ć Ó”ÅÓ”Ģ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŚÓ”ŠÓ¦Ø Ó””Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ČÓ”©Ó”┐Ó”Ģ, Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”¬Ó”ŠÓ¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”żÓ”▓Ó”ŠÓ¦¤ Ó”¬Ó¦£Ó¦ć Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”¤Ó”ŠÓ”ĢÓ”Š Ó”åÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”” Ó”åÓ”░ Ó”©Ó”ŠÓ”░Ó¦ĆÓźż Ó””Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ¦¤Ó¦ćÓ”ŁÓ¦ŹÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ”┐Ó”░ ŌĆśÓ”ćÓ”ĪÓ”┐Ó¦¤Ó”¤ŌĆÖÓźż Ó”¼Ó”Š, Ó”åÓ”½Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”Š Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”£Ó”ŠÓ”╣Ó”ŠÓ”£Ó¦ćÓ”░ Ó”¢Ó¦ŗÓ”▓Ó¦ć Ó”ŁÓ”░Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”åÓ”ĖÓ”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓ Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░ Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ¦¤ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”ČÓ¦ŹÓ”░Ó”«Ó”┐Ó”Ģ Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░Ó”ć Ó”¼Ó”éÓ”ČÓ”¦Ó”░ Ó”ÅÓ”¢Ó”© Ó”ÅÓ”ć Ó”¼Ó”┐Ó”Č-Ó”ÅÓ”ĢÓ¦üÓ”Č Ó”ČÓ”żÓ”ĢÓ¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ČÓ¦ŹÓ”© Ó”żÓ¦üÓ”▓Ó”øÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ”¬Ó”░Ó”┐Ó”ÜÓ¦¤ Ó”ō Ó”¼Ó”éÓ”Č Ó”¬Ó”░Ó”┐Ó”ÜÓ¦¤ Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓźż Ó”¤Ó”©Ó”┐ Ó”«Ó”░Ó”┐Ó”ĖÓ”©-Ó”ÅÓ”░ ŌĆśÓ”¼Ó”┐Ó”▓Ó”ŠÓ”ŁÓ¦ćÓ”ĪŌĆÖÓźż Ó”ģÓ”ĖÓ”ēÓ”ćÓ¦ÄÓ”Ė-ӔŠӔ»Ó¦ć Ó”¼Ó”©Ó¦ŹÓ””Ó¦Ć Ó”øÓ”┐Ó”▓ Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”ÅÓ”Ģ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Ģ Ó”¼Ó¦ćÓ”üÓ”ÜÓ¦ć Ó”½Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ČÓ¦ŹÓ”© Ó”żÓ¦üÓ”▓Ó”øÓ¦ćŌĆö Ó”ĖÓ¦ć Ó”ĢÓ”┐ Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó¦ć Ó”½Ó”┐Ó”░Ó”▓Óźż Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”¤Ó¦ćÓ”£-Ó”ÅÓ”░ ŌĆśÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ¦üÓ”ćÓ”« Ó”½Ó”░ Ó”ģÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”© Ó”åÓ”©Ó”¼Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŹÓ”© Ó”ÜÓ”ŠÓ”ćÓ”▓Ó¦ŹÓ”ĪŌĆÖÓźż Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”Š Ó”¬Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó”« Ó”åÓ”░ Ó”¬Ó¦üÓ”¼Ó¦ć Ó”ŁÓ”ŠÓ”Ś Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”ōÓ¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”¬Ó”░ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐ Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”¬Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó”« Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”¬Ó¦üÓ”¼Ó¦ć Ó”ÜÓ”▓Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”ōÓ¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”¬Ó”ź Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”¬Ó”źÓ¦ćÓ”░ Ó””Ó¦üÓ”¤Ó”┐ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”░Óźż Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”ÜÓ¦ŹÓ”ø Ó”¼Ó”░Ó”½Ó¦ćÓ”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░ Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó””Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤ Ó”żÓ”▓Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”▓ Ó”¬Ó”źÓźż Ó”ČÓ¦üÓ”¦Ó¦ü Ó”¬Ó”źÓ”¼Ó”ŠÓ”╣Ó”©Óźż Ó”ÅÓ”ĢÓ”ć Ó”¬Ó””-Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó””Ó¦üÓ”¤Ó¦ŗ Ó”¬Ó”źÓźż Ó”«Ó”ŠÓ”╣Ó”«Ó¦üÓ””Ó¦üÓ”▓ Ó”╣Ó”Ģ-Ó”ÅÓ”░ ŌĆśÓ”ĢÓ”ŠÓ”▓Ó¦ŗ Ó”¼Ó”░Ó”½ŌĆÖÓźż Ó”ÅÓ”Ģ Ó”¼Ó¦üÓ¦£Ó¦ŗ Ó”«Ó”ŠÓ”ØÓ”┐ Ó”½Ó”┐Ó”░Ó”øÓ¦ć Ó”ĖÓ”«Ó¦üÓ””Ó¦ŹÓ”░Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ĪÓ”┐Ó”ÖÓ”┐Ó”żÓ¦ć Ó”╣Ó”ŠÓ”ÖÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”»Ó¦üÓ””Ó¦ŹÓ”¦ Ó”ĖÓ¦ćÓ”░Ó¦ćÓźż Ó”╣Ó”ŠÓ”ÖÓ”░, Ó”░Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ż, Ó”«Ó¦āÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ü Ó”ō Ó”«Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Óźż Ó”åÓ”░Ó¦ŹÓ”©Ó¦ćÓ”ĖÓ¦ŹÓ”¤ Ó”╣Ó¦ćÓ”«Ó”┐Ó”éÓ”ōÓ¦¤Ó¦ćÓ”░ ŌĆśÓ””Ó”┐ Ó”ōÓ”▓Ó¦ŹÓ”Ī Ó”«Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”© Ó”ÅÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”Ī Ó””Ó”┐ Ó”ĖÓ”┐ŌĆÖÓźż
Ó”ÅÓ”ć Ó”ĖÓ”¼Ó”ć Ó”ĢÓ”┐ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”░ Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬? Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”░ Ó”åÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”ĖÓ”©Ó¦ŹÓ”¦Ó”ŠÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”Š Ó”åÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”¼Ó”éÓ”ĖÓ¦ćÓ”░? Ó”ĖÓ”¼ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”ć Ó”ĢÓ”┐ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”░ Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”źÓ”ŠÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ¦ŗÓ”¬Ó”ŠÓ”© Ó”¼Ó”Š Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”░ Ó”¦Ó¦ŹÓ”¼Ó”éÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”¦Ó¦ŹÓ”¼Ó”ĖÓ¦ŹÓ”ż Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”ĢÓ”ŠÓ”░? Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓ”ć Ó”ĢÓ”┐ Ó”¼Ó”▓Ó”øÓ¦ćÓ”© Ó”¬Ó”ŠÓ”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”¼Ó¦üÓ”░Ó¦ŹÓ”£Ó¦ćÓ”ŠÓ¦¤Ó”Š Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”źÓ”ŠÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”╣Ó”żÓ¦ŹÓ”żÓ”« Ó””Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ČÓ”©Ó”┐Ó”Ģ Ó”╣Ó¦ćÓ”ŚÓ¦ćÓ”▓ Ó”ō Ó”╣Ó¦ćÓ”ŚÓ¦ćÓ”▓ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”«Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĖÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ć Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ĆÓ”░Ó¦ŹÓ”Ż Ó”ŚÓ¦ćÓ¦¤Ó”░Ó¦ŹÓ”Ś Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü?
Ó””Ó¦üÓ”ć
Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ć Ó”▓Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó”¤Ó”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”»Ó¦ćÓ”© Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó¦ü Ó”żÓ”ŠÓ¦ÄÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”ŻÓ”┐Ó”ĢÓ”żÓ”Š Ó”åÓ”øÓ¦ć, Ó”▓Ó”┐Ó”¢Ó”żÓ¦ć Ó”▓Ó”┐Ó”¢Ó”żÓ¦ć Ó”»Ó¦ćÓ”«Ó”© Ó”«Ó”©Ó¦ć Ó”åÓ”ĖÓ”øÓ¦ć Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗÓ”░ Ó”ēÓ”▓Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ćÓ”¢ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ”┐Óźż Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓ”¤Ó”Š Ó”ģÓ”░Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ćÓ”Ģ Ó”ĀÓ”┐Ó”ĢÓźż Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”▓Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤ Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”©Ó”┐Ó”£Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”üÓ”¦Ó”żÓ¦ć Ó”ÜÓ”ŠÓ”ć Ó”©Ó”┐Óźż Ó”żÓ¦ćÓ”«Ó”©Ó”┐ Ó”åÓ”¼Ó”ŠÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦āÓ”ÖÓ¦ŹÓ”¢Ó”▓ Ó”▓Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó”┐ Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”©Ó”┐Ó”£Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”▓Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó”┐Ó”żÓ¦ćÓ”ō Ó”¼Ó”ŠÓ”üÓ”¦Ó”żÓ¦ć Ó”ÜÓ”ŠÓ”ć Ó”©Ó”┐ Ó”ÅÓ”ć Ó”ĖÓ¦éÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó”¤Ó”Š Ó”¬Ó”░Ó¦ĆÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”Š Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”»Ó¦ć Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó¦ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”¦Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”» Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”┐Ó”ż Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”ģÓ”░Ó¦ŹÓ”źÓ”©Ó¦łÓ”żÓ”┐Ó”Ģ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”ĖÓ¦ŹÓ”źÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”ŻÓ¦ć Ó”ō Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”ŻÓ¦ćÓ”░ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦éÓ”¬Óźż Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”ĘÓ¦ćÓ”░ Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó”»Ó”ŠÓ”¬Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”ŠÓ””Ó”ŠÓ”©Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”ć Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ŁÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”żÓ”┐ŌĆö Ó”ÅÓ”ć Ó”ĖÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó”¤Ó”┐ Ó”ÅÓ”żÓ”ć Ó”£Ó”¤Ó”┐Ó”▓ Ó”»Ó¦ć Ó”ĖÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó”¤Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó¦üÓ”ØÓ¦ć Ó”©Ó¦ćÓ¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”Š Ó”żÓ”źÓ¦ŹÓ”»Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”ĖÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”ĢÓ¦éÓ”▓Ó¦ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”£Ó”ŠÓ”©Ó¦ŗÓ”░ Ó”żÓ¦£Ó”┐Ó”śÓ¦£Ó”┐ Ó””Ó”░Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”ĘÓ¦ćÓ”░ Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”© Ó”ō Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó”»Ó”ŠÓ”¬Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ŁÓ”┐Ó”żÓ”░Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¬Ó”░Ó”┐Ó”Ģ Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ”ŁÓ”░Ó”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”ÜÓ¦īÓ”ĢÓ¦ŗ Ó”¢Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ćÓ”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░ Ó”åÓ”░-Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤ Ó”ÜÓ¦īÓ”ĢÓ¦ŗ Ó”¢Ó¦ŗÓ”¬ Ó”¼Ó”ĖÓ”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”«Ó”ż Ó”øÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”ĘÓ”┐ Ó”¢Ó¦ćÓ”▓Ó”Š, Ó”¼Ó”Š Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”żÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ŁÓ¦üÓ”£Ó”ŠÓ”ĢÓ¦āÓ”żÓ”┐┬ĀÓ”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó”ŠÓ”░ Ó”«Ó”ż Ó”£Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”«Ó”┐Ó”żÓ”┐Ó”Ģ Ó”¢Ó¦ćÓ”▓Ó”ŠÓ¦¤, Ó”«Ó¦ćÓ”żÓ¦ć Ó”ōÓ”ĀÓ”ŠÓ”¤Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ćÓ”ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”£Ó”┐Ó”£Ó¦ŹÓ”×Ó”ŠÓ”ĖÓ”Š Ó”«Ó”©Ó¦ć Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Óźż
Ó”ÅÓ”ć Ó”▓Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó”¤Ó”ŠÓ”żÓ¦ć Ó¦¦Ó¦ŁÓ¦©Ó¦© Ó”ĖÓ”ŠÓ”▓Ó¦ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š ŌĆśÓ”«Ó”▓ Ó”½Ó¦ŹÓ”▓Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”ĪÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖŌĆÖ Ó”åÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”ĖÓ”¼Ó¦ć Ó”«Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”»Ó”ŠÓ”üÓ”░Ó”Š Ó”ÅÓ”¤Ó”Š Ó”▓Ó”┐Ó”¢Ó”øÓ¦ćÓ”© Ó”żÓ”ŠÓ”░Ó”ŠÓ”ō Ó”£Ó”ŠÓ”©Ó¦ćÓ”© Ó”©Ó”Š Ó”»Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦éÓ”¬Ó¦ćÓ”░ Ó”£Ó”©Ó¦ŹÓ”« Ó””Ó”┐Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”żÓ”ŠÓ”░Ó”ŠÓźż Ó”«Ó”▓ Ó”½Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”ĪÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”Ė Ó”ĖÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”ĢÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”«Ó¦ćÓ¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”öÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”Ģ Ó”ÜÓ”░Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”░, Ó”¼Ó”ŠÓ”©Ó”ŠÓ”©Ó¦ŗ Ó”ō Ó”¼Ó”ŠÓ”©Ó”ŠÓ”©Ó¦ŗ Ó”©Ó¦¤Óźż Ó”ĖÓ¦ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”¤Ó¦ćÓ”© Ó”ō Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”░ Ó”ŁÓ”┐Ó”żÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”ĖÓ¦ćÓ”żÓ¦ü Ó”¼Ó”Š Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¼Ó”©Ó¦ŹÓ”¦ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ēÓ”ĀÓ¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ĖÓ¦ć Ó”©Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ¦¤Ó”ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”¤Ó¦ćÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”żÓ”¢Ó”©Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ģÓ”░Ó¦ŹÓ”źÓ”©Ó¦łÓ”żÓ”┐Ó”Ģ Ó”¬Ó”░Ó”┐Ó”¼Ó”░Ó¦ŹÓ”żÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ¦üÓ”»Ó¦ŗÓ”ŚÓ¦ć Ó”©Ó”┐Ó”£Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”¬Ó”ĢÓ¦ćÓ”¤Ó”«Ó”ŠÓ”░, Ó”ÜÓ¦ŗÓ”░ Ó”ō Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ¦ŹÓ”»Ó”Š Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”┐Ó”ż Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó¦ćÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓ Ó”ō Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”«Ó”ż Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”ĘÓ”£Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”»Ó”ŠÓ”¬Ó”© Ó”¼Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”¤Ó¦ćÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó”┐Ó”Ģ Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ¦ć Ó”ĢÓ”▓Ó”ÖÓ¦ŹÓ”Ģ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ēÓ”ĀÓ”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”ŁÓ¦ćÓ”¼Ó¦ćÓ”ć Ó”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”¤Ó¦ćÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐ Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ”©Ó¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”ĀÓ”ŠÓ”©Ó¦ŗ Ó”╣Ó”▓Óźż Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó”░ Ó”ģÓ”¬Ó”░Ó”ŠÓ”¦-Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¦Ó”ŠÓ”© Ó”«Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ż Ó”¬Ó”░Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ¦ć Ó”«Ó”▓ Ó”½Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”ĪÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”Ė Ó”¼Ó¦ćÓ”Č Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”┐Ó”ż Ó”╣Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó”▓Óźż Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”»Ó”©Ó¦ŹÓ”ż Ó”ĖÓ¦ć Ó”ÅÓ”żÓ”¤Ó”ŠÓ”ć Ó”ŁÓ””Ó¦ŹÓ”░Ó”▓Ó¦ŗÓ”Ģ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ēÓ”ĀÓ”▓ Ó”»Ó¦ć Ó”¢Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ćÓ”░ Ó”░Ó¦ĆÓ”żÓ”┐ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”»Ó”ŠÓ¦¤Ó¦Ć Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”żÓ”ŠÓ”¬ Ó”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”»Ó”©Ó¦ŹÓ”ż Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”½Ó¦ćÓ”▓Ó”▓Óźż Ó”«Ó”▓ Ó”½Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”ĪÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”Ė-Ó”ÅÓ”░ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”ČÓ”┐Ó”ż Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ēÓ”ĀÓ”▓ Ó”ĢÓ”┐ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”żÓ”¢Ó”©Ó”ć, Ó”»Ó”¢Ó”© Ó”ĖÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”ż Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”ČÓ¦ĆÓ”▓ Ó”¬Ó¦ćÓ”ČÓ”Š Ó”ō Ó”¬Ó¦ćÓ”ČÓ”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”£Ó¦ŗÓ”░Ó¦ć Ó”åÓ”╣Ó¦āÓ”ż Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦üÓ”¤Ó”Š Ó”¤Ó”ŠÓ”ĢÓ”ŠÓ”¬Ó¦¤Ó”ĖÓ”Š Ó”ō Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦üÓ”¤Ó”Š Ó”åÓ”ćÓ”© Ó”«Ó¦ŗÓ”żÓ”ŠÓ”¼Ó¦ćÓ”Ģ Ó”ČÓ”ŠÓ”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”ĖÓ”╣ Ó”¬Ó¦üÓ”░Ó”©Ó¦ŗ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ĆÓ”ĢÓ¦āÓ”ż Ó”¢Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó”ŠÓ”© Ó”ŁÓ””Ó¦ŹÓ”░Ó”▓Ó¦ŗÓ”Ģ Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó¦ćÓ”░ Ó”»Ó¦ŗÓ”ŚÓ¦ŹÓ”» Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ēÓ”ĀÓ”▓?
Ó”ŚÓ¦ŗÓ”ŚÓ¦ŗÓ”▓Ó¦ćÓ”░ ŌĆśÓ”ĪÓ¦ćÓ”Ī Ó”ĖÓ¦ŗÓ”▓Ó¦ŹÓ”ĖŌĆÖ-Ó”ÅÓ”░ Ó”ÜÓ”┐Ó”ÜÓ”┐Ó”ĢÓ”Ł, Ó”¼Ó”ŠÓ”▓Ó”£Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ćÓ”░ ŌĆśÓ”ŚÓ”ŠÓ”¦Ó”ŠÓ”░ Ó”ÜÓ”ŠÓ”«Ó¦£Ó”ŠÓ”░ŌĆÖ Ó”©Ó”ŠÓ¦¤Ó”Ģ, Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”ŠÓ”░ ŌĆśÓ”åÓ”▓Ó”ŠÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”śÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó””Ó¦üÓ”▓Ó”ŠÓ”▓ŌĆÖ-Ó”ÅÓ”░ Ó”ĀÓ”ĢÓ”ÜÓ”ŠÓ”ÜÓ”Š Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”ÅÓ”ĢÓ”ć Ó”░Ó”ĢÓ”« Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”ĘÓźż Ó”ÅÓ”ć Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”£Ó”©, Ó”«Ó”▓ Ó”½Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”ĪÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖÓ”ĖÓ”╣ Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó”┐Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”» Ó”ÜÓ”░Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ēÓ”ĀÓ¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ÅÓ”░Ó”Š Ó”ĢÓ¦ćÓ”ēÓ”ć Ó”©Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ¦¤Ó”ć Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦éÓ”¬ Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐Ó”¦Ó”┐-Ó”¬Ó¦üÓ”░Ó¦üÓ”Ę Ó”¼Ó”Š Ó”©Ó”ŠÓ¦¤Ó”Ģ Ó”©Ó¦¤, Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”ÅÓ”░Ó”Š Ó”żÓ¦ŗ Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó”┐Ó”ĢÓ”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó¦ć Ó”¬Ó”░Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓźż
Ó”żÓ¦ćÓ”«Ó”©Ó”┐ Ó”ÅÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”¬Ó”░Ó¦ĆÓ”żÓ¦ć Ó”ÅÓ”ć Ó”▓Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó¦ć Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦éÓ”¬ Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¼Ó”▓ Ó”ÜÓ”░Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ēÓ”▓Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ō Ó”åÓ”øÓ¦ćÓźż Ó””Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ¦¤Ó¦ćÓ”ŁÓ¦ŹÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ”┐-Ó”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”Ė, Ó”żÓ”▓Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ¦¤-Ó”ÅÓ”░ Ó”åÓ”©Ó”Š Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”©Ó”┐Ó”©Ó”Š, Ó”░Ó”¼Ó¦ĆÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó¦ŹÓ”░Ó”©Ó”ŠÓ”źÓ¦ćÓ”░ Ó”ŚÓ¦ŗÓ”░Ó”Š Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¼Ó”▓ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Óźż Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ÜÓ”░Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”░Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”ć Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó”ĢÓ¦ć Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”żÓ¦üÓ”▓Ó¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”░ Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó¦Ć, Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó¦éÓ”▓Ó¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”ō Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”©Ó¦ĆÓźż
Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ć Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ćÓ”ć Ó”ĖÓ”¼Ó”ÜÓ¦ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ”┐ Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć, Ó”ĖÓ¦ć-Ó”ĖÓ”¼ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”ÜÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ćÓ”ć Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ĢÓ¦Ć Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░ Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”ĢÓ¦ćÓ”ō Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ŁÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”żÓ”┐ Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”¦Ó”░Ó”Š Ó”╣Ó¦¤ Ó”©Ó”Š, Ó”ĢÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ-Ó”ĖÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”żÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”« Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”½Ó”ĢÓ”©Ó”ŠÓ”░Ó”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó¦üÓ¦üÓ¦£Ó”┐Ó”øÓ¦ćÓ”ŠÓ”üÓ¦¤Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”░Ó”ŠÓ”¢Ó”Š Ó”╣Ó¦¤ Ó”«Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”░Óźż Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░ Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”ć Ó”»Ó””Ó”┐ Ó”ÅÓ”ć Ó”╣Ó”ŠÓ”▓, Ó”żÓ”ŠÓ”╣Ó”▓Ó¦ć Ó”¼Ó”┐Ó”░Ó”ŠÓ”¤ Ó”¬Ó¦āÓ”źÓ”┐Ó”¼Ó¦ĆÓ”░ Ó”¼Ó”ŠÓ”ĢÓ”┐ Ó”ĖÓ”¼ Ó”«Ó”╣Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”░Ó¦ŹÓ”ŚÓ”ż Ó”ģÓ”£Ó”ĖÓ¦ŹÓ”░ Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”£Ó”ĖÓ¦ŹÓ”░ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”ŠÓ¦¤ Ó”»Ó¦ć-Ó”▓Ó”ĢÓ¦ŹÓ”Ę Ó”▓Ó”ĢÓ¦ŹÓ”Ę Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”ō Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć Ó”ĖÓ¦ć-Ó”ĖÓ”¼ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ”ōÓ”żÓ”ŠÓ”░ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć, Ó”åÓ”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ģÓ”źÓ”Ü Ó”¬Ó¦āÓ”źÓ”┐Ó”¼Ó¦ĆÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė-Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”┐Ó”ÜÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”«Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”©Ó”┐Ó”░Ó”┐Ó”¢ Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Óźż Ó”ĖÓ¦ć-Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ć Ó”åÓ”¼Ó”ŠÓ”░ Ó”¼Ó¦üÓ”░Ó¦ŹÓ”£Ó¦ćÓ”ŠÓ¦¤Ó”Š Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”¼Ó”┐Ó”” Ó”åÓ”░ Ó”«Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĖÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦Ć Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”¼Ó”┐Ó””Ó”░Ó”Š Ó”ÅÓ”ĢÓ”«Ó”żÓźż
Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”ÅÓ”ĢÓ”ć Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”åÓ”øÓ¦ć Ó”¤Ó”©Ó”┐ Ó”«Ó”░Ó”┐Ó”ĖÓ”©, Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”¤Ó¦ćÓ”£Ó”ŠÓ”░, Ó”«Ó”ŠÓ”╣Ó”«Ó¦üÓ””Ó¦üÓ”▓ Ó”╣Ó”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ÜÓ”░Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”░Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓźż Ó”ĖÓ¦ć Ó”ÜÓ”░Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”░Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”ÅÓ”ĢÓ¦ćÓ”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”Š Ó”ÅÓ”ĢÓ”Š Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó”»Ó”ŠÓ”¬Ó”© Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”¦Ó¦ŹÓ”» Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć, Ó”»Ó¦ć-Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”© Ó”ÅÓ”ĢÓ”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”░Ó”ć Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Óźż Ó”ĖÓ¦ć-Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ČÓ”░Ó”┐Ó”Ģ Ó”╣Ó¦¤ Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”¬Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó”«Ó”¼Ó”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”£Ó”© Ó”«Ó¦üÓ”ĖÓ”▓Ó”«Ó”ŠÓ”©, Ó”åÓ”½Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”©Ó”ŠÓ”░Ó¦Ć Ó”ō Ó”╣Ó”┐Ó”¤Ó”▓Ó”ŠÓ¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó¦āÓ”╣Ó”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░ Ó”£Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”«Ó”ŠÓ”©Ó”┐Ó”░ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”ĢÓ”┐Ó”ČÓ¦ŗÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ¦ćÓ”ć Ó”«Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”ĖÓ¦ć-Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”ĖÓ”żÓ¦ŹÓ”» Ó”╣Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓźż Ó”«Ó”░Ó”┐Ó”ĖÓ”©, Ó”«Ó”ŠÓ”╣Ó”«Ó¦üÓ””Ó¦üÓ”▓ Ó”╣Ó”Ģ Ó”ō Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”¤Ó¦ćÓ”£Ó”ŠÓ”░ Ó”»Ó”¢Ó”© Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”▓Ó”┐Ó”¢Ó”øÓ¦ćÓ”© Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░Ó”Š Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ÜÓ”░Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”░Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”░ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”Č Ó”śÓ”¤Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”ŚÓ”ż Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”ŁÓ¦éÓ”żÓ”┐ Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”ĖÓ”╣Ó¦āÓ””Ó¦¤Ó”╣Ó¦āÓ””Ó¦¤Ó”ĖÓ”éÓ”¼Ó¦ćÓ””Ó¦Ć Ó”╣Ó”ōÓ¦¤Ó”Š Ó”É Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”░ Ó”öÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”Ģ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”ć Ó”©Ó¦¤Óźż Ó”ÅÓ”ć Ó”¬Ó”░Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”źÓ”┐Ó”żÓ”┐ Ó”ÅÓ”¢Ó”© Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė-Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”┐Ó”ż Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”ÜÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó”┐Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”» Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ōÓ”¤Ó”Š Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦¤Ó¦ŗÓ”£Ó”©Óźż Ó”¦Ó”©Ó”żÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”»Ó¦ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”£Ó¦ŹÓ”»Ó”żÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó¦ć Ó”░Ó¦éÓ”¬Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”░Ó”┐Ó”ż Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”»Ó”©Ó¦ŹÓ”ż Ó”½Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”©Ó”┐Ó”▓, Ó”ō ┬ĀÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”«Ó”żÓ”ŠÓ”¼Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”£Ó”©Ó¦ŹÓ”» Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ĖÓ”¼ Ó”¬Ó””Ó¦ŹÓ”¦Ó”żÓ”┐ Ó”ō Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”░Ó”ŠÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ¦¤Ó”żÓ¦ŹÓ”ż Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”½Ó¦ćÓ”▓Ó”▓, Ó”ō Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”░ Ó”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”»Ó”©Ó¦ŹÓ”ż Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”¬Ó””Ó¦ŹÓ”¦Ó”żÓ”┐ Ó”ō Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”ŚÓ”ŻÓ”żÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”░Ó”ō Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”źÓ”Ģ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”żÓ¦üÓ”▓Ó”▓, Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”£Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó””Ó¦ü-Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”Č Ó”¼Ó”øÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ćÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ć Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”ĘÓ”£Ó”©Ó”ĢÓ¦ć Ó”ģÓ”¦Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”© Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”£Ó¦ĆÓ”¼ Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ÅÓ”ć Ó”ĢÓ¦¤Ó¦ćÓ”Ģ Ó”¼Ó”øÓ”░ Ó”åÓ”ŚÓ¦ćÓ”ō Ó””Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”┐Ó”Ż Ó”åÓ”½Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ¦āÓ”ĘÓ¦ŹÓ”ŻÓ”ŠÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó”¼Ó”┐Ó”Ģ Ó”ģÓ”¦Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”øÓ”┐Ó”▓ Ó”©Ó”Š, Ó”©Ó”ŠÓ”ŚÓ”░Ó”┐Ó”Ģ Ó”ģÓ”¦Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”żÓ¦ŗ Ó””Ó¦éÓ”░Ó”ĖÓ¦ŹÓ”źÓ”ŠÓ”©Óźż Ó”óÓ”ŠÓ”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”żÓ”┐Ó””Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó¦üÓ¦£Ó¦ŗ Ó”åÓ”ÖÓ¦üÓ”▓ Ó”ĢÓ¦ćÓ”¤Ó¦ć Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š Ó”¼Ó”Š Ó”¬Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó”« Ó”åÓ”½Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó””Ó”ŠÓ”ĖÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”╣Ó”ŠÓ”żÓ¦ćÓ”░ Ó”żÓ¦ćÓ”▓Ó¦ŗ Ó”½Ó¦üÓ”¤Ó¦ŗ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”£Ó”ŠÓ”╣Ó”ŠÓ”£Ó¦ćÓ”░ Ó”¢Ó¦ŗÓ”▓Ó¦ć Ó”ŁÓ”░Ó¦ć Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”ČÓ¦ŹÓ”░Ó”«Ó”┐Ó”Ģ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”åÓ”ĖÓ”Š Ó”ģÓ”«Ó”ŠÓ”©Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”żÓ”ŠÓ¦¤ Ó”©Ó”ŠÓ¦ÄÓ”ĖÓ”┐Ó””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”©Ó”ĖÓ¦ćÓ”©Ó”¤Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”ČÓ”© Ó”ĢÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó¦ćÓ”░ Ó”ÜÓ”ŠÓ”ćÓ”żÓ¦ć Ó”ĢÓ”« Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ģÓ”¬Ó”░Ó”ŠÓ”¦ Ó”©Ó¦¤Óźż
Ó”¤Ó”©Ó”┐ Ó”«Ó”░Ó”┐Ó”ĖÓ”© Ó”»Ó”¢Ó”© Ó”ģÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”½Ó¦ŹÓ”░Ó¦ŗ-Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”© Ó”ģÓ”żÓ¦ĆÓ”ż Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó”Š Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”¤Ó¦ćÓ”£Ó”ŠÓ”░ Ó”»Ó”¢Ó”© Ó”ģÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ēÓ”ćÓ”źÓ”ĖÓ¦Ź-Ó”ÅÓ”░ Ó”ĢÓ”©Ó”ĖÓ¦ćÓ”©Ó”¤Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”ČÓ”© Ó”ĢÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”¬ Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó”Š Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”Ģ Ó”öÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”Ģ Ó”»Ó”¢Ó”© Ó”¬Ó”ŠÓ”ĢÓ”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”©-Ó”ĖÓ¦ćÓ”©Ó”ŠÓ”¼Ó”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”©Ó¦ĆÓ”░ Ó”©-Ó”«Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”░Ó¦ŹÓ”¼Ó”░Ó”żÓ”Š Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó¦ćÓ”©, Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”ĖÓ¦ćÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”©Ó¦Ć Ó”╣Ó¦¤ Ó”©Ó”Š, Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”Š Ó”¦Ó¦ŹÓ”¼Ó”éÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”©Ó¦Ć Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”©Ó”Š, Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”ĖÓ¦ćÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ōÓ”ĀÓ¦ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”¼Ó”┐Ó”©Ó”ŠÓ”ČÓ¦Ć Ó”ÅÓ”Ģ Ó”ĖÓ”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó¦ćÓ”«Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ČÓ”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”åÓ”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”«Ó”ŻÓ¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”©Ó¦ĆÓźż Ó”ō Ó”ĖÓ”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó¦ćÓ”«Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”£Ó¦¤Ó”ŚÓ”ŠÓ”źÓ”ŠÓźż
Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”¦Ó”©Ó”żÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”ō Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”Č Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó¦üÓ”░Ó¦ŹÓ”£Ó¦ćÓ”ŠÓ¦¤Ó”Š Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”┐Ó”Ģ Ó”ō Ó”«Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĖÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ĆÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”«Ó”ŠÓ”© Ó”åÓ”░ Ó”«Ó¦ćÓ”©Ó¦ć Ó”©Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤ Ó”©Ó”Š Ó”»Ó¦ć These hypotheses concern, on the one hand, the homology between the structure of the classical novel and the structure of exchange in the liberal economy, and on the other hand certain parallels in their later evolutions.
Ó”żÓ”┐Ó”©
Ó”ŚÓ¦ćÓ¦¤Ó”░Ó¦ŹÓ”Ś Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü, Ó”▓Ó¦üÓ”ĖÓ”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”ü Ó”ŚÓ¦ŗÓ”▓Ó¦ŹÓ”ĪÓ”«Ó”ŠÓ”©, Ó”ÅÓ”üÓ”░Ó”Š, Ó”¢Ó¦üÓ”¼Ó”ć Ó”ČÓ¦ŹÓ”░Ó””Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ćÓ¦¤ Ó”«Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĖÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦Ć Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”¼Ó”┐Ó””ŌĆö Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░Ó”Š Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼┬ĀÓ”ō Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó”¦Ó”ŠÓ”░Ó”ŻÓ”ŠÓ”░ Ó”ŁÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”żÓ”┐ Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”ĖÓ”éÓ”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”ż Ó”ĖÓ”«Ó”ĖÓ¦ŹÓ”ż Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”┐Ó”Ģ Ó”¦Ó”ŠÓ”░Ó”ŻÓ”ŠÓ”ć Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”ģÓ”ŁÓ”┐Ó”£Ó¦ŹÓ”×Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ŁÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”żÓ¦ćÓźż Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ć Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ćÓ”ć Ó”ĖÓ”¼Ó”ÜÓ¦ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ”┐ Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć, Ó”ĖÓ¦ć-Ó”ĖÓ”¼ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”ÜÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ćÓ”ć Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ĢÓ¦Ć Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░ Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”ĢÓ¦ćÓ”ō Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ŁÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”żÓ”┐ Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”¦Ó”░Ó”Š Ó”╣Ó¦¤ Ó”©Ó”Š, Ó”ĢÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ-Ó”ĖÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”żÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”« Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”½Ó”ĢÓ”©Ó”ŠÓ”░Ó”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó¦üÓ¦üÓ¦£Ó”┐Ó”øÓ¦ćÓ”ŠÓ”üÓ¦¤Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”░Ó”ŠÓ”¢Ó”Š Ó”╣Ó¦¤ Ó”«Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”░Óźż Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░ Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”ć Ó”»Ó””Ó”┐ Ó”ÅÓ”ć Ó”╣Ó”ŠÓ”▓, Ó”żÓ”ŠÓ”╣Ó”▓Ó¦ć Ó”¼Ó”┐Ó”░Ó”ŠÓ”¤ Ó”¬Ó¦āÓ”źÓ”┐Ó”¼Ó¦ĆÓ”░ Ó”¼Ó”ŠÓ”ĢÓ”┐ Ó”ĖÓ”¼ Ó”«Ó”╣Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”░Ó¦ŹÓ”ŚÓ”ż Ó”ģÓ”£Ó”ĖÓ¦ŹÓ”░ Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”£Ó”ĖÓ¦ŹÓ”░ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”ŠÓ¦¤ Ó”»Ó¦ć-Ó”▓Ó”ĢÓ¦ŹÓ”Ę Ó”▓Ó”ĢÓ¦ŹÓ”Ę Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”ō Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć Ó”ĖÓ¦ć-Ó”ĖÓ”¼ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ”ōÓ”żÓ”ŠÓ”░ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć, Ó”åÓ”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ģÓ”źÓ”Ü Ó”¬Ó¦āÓ”źÓ”┐Ó”¼Ó¦ĆÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė-Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”┐Ó”ÜÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”«Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”©Ó”┐Ó”░Ó”┐Ó”¢ Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Óźż Ó”ĖÓ¦ć-Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ć Ó”åÓ”¼Ó”ŠÓ”░ Ó”¼Ó¦üÓ”░Ó¦ŹÓ”£Ó¦ćÓ”ŠÓ¦¤Ó”Š Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”¼Ó”┐Ó”” Ó”åÓ”░ Ó”«Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĖÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦Ć Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”¼Ó”┐Ó””Ó”░Ó”Š Ó”ÅÓ”ĢÓ”«Ó”żÓźż Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ŁÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”© Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”ŠÓ¦¤ Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó”¼Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”░Ó¦Ć Ó”¦Ó”©Ó”żÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”£Ó¦£Ó”┐Ó”ż Ó”¼Ó”┐Ó”ŁÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”© Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”ĘÓ¦ćÓ”░ Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”© Ó”»Ó¦ćÓ”«Ó”© Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ōÓ”ĀÓ¦ć, Ó”żÓ¦ćÓ”«Ó”©Ó”┐ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”¼Ó¦āÓ”╣Ó”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░ Ó”¬Ó¦āÓ”źÓ”┐Ó”¼Ó¦ĆÓ”░ Ó”©Ó”ŠÓ”©Ó”Š Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”ŠÓ”░ Ó”©Ó”ŠÓ”©Ó”Š Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ”┐Ó”ż Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”£, Ó”ō Ó”©Ó”ŠÓ”©Ó”Š Ó”¼Ó”┐Ó”ÜÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”¬Ó””Ó¦ŹÓ”¦Ó”żÓ”┐Ó”żÓ¦ć Ó”ČÓ¦ŗÓ”ĘÓ”┐Ó”ż Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”ĘÓ”£Ó”©Ó”ō Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤ Ó”╣Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓźż Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”»Ó”ŠÓ¦¤Ó¦Ć Ó”żÓ”ŠÓ”░Ó”Š Ó””Ó¦üÓ”£Ó”©Ó”ć Ó”╣Ó”┐Ó”░Ó¦ŗ Ó”¼Ó”Š Ó”©Ó”ŠÓ¦¤Ó”ĢÓźż Ó”ÅÓ”ć Ó””Ó¦üÓ”£Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”£Ó”© Ó”»Ó¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŁÓ¦ü Ó”ō Ó”åÓ”░Ó¦ćÓ”ĢÓ”£Ó”© Ó”»Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŁÓ¦üÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ČÓ”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ŌĆö Ó”ÅÓ”ć Ó”¼Ó¦łÓ”¬Ó”░Ó¦ĆÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ĆÓ”ĢÓ¦āÓ”żÓ”┐ Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ć Ó”©Ó¦ćÓ”ćÓźż Ó”¦Ó”©Ó”żÓ”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”Ģ Ó”ģÓ”░Ó¦ŹÓ”źÓ”©Ó¦ĆÓ”żÓ”┐, Ó”»Ó”ŠÓ”░ Ó”åÓ”░-Ó”ÅÓ”Ģ Ó”©Ó”ŠÓ”« Ó”ēÓ””Ó”ŠÓ”░-Ó”ģÓ”░Ó¦ŹÓ”źÓ”©Ó¦ĆÓ”żÓ”┐, Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”©Ó”ŠÓ”©Ó”Š Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”©Ó”ŠÓ”©Ó”Š Ó”¦Ó”░Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”»Ó¦ć Ó”«Ó”┐Ó”▓ Ó”▓Ó¦üÓ”ĖÓ”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”ü Ó”ŚÓ¦ŗÓ”▓Ó¦ŹÓ”ĪÓ”«Ó”ŠÓ”© Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”«Ó”ŠÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”ēÓ”¬Ó”ĖÓ¦ŹÓ”źÓ”┐Ó”ż Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©, Ó”ĖÓ¦ćÓ”¤Ó”Š Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¢Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤ Ó”¬Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ŚÓ¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż
Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”ō Ó”żÓ¦ŗ Ó”©Ó”©Ó¦ŹÓ””Ó”©Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░Ó”ć Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”░Ó¦ŹÓ”ŚÓ”żÓźż Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ć Ó”¬Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó”« Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”åÓ”¦Ó”┐Ó”¬Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”ŠÓ”” Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”¼Ó¦üÓ”░Ó¦ŹÓ”£Ó¦ćÓ”ŠÓ¦¤Ó”Š Ó”¼Ó”┐Ó”¬Ó¦ŹÓ”▓Ó”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”╣Ó”żÓ¦ŹÓ”żÓ”« Ó””Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ČÓ”©Ó”┐Ó”Ģ Ó”╣Ó¦ćÓ”ŚÓ¦ćÓ”▓-Ó”ÅÓ”░ Ó”©Ó¦ćÓ”żÓ¦āÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓźż
Ó”╣Ó¦ćÓ”ŚÓ¦ćÓ”▓-Ó”ÅÓ”░ Ó”«Ó¦āÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦üÓ”░ Ó”¬Ó”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”ŠÓ”ČÓ”┐Ó”ż Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ ŌĆśÓ”▓Ó¦ćÓ”ĢÓ”ÜÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”Ė Ó”ģÓ”© Ó”ÅÓ”ĖÓ”źÓ¦ćÓ”¤Ó”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĖŌĆÖ (Ó¦¦Ó¦«Ó¦¦Ó¦«)-ӔŠӔżÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”╣Ó¦ŹÓ”» Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”░Ó”ŻÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”żÓ”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”ĢÓ”Š Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”╣Ó¦ćÓ”ŚÓ¦ćÓ”▓ Ó”ÅÓ”ć Ó”¼Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ¦āÓ”żÓ”ŠÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤ Ó”ō Ó”åÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ”┐Ó”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó”ÉÓ”ĢÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░ Ó”£Ó¦ŗÓ”░ Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©ŌĆö Ó”ÅÓ”ć Ó”ÉÓ”ĢÓ¦ŹÓ”» Ó”ĢÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ÖÓ”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”©Ó”Š, Ó”ĖÓ¦īÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó”░Ó¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”ĢÓ¦üÓ¦ÄÓ”ĖÓ”┐Ó”ż Ó”¦Ó”ŠÓ”░Ó”ŻÓ”ŠÓ”ć Ó”ĖÓ¦īÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó”░Ó¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”ĢÓ¦üÓ¦ÄÓ”ĖÓ”┐Ó”ż Ó”åÓ”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓźż Ó”╣Ó¦ćÓ”ŚÓ¦ćÓ”▓ Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©, ŌĆśÓ”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó”¤Ó”┐Ó”ć Ó”åÓ”ĢÓ”ŠÓ”░ÓźżŌĆÖ Ó”åÓ”░Ó¦ŗ Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©, ŌĆśÓ”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó””Ó¦ŗÓ”Ę Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ćÓ”ć Ó”åÓ”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó””Ó¦ŗÓ”Ę Ó”śÓ”¤Ó¦ćÓźżŌĆÖ Ó”ÅÓ”ć Ó”¢Ó”ŠÓ”░Ó”ŠÓ”¬ Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤ Ó”ō Ó”¢Ó”ŠÓ”░Ó”ŠÓ”¬ Ó”åÓ”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ēÓ””Ó”ŠÓ”╣Ó”░Ó”Ż Ó””Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”ŚÓ”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”╣Ó¦ćÓ”ŚÓ¦ćÓ”▓ Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©, ŌĆśÓ”ÜÓ”┐Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”▓Ó¦ŗÓ”ĢÓ”░Ó”Š, Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”żÓ¦ĆÓ¦¤Ó”░Ó”Š, Ó”ćÓ”£Ó”┐Ó”¬Ó¦ŹÓ”¤Ó¦ćÓ”░ Ó”▓Ó¦ŗÓ”ĢÓ”£Ó”© Ó”ĢÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ Ó”»Ó”źÓ”ŠÓ”»Ó”ź Ó”ĖÓ¦īÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó”░Ó¦ŹÓ”» Ó”åÓ”üÓ”ĢÓ”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”©Ó”┐Óźż Ó”żÓ”ŠÓ”░Ó”Š Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó””Ó¦ćÓ”¼Ó””Ó¦ćÓ”¼Ó¦ĆÓ”░ Ó”»Ó¦ć-Ó”ĖÓ”¼ Ó”øÓ”¼Ó”┐ Ó”ō Ó”«Ó¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”żÓ”┐ Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ć, Ó”ĖÓ¦ćÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”╣Ó¦¤ Ó”åÓ”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”╣Ó¦ĆÓ”© Ó”ģÓ”źÓ”¼Ó”Š Ó”åÓ”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”«Ó”┐Ó”źÓ¦ŹÓ”»Ó”Š Ó”ō Ó”ŁÓ¦¤Ó”ÖÓ¦ŹÓ”ĢÓ”░ Ó”ÜÓ¦ćÓ”╣Ó”ŠÓ”░Ó”ŠÓźżŌĆÖ
Ó”╣Ó¦ćÓ”ŚÓ¦ćÓ”▓ Ó”»Ó”¢Ó”© Ó”ÅÓ”ć Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©, Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”ĢÓ”▓Ó”ĢÓ”ŠÓ”żÓ”ŠÓ”░ ŌĆśÓ”ÅÓ”ČÓ”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”¤Ó”┐Ó”Ģ Ó”ĖÓ¦ŗÓ”ĖÓ”ŠÓ”ćÓ”¤Ó”┐ŌĆÖÓ”░ Ó”¼Ó¦¤Ó”Ė Ó¦½Ó¦” Ó”¬Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ŚÓ¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”ō Ó”»Ó¦ć-Ó”ĖÓ”¼ Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó¦ćÓ”¼Ó”¬Ó”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ”┐Ó”żÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ”«Ó”░Ó”Š Ó”¬Ó”░Ó”¼Ó”░Ó¦ŹÓ”żÓ¦Ć Ó”ĢÓ”ŠÓ”▓Ó¦ć ŌĆśÓ”ģÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”©Ó¦ŹÓ”¤Ó”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤ŌĆÖ Ó”¼Ó”▓Ó”¼, Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░Ó”Š Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ć Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”żÓ¦ĆÓ¦¤ Ó”ō Ó”ćÓ”£Ó”┐Ó”¬Ó¦ŹÓ”¤Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”źÓ”ŠÓ”¬Ó”żÓ¦ŹÓ”», Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”ŠÓ”▓Ó”ÜÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”░, Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ”░Ó¦ŹÓ”», Ó”ÜÓ”┐Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬, Ó”ćÓ”£Ó”┐Ó”¬Ó¦ŹÓ”¤Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”¦Ó”┐Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬ŌĆö Ó”ÅÓ”ć Ó”ĖÓ”¼ Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦üÓ”░ Ó”©Ó”┐Ó””Ó”░Ó¦ŹÓ”ČÓ”© Ó””Ó¦ćÓ”¢Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó¦ćÓ¦£Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż
Ó”╣Ó¦ćÓ”ŚÓ¦ćÓ”▓-Ó”ÅÓ”░ Ó”©Ó”©Ó¦ŹÓ””Ó”©Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó”Ģ Ó”¼Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ¦āÓ”żÓ”ŠÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó¦ŗÓ”ØÓ”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤ŌĆö Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”ĖÓ¦ć-Ó”ĖÓ”¼ Ó”¢Ó”¼Ó”░Ó”ć Ó”£Ó”ŠÓ”©Ó”żÓ¦ćÓ”© Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”©Ó”ŠÓ”ć Ó”£Ó”ŠÓ”©Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”żÓ”źÓ¦ŹÓ”» Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”ČÓ”ĢÓ”żÓ”ŠÓ”░Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”»Ó¦ć-Ó”ĖÓ”¼ Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”åÓ”«Ó”░Ó”Š Ó”ČÓ¦üÓ”©Ó¦ćÓ”øÓ”┐ Ó”¬Ó”░Ó¦ć, Ó”ĖÓ¦ć-Ó”ĖÓ”¼ Ó”åÓ”£Ó”ŚÓ¦üÓ”¼Ó”┐ Ó”ĀÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ō Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”ģÓ”źÓ¦ŹÓ”»Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ”ŁÓ”░ Ó”©Ó¦¤ Ó”ÅÓ”¤Ó”ŠÓ”ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”«Ó”ŠÓ”ŻÓ”┐Ó”ż Ó”╣Ó¦¤Óźż
Ó¦¦Ó¦«Ó¦¦Ó¦«-Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”ŠÓ”ČÓ”┐Ó”ż Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ ŌĆśÓ”©Ó”©Ó¦ŹÓ””Ó”©Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó”Ģ Ó”¼Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ¦āÓ”żÓ”ŠŌĆÖÓ¦¤ Ó”╣Ó¦ćÓ”ŚÓ¦ćÓ”▓ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”░Ó”ŻÓ¦ćÓ”░ Ó”»Ó¦ć-Ó”żÓ”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”ĢÓ”Š Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©, Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓ Ó”øÓ”┐Ó”▓ Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ģÓ”źÓ”Ü Ó”żÓ”żÓ””Ó”┐Ó”©Ó¦ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”░Ó”ŁÓ¦ćÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ćÓ”Ė-Ó”ÅÓ”░ ŌĆśÓ”ĪÓ”© Ó”ĢÓ¦üÓ”ćÓ”ĢÓ”£Ó¦ŗÓ”¤ŌĆÖ Ó”¼Ó”ć-Ó”åÓ”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”ć Ó¦©Ó¦¦Ó¦® Ó”¼Ó”øÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦üÓ”░Ó”©Ó¦ŗ, Ó”░ŌĆīÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¼Ó”▓Ó¦ć-Ó”░ ŌĆśÓ”ŚÓ”ŠÓ”░Ó”ŚÓ”ŠÓ”©Ó”¤Ó¦üÓ¦¤Ó”Š-Ó”░Ó”ō Ó”ÅÓ”ĢÓ”Č Ó”¼Ó”øÓ”░ Ó”¬Ó”ŠÓ”░ Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”▓Ó¦ćÓ”░Ó”«Ó”©Ó”żÓ¦ŗÓ”Ł-Ó”ÅÓ”░ Ó”©Ó”ŠÓ¦¤Ó”Ģ Ó”ĢÓ”ĢÓ¦ćÓ”ČÓ”ŠÓ”ĖÓ¦ć Ó”śÓ¦üÓ”░Ó¦ć Ó”¼Ó¦ćÓ¦£Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć, ┬ĀÓ”¬Ó¦üÓ”ČÓ”ĢÓ”┐Ó”©-Ó”ÅÓ”░ Ó”½Ó¦ćÓ”░Ó”ŠÓ”░ Ó”«Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”©Ó”░Ó”Š Ó”«Ó”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ¦ŗ Ó”ō Ó”ĖÓ¦ćÓ”©Ó¦ŹÓ”¤ Ó”¬Ó”┐Ó”¤Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖÓ”¼Ó¦üÓ”░Ó¦ŹÓ”Ś-Ó”ÅÓ”░ Ó”¼Ó¦£Ó”▓Ó¦ŗÓ”ĢÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó¦łÓ”ĀÓ”ĢÓ”¢Ó”ŠÓ”©Ó”ŠÓ¦¤ Ó”óÓ¦üÓ”ĢÓ¦ć Ó”¬Ó¦£Ó¦ćÓ”øÓ¦ć, Ó”ŚÓ¦ŗÓ”ŚÓ¦ŗÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”░Ó”Š Ó””Ó”ŠÓ”ĖÓ”░Ó”Š Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”▓Ó¦ŗÓ”Ģ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć Ó”ō Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”░Ó”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”ČÓ”╣Ó”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”▓Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”¤ Ó”¬Ó¦ćÓ”░Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”░Ó”Š Ó”żÓ”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”üÓ”¦ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ĢÓ¦ćÓ”░Ó”ŠÓ”©Ó”┐Ó”░ Ó”ŁÓ¦éÓ”żÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”ČÓ¦üÓ”¦Ó¦üÓ”ć Ó”ōÓ”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”ĢÓ¦ŗÓ”¤Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”¢Ó¦üÓ”▓Ó¦ć Ó”©Ó”┐Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ćÓźż
Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ćÓ”ć Ó”»Ó¦ć Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬-Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć Ó”╣Ó¦ćÓ”ŚÓ¦ćÓ”▓ Ó”żÓ”ŠÓ”░Ó”ō Ó”¢Ó”░Ó”¼ Ó”░Ó”ŠÓ”¢Ó”żÓ¦ćÓ”© Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”©Ó”ŠÓ”ć Ó”░Ó”ŠÓ”¢Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”żÓ¦ŗ Ó”¼Ó¦üÓ”ØÓ”żÓ¦ćÓ”ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”©Ó”©Ó”┐ ŌĆśÓ”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓ŌĆÖ Ó”¼Ó”Š ŌĆśÓ”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬ŌĆÖ Ó”¼Ó”▓Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”Ż Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”░Ó”Ż Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ēÓ”ĀÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”»Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”ĢÓ¦üÓ¦ÄÓ”ĖÓ”┐Ó”ż Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤ Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©ŌĆö Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ÜÓ¦üÓ”░Ó”┐, Ó”£Ó¦ŗÓ”ÜÓ¦ŹÓ”ÜÓ¦üÓ”░Ó”┐, Ó”«Ó¦ćÓ¦¤Ó¦ćÓ”¼Ó”ŠÓ”£Ó”┐, Ó”ĢÓ¦ćÓ”░Ó”ŠÓ”©Ó”┐Ó”ŚÓ”┐Ó”░Ó”┐, Ó”«Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”©Ó”┐ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ēÓ”ĀÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”¼Ó¦üÓ”░Ó¦ŹÓ”£Ó¦ćÓ”ŠÓ¦¤Ó”Š Ó”¼Ó”┐Ó”¬Ó¦ŹÓ”▓Ó”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”┐Ó”Ģ Ó”ŚÓ¦üÓ”░Ó¦ü Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó¦ćÓ”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”Ė-Ó”ĖÓ”«Ó”żÓ¦üÓ”▓Ó¦ŹÓ”» Ó”ÅÓ”░Ó¦ŗÓ”Ė-Ó”ÅÓ”źÓ¦ŗÓ”Ė-Ó”ÅÓ”░ Ó”©Ó”┐Ó”░Ó”┐Ó”¢ Ó”åÓ”░Ó¦ŗÓ”¬ Ó”ĢÓ”░Ó”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”żÓ”ż Ó””Ó”┐Ó”©Ó¦ć Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ĖÓ”¼ Ó”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”Ģ Ó”åÓ””Ó”░Ó¦ŹÓ”Č Ó”żÓ¦ŗ Ó”▓Ó¦ŗÓ”¬Ó”ŠÓ”¤ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ŚÓ¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”åÓ”¦Ó¦üÓ”©Ó”┐Ó”Ģ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”░Ó”Ż Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ēÓ”ĀÓ¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”ō Ó”ēÓ”ĀÓ”¼Ó¦ćŌĆö Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓, Ó”¢Ó”¼Ó”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”ŚÓ”£, Ó”ĖÓ”┐Ó”©Ó¦ćÓ”«Ó”Š, Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó¦ćÓ”ĪÓ”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”«Ó¦ć Ó”¢Ó¦ćÓ”▓Ó”Š Ó”ō Ó”©Ó”ŠÓ”¤Ó”Ģ, Ó”ćÓ”▓Ó¦ćÓ”ĢÓ”¤Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”Ģ Ó”åÓ”▓Ó¦ŗ, Ó”¦Ó¦ĆÓ”░Ó¦ć-Ó”¦Ó¦ĆÓ”░Ó¦ć Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”ĖÓ”¼ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”░Ó”ŻÓ¦ćÓ”░ Ó”£Ó”©Ó¦ŹÓ”« Ó””Ó”┐Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”▓Ó”┐Ó”© Ó”ģÓ”▓Ó”┐Ó”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”┐Ó”ĢÓ¦ćÓ”ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”« Ó”╣Ó”┐Ó”¤Ó”▓Ó”ŠÓ”░ Ó”«Ó”ŠÓ”¤Ó”┐ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ēÓ¦ÄÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”┐Ó”¬Ó¦ŹÓ”ż Ó”ĖÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ÜÓ”▓Ó”ŠÓ”ćÓ”¤Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”▓Ó”ŠÓ¦¤ Ó”ĖÓ”ŠÓ”£Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó””Ó¦üÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”ŁÓ¦£Ó”ĢÓ¦ć Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó¦ćÓ”░ Ó”©Ó”┐Ó”ŁÓ¦āÓ”ż Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”ÜÓ”░Ó¦ŹÓ”ÜÓ”Š Ó”¼Ó””Ó”▓Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć Ó”¬Ó”░Ó”┐Ó”¼Ó”░Ó¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”ż Ó”¤Ó¦ćÓ”ĢÓ”©Ó¦ŗÓ”▓Ó”£Ó”┐Ó”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć-Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ćÓźż Ó”øÓ”ŠÓ”¬Ó”ŠÓ”¢Ó”ŠÓ”©Ó”ŠÓ¦¤ Ó”¼Ó”ć Ó”øÓ”ŠÓ”¬Ó”Š Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć Ó”╣Ó”ŠÓ”£Ó”ŠÓ”░ Ó”╣Ó”ŠÓ”£Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”¬Ó”┐Óźż Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó”ć Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”åÓ”¦Ó¦üÓ”©Ó”┐Ó”Ģ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”« Ó”©Ó”┐Ó””Ó”░Ó¦ŹÓ”ČÓ”©Óźż Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”©Ó”©Ó¦ŹÓ””Ó”©Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”╣Ó””Ó”┐Ó”Č Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”©Ó”┐Óźż
Ó”ÜÓ”ŠÓ”░
Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓ”¤Ó”Š Ó”åÓ”ÜÓ”«Ó”ĢÓ”Š Ó”ČÓ¦üÓ”©Ó”żÓ¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó¦ü Ó”¦Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĢÓ”Š Ó”▓Ó”ŠÓ”ŚÓ”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓźż Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ćÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”Ė Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¦Ó”ŠÓ”©Ó”ż Ó”ćÓ”éÓ”░Ó¦ćÓ”£Ó”┐ Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ćÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”ĀÓ”ŠÓ”«Ó¦ŗÓ”żÓ¦ćÓ”ć Ó”»Ó¦ć-Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó¦ć Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć, Ó”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”¦Ó”ŠÓ”░Ó”ŻÓ”Š Ó”żÓ¦ŗ Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ŁÓ”┐Ó”żÓ”░ Ó”¼Ó””Ó¦ŹÓ”¦Ó”«Ó¦éÓ”▓, Ó”»Ó¦ć Ó”ćÓ”éÓ”░Ó¦ćÓ”£Ó””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”ø Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ćÓ”ć Ó”åÓ”«Ó”░Ó”Š Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”ČÓ”┐Ó”¢Ó¦ćÓ”øÓ”┐ Ó”ō Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó¦ćÓ”¼Ó””Ó¦ćÓ”░ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”¬Ó”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”¬Ó¦£Ó¦ć-Ó”¬Ó¦£Ó¦ćÓ”ć Ó”åÓ”«Ó”░Ó”Š Ó”ÜÓ”┐Ó”░Ó”ĢÓ”ŠÓ”▓ Ó”£Ó¦ćÓ”©Ó¦ć Ó”åÓ”ĖÓ”øÓ”┐ Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¦Ó”ŠÓ”© Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó¦ćÓ”░ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”░Ó”Ż Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”ć Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓ Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć, Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”Š Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó”ōÓźż
Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”Š Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”ČÓ¦üÓ”░Ó¦ü Ó”╣Ó”ōÓ¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”¤Ó”Š Ó”åÓ”«Ó”░Ó”Š Ó”¬Ó”░Ó¦ć Ó”åÓ”▓Ó¦ŗÓ”ÜÓ”©Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó”¼ Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”åÓ”¬Ó”ŠÓ”żÓ”ż Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ”░Ó¦ŗ Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”ĖÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ¦ŹÓ”» Ó”╣Ó”ŠÓ”£Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”╣Ó”¼Ó¦ćŌĆö Ó”ÅÓ”ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”źÓ”«Ó”┐Ó”Ģ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”¬Ó”ŠÓ””Ó¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ¦ć Ó”»Ó¦ć Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”»Ó”¢Ó”© Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ”┐Ó”▓ Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”░Ó”Ż Ó”¼Ó¦üÓ”ØÓ¦ć Ó”ēÓ”ĀÓ”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”©Ó”┐Óźż
Ó”╣Ó¦ćÓ”ŚÓ¦ćÓ”▓-Ó”ÅÓ”░ Ó”¬Ó”░ Ó”ŚÓ¦ćÓ¦¤Ó”░Ó¦ŹÓ”Ś Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü-Ó”ÅÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó””Ó¦āÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”ż Ó”©Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š Ó”»Ó”ŠÓ”Ģ Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”Ż Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”┐Ó”ż Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”Ģ Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©-Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”░Ó”ŻÓ”ŠÓ”░ Ó”åÓ””Ó”┐Ó”¬Ó¦üÓ”░Ó¦üÓ”ĘÓźż
Ó¦¦Ó¦»Ó¦©Ó¦”-ӔŠӔ▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”ÜÓ¦ćÓ”░ ŌĆśÓ””Ó”┐ Ó”źÓ”┐Ó¦¤Ó”░Ó”┐ Ó”ģÓ”Ł Ó””Ó”┐ Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓ŌĆÖ Ó”¼Ó”ćÓ”¤Ó”┐ Ó”¼Ó¦ćÓ”░Ó¦¤Óźż Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”åÓ”ŚÓ¦ć Ó¦¦Ó¦»Ó¦¦Ó¦¬ Ó”ō Ó¦¦Ó¦»Ó¦¦Ó¦¼-Ó”żÓ¦ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”¤Ó”┐ Ó”¬Ó”żÓ¦ŹÓ”░-Ó”¬Ó”żÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ¦¤ Ó”¼Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó¦¦Ó¦»Ó¦¼Ó¦©-Ó”░ Ó”£Ó¦üÓ”▓Ó”ŠÓ”ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó”ćÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”ĖÓ”éÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ”░Ó”ŻÓ¦ćÓ”░ Ó”ŁÓ¦éÓ”«Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ¦¤ Ó”ŚÓ¦ćÓ¦¤Ó”░Ó¦ŹÓ”Ś Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü Ó”¼Ó”ćÓ”¤Ó”┐ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”░ Ó”ćÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”Ė, Ó”żÓ¦ÄÓ”ĢÓ”ŠÓ”▓Ó¦ĆÓ”© Ó”«Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĖÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦Ć Ó”ō Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”ģÓ”«Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĖÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ĆÓ”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░ Ó”ÅÓ”ć Ó”¼Ó”ćÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼ Ó”ō Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó”Š Ó”ō Ó”¼Ó”ćÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”¬Ó”░Ó”┐Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”┐Ó”ż Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”Ģ Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ŁÓ¦éÓ”«Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó””Ó¦üÓ”ć-Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”£Ó”ŠÓ¦¤Ó”ŚÓ”Š Ó”ÅÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ”┐Ó”ĢÓźż Ó”»Ó¦ćÓ”«Ó”©, Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü Ó”¼Ó”▓Ó”øÓ¦ćÓ”©, ŌĆśÓ””Ó”┐ Ó”źÓ”┐Ó¦¤Ó”░Ó”┐ Ó”ģÓ”¼ Ó””Ó”┐ Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓ŌĆÖ Ó”¼Ó”ćÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”ĖÓ”ŠÓ”¦Ó”ŠÓ”░Ó”Ż Ó”¬Ó””Ó¦ŹÓ”¦Ó”żÓ”┐Ó”ŚÓ”ż Ó”åÓ””Ó”░Ó¦ŹÓ”Č Ó”╣Ó¦ćÓ”ŚÓ¦ćÓ”▓Óźż Ó”©Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó”©Ó”┐Ó”Ģ Ó”ō Ó””Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ČÓ”©Ó”┐Ó”Ģ Ó””Ó”┐Ó”Ģ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”╣Ó¦ćÓ”ŚÓ¦ćÓ”▓-Ó”ÅÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”¼Ó”ćÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”¼Ó”┐Ó”░Ó¦ŗÓ”¦Ó”┐Ó”żÓ”Š Ó”©Ó¦ćÓ”ćÓźż Ó”»Ó¦ćÓ”¤Ó¦üÓ”ĢÓ¦ü Ó”¼Ó”┐Ó”░Ó¦ŗÓ”¦Ó”┐Ó”żÓ”Š Ó”żÓ”Š Ó”ČÓ¦üÓ”¦Ó¦üÓ”ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó”┐Ó”ĢÓźż Ó”åÓ”░-Ó”ÅÓ”Ģ Ó”£Ó”ŠÓ¦¤Ó”ŚÓ”ŠÓ¦¤ Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü Ó”¼Ó”▓Ó”øÓ¦ćÓ”©, ŌĆśÓ”åÓ”«Ó”┐ Ó”»Ó””Ó¦ŹÓ””Ó¦üÓ”░ Ó”¼Ó¦üÓ”ØÓ”┐ Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”¼Ó”▓Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó”┐, Ó””Ó”┐ Ó”źÓ”┐Ó¦¤Ó”░Ó”┐ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”« Ó”£Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”«Ó”ŠÓ”© Ó”¼Ó”ć Ó”»Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”©Ó¦ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”Ģ Ó”¼Ó”┐Ó”¬Ó¦ŹÓ”▓Ó”¼Ó”«Ó¦üÓ”¢Ó¦Ć Ó”¼Ó”ŠÓ”«Ó”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”źÓ¦Ć Ó”©Ó¦ĆÓ”żÓ”┐ Ó”ō Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ÉÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó¦ŹÓ”»Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”«Ó”ż Ó”ō Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ÜÓ”▓Ó”┐Ó”ż Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ¦ŹÓ”» Ó”«Ó¦ćÓ”▓Ó”ŠÓ”©Ó¦ŗ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźżŌĆÖ
Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”ÜÓ¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ć Ó”¦Ó”ŠÓ”░Ó”ŻÓ”ŠÓ”¤Ó”┐ Ó”»Ó”źÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”źÓźż Ó”ÅÓ”ć Ó”¼Ó”ćÓ¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”żÓ”ŠÓ”ć Ó””Ó¦üÓ”¤Ó”┐ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ŚÓźż Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”« Ó”ŁÓ”ŠÓ”ŚŌĆö ŌĆśÓ”żÓ¦ÄÓ”ĢÓ”ŠÓ”▓Ó¦ĆÓ”© Ó”ĖÓ”ŁÓ¦ŹÓ”»Ó”żÓ”Š Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ”żÓ”┐Ó”¬Ó¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”Ż Ó”©Ó”Š Ó”ĖÓ”éÓ”ĢÓ”¤Ó”¬Ó¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”Ż Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ČÓ¦ŹÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó¦ĆÓ”«Ó”ŠÓ”éÓ”ĖÓ”ŠÓ¦¤ Ó”«Ó”╣Ó”ŠÓ”© Ó”ÅÓ”¬Ó”┐Ó”Ģ Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ŁÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”© Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ÓźżŌĆÖ Ó””Ó¦ŹÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ¦ĆÓ¦¤ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ŚŌĆö ŌĆśÓ”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”░Ó”ŻÓ¦ćÓ”░ Ó”ÜÓ”░Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”ĖÓ”©Ó¦ŹÓ”¦Ó”ŠÓ”©ÓźżŌĆÖ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”« Ó”ŁÓ”ŠÓ”ŚÓ¦ćŌĆö Ó”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”Ė, Ó”¢Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó”ŠÓ”© Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«, Ó”¼Ó”┐Ó”ŁÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”© Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó”ĖÓ¦ŹÓ”»Ó”Š, Ó”ÅÓ”¬Ó”┐Ó”Ģ Ó”ō Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓, Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”ŁÓ”┐Ó”żÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ŚÓ”ĀÓ”©, Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”ÉÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”Ģ-Ó””Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ČÓ”©Ó”┐Ó”Ģ Ó”åÓ”¼Ó”╣ŌĆö Ó”ÅÓ”ć Ó”¬Ó”ŠÓ”üÓ”ÜÓ”¤Ó”┐ Ó”¬Ó”░Ó”┐Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ćÓ””Óźż Ó””Ó¦ŹÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ¦ĆÓ¦¤ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ŚÓ¦ćŌĆö Ó”¼Ó”┐Ó”«Ó¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”ż Ó”åÓ””Ó”░Ó¦ŹÓ”ČÓ”¼Ó”ŠÓ””, Ó”░Ó¦ŗÓ”«Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”¤Ó”┐Ó”ĖÓ”┐Ó”£Ó”«Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”¬Ó¦ŹÓ”©Ó”ŁÓ”ÖÓ¦ŹÓ”Ś, Ó”ŚÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”¤Ó¦ćÓ”░ Ó”ēÓ”ćÓ”▓Ó”╣Ó¦ćÓ”▓Ó”« Ó”«Ó¦ćÓ”ćÓ”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó”ŠÓ”░Ó”Ė-Ó”ÅÓ”░ Ó”ČÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”ŠÓ”©Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ”┐Ó”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”¼, Ó”żÓ”▓Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ¦¤ Ó”ō Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó”ĖÓ”éÓ”ŚÓ”ĀÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”╣Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦üÓ”¢ŌĆö Ó”ÅÓ”ć Ó”ÜÓ”ŠÓ”░Ó”¤Ó”┐ Ó”¬Ó”░Ó”┐Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ćÓ””Óźż Ó”¬Ó¦āÓ”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”ŠÓ”░ Ó””Ó”┐Ó”Ģ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”« Ó”ŁÓ”ŠÓ”ŚÓ”¤Ó”┐ Ó””Ó¦ŹÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ¦ĆÓ¦¤ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ŚÓ¦ćÓ”░ Ó””Ó¦ćÓ¦£Ó”ŠÓźż Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”¼Ó¦ŗÓ”ØÓ”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤, Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ĆÓ”© Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░, Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¦Ó”ŠÓ”©Ó”ż Ó”ÅÓ”¬Ó”┐Ó”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”éÓ”»Ó¦ŗÓ”ŚÓ”ĖÓ¦éÓ”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ĆÓ”© Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦üÓ”©Ó”░Ó¦ŹÓ”¬Ó”ŠÓ”ĀÓ¦ć Ó”¼Ó”Š Ó”¬Ó¦üÓ”©Ó”░Ó¦ŹÓ”ŚÓ”ĀÓ”©Ó¦ć Ó”»Ó”żÓ¦ŹÓ”«Ó”ČÓ¦ĆÓ”▓, Ó”åÓ”░ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ģÓ”ŁÓ”┐Ó”£Ó¦ŹÓ”×Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ćÓ”ć Ó””Ó¦ŹÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ¦ĆÓ¦¤ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ŚÓ¦ć Ó”ĪÓ”© Ó”ĢÓ¦üÓ”ćÓ”ĢÓ”£Ó¦ŗÓ”¤, Ó”¼Ó”ŠÓ”▓Ó”£Ó”ŠÓ”Ģ, Ó”ŚÓ¦ŗÓ”▓Ó”ÜÓ”ŠÓ”░Ó”Ł, Ó”½Ó¦ŹÓ”▓Ó”¼Ó¦ćÓ¦¤Ó”ŠÓ”░, Ó”ŚÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”¤Ó¦ć, Ó”żÓ”▓Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ¦¤, Ó””Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ¦¤Ó¦ćÓ”ŁÓ¦ŹÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”ĖÓ”éÓ”»Ó¦üÓ”ż Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż
Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü-Ó”ÅÓ”░ Ó”ÅÓ”ć Ó”ÜÓ¦ćÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”Š Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ćÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ćÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ć Ó”¬Ó”źÓ”┐Ó”ĢÓ¦āÓ”żÓ¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£Óźż Ó”ÅÓ”ć Ó”¼Ó”ćÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ¦¤ Ó”¬Ó”©Ó¦ćÓ”░-Ó”¼Ó”┐Ó”Č Ó”¼Ó”øÓ”░ Ó”¬Ó”░ Ó”«Ó”┐Ó”¢Ó”ŠÓ”ćÓ”▓ Ó”¼Ó”ŠÓ”¢Ó”żÓ”┐Ó”© Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¦Ó”ŠÓ”©Ó”ż Ó””Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ¦¤Ó¦ćÓ”ŁÓ¦ŹÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ”┐ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó””Ó”ŠÓ¦¤Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”ĢÓ¦ć Ó”«Ó”┐Ó”©Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”«Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”© Ó”¤Ó¦ŹÓ”░Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”£Ó¦ćÓ”ĪÓ”┐Ó”░ Ó”«Ó”ż Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ĆÓ”© Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”»Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ż Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”»Ó””Ó”┐Ó”ō Ó”¼Ó”ŠÓ”¢Ó”żÓ”┐Ó”©-Ó”ÅÓ”░ Ó”ĖÓ¦ć-Ó”ĖÓ”¼ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”¬Ó¦üÓ”©Ó”░Ó¦üÓ””Ó¦ŹÓ”¦Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”ż Ó”åÓ”░Ó¦ŗ Ó”¼Ó”øÓ”░ Ó”żÓ”┐Ó”░Ó”┐Ó”Č Ó”ĢÓ¦ćÓ”¤Ó¦ć Ó”ŚÓ”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Óźż
Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”ÅÓ”ć Ó”ĢÓ”ŠÓ”£Ó¦ćÓ”░ Ó”»Ó¦ć-Ó”¼Ó¦łÓ”ČÓ”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó¦ŹÓ”» Ó¦¬Ó¦©-Ó”¼Ó”øÓ”░ Ó”¬Ó”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”éÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ”░Ó”ŻÓ¦ć Ó”ēÓ”▓Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ćÓ”¢ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©, Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”Ģ Ó”¼Ó”┐Ó”¬Ó¦ŹÓ”▓Ó”¼Ó”«Ó¦üÓ”¢Ó¦Ć Ó”¼Ó”ŠÓ”«Ó”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”źÓ¦Ć Ó”©Ó¦ĆÓ”żÓ”┐ Ó”ō Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ÉÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó¦ŹÓ”»Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”«Ó”ż Ó”ō Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ÜÓ”▓Ó”┐Ó”ż Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ¦ŹÓ”»-Ó”ÅÓ”░ Ó”ŁÓ”┐Ó”żÓ”░ Ó”ĖÓ”éÓ”»Ó¦ŗÓ”Ś Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”åÓ”░ Ó”¼Ó”ŠÓ”¢Ó”żÓ”┐Ó”© Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ””Ó”░Ó¦ŹÓ”ČÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦Ć Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó¦łÓ”░Ó”ŠÓ”ÜÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”¼Ó”┐Ó”¬Ó”░Ó¦ĆÓ”ż Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ¦ŹÓ”» Ó”»Ó¦ć-Ó”¢Ó¦üÓ”üÓ”£Ó”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”© Ó”░ŌĆīÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¼Ó”▓Ó¦ć Ó”ō Ó””Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ¦¤Ó¦ćÓ”ŁÓ¦ŹÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ”┐Ó”░ Ó”░Ó”ÜÓ”©Ó”ŠÓ¦¤ŌĆö Ó”ÅÓ”ć Ó””Ó¦üÓ”ćÓ¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”ŁÓ”┐Ó”żÓ”░Ó”ō Ó”«Ó”┐Ó”▓ Ó”»Ó”źÓ¦ćÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Óźż Ó”«Ó”┐Ó”▓ Ó”╣Ó¦¤Ó”żÓ¦ŗ Ó”åÓ”░Ó¦ŗ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó¦ü Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ”┐Óźż Ó¦¦Ó¦»Ó¦©Ó¦®-ӔŠӔ▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü, Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ŗ-Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ŗ Ó”«Ó”żÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”ĖÓ”¼Ó”ÜÓ¦ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó¦£ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£, ŌĆśÓ”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó”░Ó”┐ Ó”ģÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”Ī Ó”ĢÓ¦ŹÓ”▓Ó”ŠÓ”ĖÓ”ĢÓ”©Ó”ĖÓ”ŠÓ”ĖÓ”©Ó¦ćÓ”ĖŌĆÖ Ó”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”¼Ó¦ćÓ”░Ó”¼Ó”ŠÓ”░ Ó”¬Ó”░Ó”¬Ó”░Ó”ć Ó”ÅÓ”▓ Ó”░Ó¦üÓ””Ó”ŠÓ”Ė, Ó”ō Ó”Å. Ó”ĪÓ¦ćÓ”░Ó¦ŗÓ”░Ó”┐Ó”© Ó”¼Ó”ćÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”«Ó”ŠÓ”░Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”Ģ Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”▓Ó¦ŗÓ”ÜÓ”©Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”▓Ó¦ćÓ”©Ó”┐Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó¦āÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦üÓ”░ Ó”¬Ó”░ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”© Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░ Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”ĖÓ”░Ó¦ŹÓ”¼Ó”«Ó¦¤ Ó”ĢÓ”░Ó¦ŹÓ”żÓ¦āÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”Š Ó”ĢÓ”░Ó”øÓ¦ćÓ”© Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”żÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”åÓ”¦Ó”┐Ó”¬Ó”żÓ¦ŹÓ”» Ó”ĖÓ”░Ó¦ŹÓ”¼Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ĆÓ”ĢÓ¦āÓ”ż Ó”╣Ó¦¤ Ó”©Ó”┐Óźż Ó¦¦Ó¦»Ó¦©Ó¦½-Ó¦©Ó¦¼ Ó”©Ó”ŠÓ”ŚÓ”ŠÓ”” Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü Ó”É Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”©Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”▓Ó¦ŗÓ”ÜÓ”©Ó”ŠÓ”░ Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¼Ó”©Ó¦ŹÓ”¦ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”ĖÓ¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¼Ó”©Ó¦ŹÓ”¦ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”źÓ”ŠÓ”ō Ó”øÓ”ŠÓ”¬Ó”Š Ó”╣Ó¦¤ Ó”©Ó”Š Ó”ō Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”ģÓ”ĖÓ”éÓ”¢Ó¦ŹÓ”» Ó”«Ó¦üÓ”¢Ó¦ŗÓ”«Ó¦üÓ”¢Ó”┐ Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓ”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ¦¤ Ó”ĢÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”£Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ō Ó”ÅÓ”ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”ēÓ”▓Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ćÓ”¢ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”© Ó”©Ó”┐Óźż Ó”¬Ó¦ćÓ”░Ó¦ćÓ”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó¦ŗÓ”ćÓ”ĢÓ”Š-Ó”░ Ó”¬Ó”░ Ó”ĖÓ¦ŗÓ”ŁÓ”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”ż Ó”ćÓ”ēÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”ŁÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ŚÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”©Ó”źÓ”┐Ó”¬Ó”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”ĖÓ”ŠÓ”░Ó”Š Ó””Ó¦üÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó”©Ó¦ć Ó”¢Ó¦üÓ”▓Ó¦ć Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š Ó”╣Ó”▓Ó¦ć Ó”ÅÓ”ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”¤Ó”┐ Ó”¬Ó”ŠÓ”ōÓ¦¤Ó”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤Óźż Ó¦©Ó¦”Ó¦”Ó¦© Ó”ĖÓ”ŠÓ”▓Ó¦ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”ćÓ”éÓ”░Ó¦ćÓ”£Ó”┐ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ”” ŌĆśÓ”ŁÓ¦ćÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖÓ¦ćÓ”ŠŌĆÖ Ó”ĢÓ”░Ó¦ŹÓ”żÓ¦āÓ”Ģ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”ŠÓ”ČÓ”┐Ó”ż Ó”╣Ó¦¤Óźż
Ó”«Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĖÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦Ć Ó”ÜÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ”Š, Ó”«Ó”©Ó”©Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó””Ó¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó¦ŹÓ”¼Ó”┐Ó”Ģ Ó”ĖÓ”éÓ”śÓ”ŠÓ”ż Ó”ō Ó”ĖÓ¦āÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”┐Ó”ČÓ¦ĆÓ”▓ Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”░Ó”ĢÓ”« Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¢Ó¦ŹÓ”»Ó”Š Ó”ÅÓ”ć Ó”ĖÓ”¼ Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦üÓ”ć Ó”»Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”ĖÓ¦éÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó¦ć Ó”ŚÓ¦ćÓ”üÓ”źÓ¦ć Ó”½Ó¦ćÓ”▓Ó”ŠÓ”░ Ó”ÜÓ¦ćÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”Š Ó”ÜÓ”▓Ó”øÓ”┐Ó”▓ Ó”¼Ó”┐Ó”Č Ó”ČÓ”żÓ”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”« Ó””Ó¦üÓ”ć Ó””Ó”ČÓ”ĢÓ¦ć Ó”ō Ó”ĖÓ¦ŗÓ”ŁÓ”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”ż Ó”ćÓ”ēÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó”© Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”ŠÓ”░ Ó”¬Ó”░Ó¦ćÓ”░ Ó””Ó”ČÓ”ĢÓ¦ćÓ”ō, Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”ō Ó”ÅÓ”ĢÓ”«Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”ēÓ””Ó¦ŹÓ””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ŹÓ”» Ó”øÓ”┐Ó”▓ Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó”żÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó¦ć Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░Ó”ŻÓ¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”¼Ó”¦Ó”ŠÓ”░Ó”┐Ó”ż Ó”¬Ó”ź Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ć Ó”©Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ¦¤Ó”żÓ”ŠÓ¦¤ Ó”¬Ó¦ćÓ¦ŚÓ”üÓ”øÓ¦üÓ”©Ó¦ŗÓźż
Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”ŻÓ¦ćÓ”ć Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü Ó”ō Ó”¼Ó”ŠÓ”¢Ó”żÓ”┐Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”ż Ó”«Ó”©Ó¦ĆÓ”ĘÓ¦ĆÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦¤Ó”ŠÓ”ĖŌĆö Ó”¬Ó¦āÓ”źÓ”┐Ó”¼Ó¦ĆÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ĆÓ”© Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”åÓ”¦Ó¦üÓ”©Ó”┐Ó”Ģ Ó”░Ó¦éÓ”¬Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”źÓ”┐Ó”ż Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”ŠÓźż Ó”åÓ”«Ó”░Ó”Š Ó”»Ó”¢Ó”© Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”ĖÓ”«Ó¦¤Ó”¤Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”«Ó”©Ó¦ć Ó”░Ó”ŠÓ”¢Ó”┐ŌĆö Ó”«Ó¦ŗÓ”¤Ó”ŠÓ”«Ó¦üÓ”¤Ó”┐ Ó”¼Ó”┐Ó”Č Ó”ČÓ”żÓ”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”« Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”¤Ó”┐ Ó””Ó”ČÓ”ĢŌĆö Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”żÓ¦ŗ Ó”¼Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”«Ó”┐Ó”ż Ó”©Ó”Š-Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”¬Ó”ź Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”©Ó”Š Ó”»Ó¦ć Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü Ó”ō Ó”¼Ó”ŠÓ”¢Ó”żÓ”┐Ó”©, Ó”żÓ”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”ż Ó”¬Ó”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ”┐Ó”ż┬ĀÓ”ĖÓ¦éÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”░Ó”Š Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ĆÓ”© Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”åÓ”¦Ó¦üÓ”©Ó”┐Ó”Ģ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¼Ó”©Ó¦ŹÓ”¦ Ó”¼Ó”┐Ó”ÜÓ”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”£Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ō Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ĆÓ”© Ó”ÅÓ”¬Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”¬Ó¦āÓ”źÓ”┐Ó”¼Ó¦ĆÓ”░ Ó”ĖÓ”¼Ó”ÜÓ¦ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”ĖÓ”«Ó¦āÓ””Ó¦ŹÓ”¦ Ó””Ó¦ćÓ”Č Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”żÓ¦ćÓ”░ Ó”░Ó”ŠÓ”«Ó”ŠÓ¦¤Ó”Ż-Ó”«Ó”╣Ó”ŠÓ”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”ż Ó”¬Ó¦üÓ”░Ó”ŠÓ”©Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»-Ó”£Ó”ŠÓ”żÓ”ĢÓ”ĢÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”©Ó¦ĆÓ”░ Ó”©Ó”ŠÓ”«Ó¦ŗÓ”▓Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ćÓ”¢ Ó”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”»Ó”©Ó¦ŹÓ”ż Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”© Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”¬Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó”« Ó”ÅÓ”ČÓ”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”« Ó”ģÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦üÓ”ĘÓ”┐Ó”ż Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó”┐ Ó”ō Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”ŚÓ”┐Ó”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó”┐ Ó”ÉÓ”╣Ó”┐Ó”Ģ Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»ŌĆö Ó”åÓ”░Ó”¼Ó¦ŹÓ”» Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė, Ó”ĖÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ””Ó”ŠÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”©Ó¦Ć Ó”ćÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ””Ó”┐ Ó””Ó¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”░Ó”Š Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ćÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”┐Ó”ż Ó”╣Ó”ōÓ¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó”¤Ó”┐Ó”ō Ó”żÓ¦ŗÓ”▓Ó¦ćÓ”© Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ō Ó”ÅÓ”ć Ó¦¦Ó¦»Ó¦©Ó¦” Ó”¼Ó”Š Ó¦¦Ó¦»Ó¦¬Ó¦” Ó”©Ó”ŠÓ”ŚÓ”ŠÓ”” Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”ż-Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ¦ć Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė-Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”»Ó¦ć Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”¼Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”«Ó¦¤Ó”ĢÓ”░ Ó”ģÓ”ŁÓ¦ŹÓ”»Ó¦üÓ””Ó¦¤ Ó”śÓ”¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć, Ó”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”¼-Ó”ĖÓ”éÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ¦āÓ”żÓ”┐Ó”░ Ó”ćÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó””Ó¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó¦ŹÓ”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”Ż Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”ēÓ””Ó”ŠÓ”╣Ó”░Ó”Ż Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ćÓ”ō Ó”¬Ó”ŠÓ”Ā Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”© Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ģÓ”źÓ”Ü Ó¦¦Ó¦»Ó¦©Ó¦”-Ó”©Ó”ŠÓ”ŚÓ”ŠÓ”” Ó”żÓ¦ŗ Ó”▓Ó¦ćÓ”©Ó”┐Ó”© Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ŹÓ”»Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”¦Ó¦ĆÓ”©Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”åÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó¦ŗÓ”▓Ó”©Ó”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”¼Ó”¼Ó”┐Ó”¬Ó¦ŹÓ”▓Ó”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”░Ó”ÖÓ¦ŹÓ”Ś Ó”ēÓ”¬Ó”ŠÓ””Ó”ŠÓ”© Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¬Ó”ĘÓ¦ŹÓ”¤ Ó”ÜÓ”┐Ó”╣Ó¦ŹÓ”©Ó”┐Ó”ż Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”åÓ”£ Ó”»Ó”¢Ó”© ŌĆśÓ”żÓ¦üÓ”▓Ó”©Ó”ŠÓ”«Ó¦éÓ”▓Ó”Ģ Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»ŌĆÖ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”¤ Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤ Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”░Ó”Š Ó”¬Ó¦āÓ”źÓ”┐Ó”¼Ó¦ĆÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó””Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ÜÓ”░Ó¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ”żÓ¦ćÓ”ć Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ĆÓ”ĢÓ¦āÓ”ż, Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”żÓ¦ŗ Ó”ÜÓ¦ŗÓ”¢Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó”©Ó¦ć Ó””Ó¦ćÓ”¢Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”ćŌĆö Ó¦¦Ó¦»Ó¦¦Ó¦” Ó”ĖÓ”ŠÓ”▓Ó¦ć Ó¦¦Ó¦»Ó¦¬Ó¦”-Ó”ÅÓ”░ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”żÓ¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ŁÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”© Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”ŠÓ¦¤, Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”øÓ¦ŗÓ”¤Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬ Ó”ō Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė, Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć Ó”»Ó¦ć-Ó”żÓ¦ÄÓ”ĢÓ”ŠÓ”▓Ó¦ĆÓ”© Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”»Ó¦ć-Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”żÓ¦üÓ”▓Ó”©Ó”ŠÓ¦¤ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”¼Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”éÓ”Č Ó”ō Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ-Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ŚÓ¦£Ó”© Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”ŠÓ”░ Ó”åÓ”ŚÓ¦ć Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”żÓ¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”ŠÓ¦¤, Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”ŠÓ¦¤, Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ēÓ”ĀÓ¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”øÓ¦ŗÓ”¤Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”░Ó¦üÓ”Č Ó”ō Ó”½Ó”░Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć-Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”ŠÓ”żÓ¦ćÓ”ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”« Ó”ĖÓ¦ŹÓ”źÓ”┐Ó”░Ó¦ĆÓ”ĢÓ¦āÓ”ż Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓ Ó”░Ó”¼Ó¦ĆÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó¦ŹÓ”░Ó”©Ó”ŠÓ”źÓ¦ćÓ”░ Ó”╣Ó”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”ēÓ”©Ó”┐Ó”Č Ó”ČÓ”żÓ”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó””Ó”ČÓ”ĢÓ¦ćÓźż
ŌĆśÓ”śÓ”░Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”░Ó¦ćŌĆÖÓ”░ Ó”░Ó”ÜÓ”©Ó”ŠÓ”ĢÓ”ŠÓ”▓Ó¦ć Ó”ŚÓ”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ĆÓ”£Ó”┐ Ó””Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”┐Ó”Ż Ó”åÓ”½Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”Š Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”½Ó”┐Ó”░Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĖÓ¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”¼Ó”¤Ó¦ć Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”░Ó”ŠÓ”£Ó”©Ó¦ĆÓ”żÓ”┐Ó”żÓ¦ć Ó”żÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ Ó”ŚÓ”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ĆÓ”»Ó¦üÓ”Ś Ó”ČÓ¦üÓ”░Ó¦ü Ó”╣Ó¦¤Ó”©Ó”┐Óźż Ó”ŚÓ”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ĆÓ”£Ó”┐ Ó”øÓ¦ŗÓ”¤Ó”¢Ó”ŠÓ”¤Ó¦ŗ Ó””Ó¦ü-Ó”ÜÓ”ŠÓ”░Ó”¤Ó¦ć Ó”åÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó¦ŗÓ”▓Ó”©Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”åÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó¦ŗÓ”▓Ó”© Ó”ō Ó”ĖÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”╣ Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”¬Ó”░Ó¦ĆÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”Š-Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ĆÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”Š Ó”ĢÓ”░Ó”øÓ¦ćÓ”© Ó”¼Ó”¤Ó¦ć Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”░Ó”ŠÓ”£Ó”©Ó¦łÓ”żÓ”┐Ó”Ģ Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”ō Ó”åÓ””Ó”░Ó¦ŹÓ”Č Ó”żÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”┐Ó”ż Ó”╣Ó¦¤Ó”©Ó”┐Óźż ŌĆśÓ”śÓ”░Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”░Ó¦ćŌĆÖ-Ó”żÓ¦ć Ó”»Ó¦ć Ó”¼Ó”┐Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦Ć Ó””Ó¦ŹÓ”░Ó”¼Ó¦ŹÓ”» Ó”¼Ó¦¤Ó”ĢÓ”¤Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”¼Ó”▓Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”ĖÓ¦ćÓ”¤Ó”Š Ó¦¦Ó¦»Ó¦”Ó¦½ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó¦¦Ó¦»Ó¦”Ó¦«-Ó”ÅÓ”░ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦Ć Ó”»Ó¦üÓ”ŚÓ¦ćÓ”░ Ó”śÓ”¤Ó”©Ó”ŠÓźż
Ó”ÅÓ”ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¬Ó¦ćÓ”ČÓ¦ć Ó”¼Ó”┐Ó”ÜÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”ēÓ””Ó”ŠÓ”╣Ó”░Ó”Ż Ó””Ó”┐Ó”▓Ó¦ć Ó”╣Ó¦¤Ó”żÓ¦ŗ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¬Ó”ĘÓ¦ŹÓ”¤ Ó”╣Ó”¼Ó¦ć, Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦Ź Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓ”¤Ó”ŠÓ”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░ Ó”£Ó¦ŗÓ”░ Ó””Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”ÜÓ”ŠÓ”ćÓźż
Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü Ó”░Ó”¼Ó¦ĆÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó¦ŹÓ”░Ó”©Ó”ŠÓ”źÓ¦ćÓ”░ ŌĆśÓ”śÓ”░Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”░Ó¦ćŌĆÖ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”¢Ó¦üÓ”¼ Ó”øÓ¦ŗÓ”¤, Ó”¢Ó¦üÓ”¼Ó”ć Ó”øÓ¦ŗÓ”¤, Ó”åÓ”▓Ó¦ŗÓ”ÜÓ”©Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©, Ó”ÅÓ”¤Ó”Š Ó”░Ó”¼Ó¦ĆÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó¦ŹÓ”░Ó”©Ó”ŠÓ”źÓ¦ćÓ”░ ŌĆśÓ”Å Ó”ŚÓ”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”¦Ó¦Ć Ó”©Ó”ŁÓ¦ćÓ”▓ÓźżŌĆÖ Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”¤Ó”┐Ó”ō Ó”¼Ó¦üÓ”ØÓ”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”© Ó”©Ó”┐, Ó”ÅÓ”ĢÓ”£Ó”© Ó”ĖÓ”ŠÓ”¦Ó”ŠÓ”░Ó”Ż Ó”¬Ó”ŠÓ”ĀÓ”ĢÓ”ō Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó¦ćÓ”░ Ó”śÓ”¤Ó”©Ó”Š Ó”»Ó¦ćÓ”«Ó”© Ó”¬Ó”░Ó”¬Ó”░ Ó”¬Ó¦£Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”©, Ó”żÓ¦ćÓ”«Ó”© Ó”ōÓ”¬Ó”░-Ó”ōÓ”¬Ó”░Ó”ō Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”¤Ó”┐ Ó”¬Ó¦£Ó¦ćÓ”© Ó”©Ó”┐ Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐Óźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”¤Ó”Š Ó”¦Ó”░Ó”Š Ó”¬Ó¦£Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ¦¤ Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”¤Ó”┐Ó”░ Ó”¤Ó¦üÓ”ĢÓ”░Ó¦ŗ Ó”¤Ó¦üÓ”ĢÓ”░Ó¦ŗ Ó”»Ó¦ć-Ó”¼Ó”┐Ó”¼Ó”░Ó”Ż Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”żÓ”Š Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ćÓźż
ŌĆśÓ”śÓ”░Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”░Ó¦ćŌĆÖ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”« Ó”«Ó”╣Ó”ŠÓ”»Ó¦üÓ””Ó¦ŹÓ”¦Ó”░ Ó”¼Ó”øÓ”░Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”żÓ¦ćŌĆö Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”«Ó¦ć Ó”ĢÓ”ŠÓ”ŚÓ”£Ó¦ć Ó”¦Ó”ŠÓ”░Ó”ŠÓ”¼Ó”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”Ģ Ó”¼Ó¦ćÓ”░Ó¦¤, Ó”¬Ó”░Ó¦ć Ó”¼Ó”ć Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć (Ó¦¦Ó¦»Ó¦¦Ó¦¼)Óźż Ó¦¦Ó¦»Ó¦¦Ó¦» Ó”©Ó”ŠÓ”ŚÓ”ŠÓ””Ó”ć Ó”ÅÓ”░ Ó”ćÓ”éÓ”░Ó¦ćÓ”£Ó”┐ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ”” Home and Abroad Ó”¼Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ¦¤Óźż
ŌĆśÓ”śÓ”░Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”░Ó¦ćŌĆÖÓ”░ Ó”░Ó”ÜÓ”©Ó”ŠÓ”ĢÓ”ŠÓ”▓Ó¦ć Ó”ŚÓ”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ĆÓ”£Ó”┐ Ó””Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”┐Ó”Ż Ó”åÓ”½Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”Š Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”½Ó”┐Ó”░Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĖÓ¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”¼Ó”¤Ó¦ć Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”░Ó”ŠÓ”£Ó”©Ó¦ĆÓ”żÓ”┐Ó”żÓ¦ć Ó”żÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ Ó”ŚÓ”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ĆÓ”»Ó¦üÓ”Ś Ó”ČÓ¦üÓ”░Ó¦ü Ó”╣Ó¦¤Ó”©Ó”┐Óźż Ó”ŚÓ”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ĆÓ”£Ó”┐ Ó”øÓ¦ŗÓ”¤Ó”¢Ó”ŠÓ”¤Ó¦ŗ Ó””Ó¦ü-Ó”ÜÓ”ŠÓ”░Ó”¤Ó¦ć Ó”åÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó¦ŗÓ”▓Ó”©Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”åÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó¦ŗÓ”▓Ó”© Ó”ō Ó”ĖÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”╣ Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”¬Ó”░Ó¦ĆÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”Š-Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ĆÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”Š Ó”ĢÓ”░Ó”øÓ¦ćÓ”© Ó”¼Ó”¤Ó¦ć Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”░Ó”ŠÓ”£Ó”©Ó¦łÓ”żÓ”┐Ó”Ģ Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”ō Ó”åÓ””Ó”░Ó¦ŹÓ”Č Ó”żÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”┐Ó”ż Ó”╣Ó¦¤Ó”©Ó”┐Óźż ŌĆśÓ”śÓ”░Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”░Ó¦ćŌĆÖ-Ó”żÓ¦ć Ó”»Ó¦ć Ó”¼Ó”┐Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦Ć Ó””Ó¦ŹÓ”░Ó”¼Ó¦ŹÓ”» Ó”¼Ó¦¤Ó”ĢÓ”¤Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”¼Ó”▓Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”ĖÓ¦ćÓ”¤Ó”Š Ó¦¦Ó¦»Ó¦”Ó¦½ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó¦¦Ó¦»Ó¦”Ó¦«-Ó”ÅÓ”░ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦Ć Ó”»Ó¦üÓ”ŚÓ¦ćÓ”░ Ó”śÓ”¤Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ģÓ”źÓ”Ü Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü Ó”ÅÓ”¤Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”ŚÓ”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ĆÓ”£Ó”┐Ó”░ Ó”¼Ó”┐Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦Ć Ó”¬Ó”ŻÓ¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”░Ó¦ŹÓ”£Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”½Ó¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”©Óźż
Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”©Ó”Š-Ó”╣Ó¦¤ Ó”½Ó¦ćÓ”▓Ó”▓Ó¦ćÓ”© Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”ĖÓ¦ćÓ”¤Ó”ŠÓ”ć Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó””Ó”ŠÓ”üÓ¦£Ó”ŠÓ”▓ Ó”¼Ó”ćÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”«Ó¦éÓ”▓Ó¦ŹÓ”» Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ”¦Ó”ŠÓ”░Ó”ŻÓ¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¦Ó”ŠÓ”© Ó”©Ó”┐Ó”░Ó”┐Ó”¢Óźż Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü Ó”ÅÓ”żÓ””Ó¦éÓ”░ Ó”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”»Ó”©Ó¦ŹÓ”ż Ó”ŚÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”© Ó”»Ó¦ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”¤Ó”┐Ó”ČÓ”¼Ó”┐Ó”░Ó¦ŗÓ”¦Ó¦Ć Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦Ć Ó”åÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó¦ŗÓ”▓Ó”©Ó¦ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”¤Ó”┐Ó”Č-Ó”¬Ó¦üÓ”▓Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”¼Ó”ĢÓ”żÓ”Š Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”░Ó”¼Ó¦ĆÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó¦ŹÓ”░Ó”©Ó”ŠÓ”ź Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓ”ō Ó”▓Ó”┐Ó”¢Ó”▓Ó¦ćÓ”©Óźż
Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”£Ó”ŠÓ”©Ó”┐ŌĆö┬ĀÓ”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ć Ó”åÓ”«Ó”░Ó”Š Ó”ÅÓ”żÓ”¤Ó”ŠÓ”ć Ó”ĖÓ”ČÓ¦ŹÓ”░Ó””Ó¦ŹÓ”¦ Ó”»Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ć Ó”ÅÓ”ć Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”ĀÓ”┐Ó”Ģ Ó”ĢÓ¦Ć Ó”©Ó”Š, Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ĖÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó¦ćÓ”╣ Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”ŻÓ¦ć, Ó”ÅÓ”ć Ó”©Ó”┐Ó”¼Ó”©Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”ÜÓ¦ćÓ”░ Ó”«Ó¦éÓ”▓ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”░ Ó”ćÓ”éÓ”░Ó¦ćÓ”£Ó”┐ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”¬Ó”┐Ó”¤Ó”┐ Ó”ĖÓ”éÓ”»Ó¦ŗÓ”£Ó”© Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”£Ó¦üÓ¦£Ó¦ć Ó””Ó”┐Ó”▓Ó”ŠÓ”«Óźż
Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ć Ó”½Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”źÓ”«Ó”┐Ó”Ģ Ó”ĖÓ¦éÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó”¬Ó”ŠÓ”ż Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ĖÓ¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”©Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”»Ó¦ć-Ó”ĖÓ”«Ó”ĖÓ¦ŹÓ”ż Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ć Ó”ŚÓ”ŻÓ”żÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”ō Ó”½Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”¼Ó”ŠÓ”” Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”åÓ”▓Ó¦ŗÓ”ÜÓ”©Ó”Š Ó”śÓ”¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć, Ó”▓Ó¦üÓ”ĢÓ”ŠÓ”Ü Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”┐Ó”ż Ó”░Ó”ÜÓ”©Ó”ŠÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”ēÓ”▓Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ćÓ”¢ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”ō Ó”ÅÓ”ć Ó”¼Ó”┐Ó”ÜÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”ć Ó”¤Ó”«Ó”ŠÓ”Ė Ó”«Ó”ŠÓ”©-Ó”ÅÓ”░ Ó”«Ó”ŠÓ”╣Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó¦ŹÓ”» Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”Š Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”©, Ó”ģÓ”źÓ”Ü ŌĆśÓ”śÓ”░Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”░Ó¦ćŌĆÖ Ó”£Ó¦üÓ¦£Ó¦ć Ó”£Ó”ŠÓ”żÓ¦ĆÓ¦¤ Ó”«Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó”Š Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”»Ó¦ć Ó”żÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”░Ó¦ŹÓ”Ģ, Ó”żÓ”Š Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”¬Ó¦£Ó”▓Ó¦ćÓ”©Ó”ć Ó”©Ó”ŠÓźż
Ó”¬Ó”ŠÓ”üÓ”Ü
Ó”É Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¼Ó”©Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ć Ó”ģÓ”¬Ó”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”¬Ó”ŠÓ””Ó¦ŹÓ”» Ó”øÓ”┐Ó”▓ŌĆö┬ĀÓ”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”ĢÓ”░Ó¦ŹÓ”« Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░, Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ćÓ”░, Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”┐Ó”Ģ Ó”ÜÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ”Š Ó”ģÓ”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”Ż Ó”ō Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦āÓ”źÓ”┐Ó”¼Ó¦ĆÓ”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¬Ó¦Ć Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”ČÓ¦ĆÓ”▓Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”»Ó”źÓ”ŠÓ”»Ó¦ŗÓ”ŚÓ¦ŹÓ”» Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”©Ó¦¤Óźż Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”ÅÓ”ō Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ”┐ŌĆö Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó¦üÓ”░Ó¦ŹÓ”£Ó¦ćÓ”ŠÓ¦¤Ó”ŠÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”Š Ó”¦Ó”©Ó”żÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”Ģ Ó”»Ó¦üÓ”ŚÓ¦ćÓ”░ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦éÓ”¬ Ó”¼Ó”▓Ó¦ć Ó”¼Ó”░Ó¦ŹÓ”ŻÓ”©Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó”ŠÓ”ō Ó”ģÓ”©Ó¦łÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”ĢÓźż Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”»Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”¼Ó”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ć Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓ”░Ó”ō Ó”åÓ”ŁÓ”ŠÓ”Ė Ó”åÓ”øÓ¦ć Ó”»Ó¦ć, Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”Š Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”éÓ”ĢÓ”¤Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”©Ó¦Ć Ó”©Ó¦¤, Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”Ģ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤Ó”ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó”┐Ó”Ģ Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”Č Ó”ō Ó”ĖÓ”éÓ”ĢÓ”¤Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”©Ó¦Ć, Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”Ģ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤Ó”ć Ó”ĖÓ”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó¦ćÓ”«Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”éÓ”ĢÓ”¤Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓźż
Ó”ÅÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”ĖÓ”¼Ó”ć Ó”ÅÓ”żÓ”ĢÓ”ŠÓ”▓ Ó”¦Ó”░Ó¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”┐Ó”ż Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”┐Ó”ż Ó”¦Ó”ŠÓ”░Ó”ŻÓ”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”¬Ó”░Ó¦ĆÓ”ż Ó”©Ó¦ćÓ”żÓ”┐Ó”¼Ó”ŠÓ”ÜÓ”Ģ Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓźż Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”éÓ”£Ó¦ŹÓ”×Ó”Š Ó”ō Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼ Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ć Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”¦Ó”ŠÓ”░Ó”ŻÓ”Š Ó”ĢÓ¦Ć, Ó”ÅÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”«Ó”ŠÓ”Ż Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó””Ó”ŠÓ¦¤-Ó””Ó”ŠÓ¦¤Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”»Ó””Ó”┐Ó”ō Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░ Ó”¼Ó”░Ó¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ¦¤ Ó”©Ó”Š, Ó”żÓ”¼Ó¦ü Ó”ĖÓ¦ć Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó¦ć Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”«Ó”ŠÓ”© Ó”©Ó”Š Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ”▓Ó¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”ģÓ”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ĆÓ”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”«Ó”ŠÓ”źÓ”ŠÓ¦¤ Ó”åÓ”ĖÓ”ż Ó”©Ó”ŠÓźż
Ó”ÅÓ”ć Ó”ĖÓ”┐Ó””Ó¦ŹÓ”¦Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”¬Ó¦ćÓ¦ŚÓ”üÓ”øÓ¦ćÓ”øÓ”┐ Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”» Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ō Ó”ĢÓ”ŠÓ”£Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŚÓ”żÓ”┐Ó”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦¤Ó¦ŗÓ”£Ó”©Ó¦ćÓźż Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ¦¤ Ó”ĘÓ”ŠÓ”¤ Ó”¼Ó”øÓ”░ Ó”¦Ó”░Ó¦ć Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬-Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”▓Ó”┐Ó”¢Ó”øÓ”┐Óźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ģÓ”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”╣Ó”ż Ó”ÜÓ”░Ó¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ”░ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”ŁÓ”¼Ó¦ć Ó”¬Ó¦ćÓ¦ŚÓ”üÓ”øÓ¦ćÓ”øÓ”┐ Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó”¼Ó”ŠÓ”░ Ó”»Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”Š Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ¦āÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”┐ Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”Š Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó”©Ó”┐Ó”£Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼ Ó”żÓ”ŠÓ¦£Ó”©Ó”ŠÓ¦¤, Ó”ō Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬-Ó”åÓ”ĢÓ”ŠÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”ŠÓ¦¤Óźż Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”«Ó¦ćÓ”ć Ó”ćÓ”éÓ”░Ó¦ćÓ”£Ó”┐ Ó”¼Ó”Š Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”» Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”ŠÓ¦¤ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”ĢÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”©Ó¦ĆÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”ĢÓ”░Ó”Ż Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”©Ó¦¤Óźż
Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ĢÓ”┐ Ó”ĢÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ-Ó”ĢÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”öÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”Ģ Ó”¼Ó”Š Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”»Ó””Ó”┐ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”Š Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ĢÓ”ĢÓ¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”┐Ó”ż Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”ō Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”żÓ”¼Ó¦ć Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”░Ó”ÜÓ”©Ó”ŠÓ”░ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”ć Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”©Ó”┐Ó”£Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”«Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ż Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”¦Ó¦ĆÓ”© Ó”ō Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó¦¤Ó”«Ó¦ŹÓ”ŁÓ”░ Ó”ĖÓ¦āÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”┐Ó”ČÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐ Ó”ō Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”Š Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ”╣Ó”┐Ó”ż Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¼Ó”▓ Ó”ŚÓ”żÓ”┐Ó”«Ó¦¤Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”£Ó¦ŗÓ”░Ó¦ćÓźż Ó¦¦Ó¦«Ó¦½Ó¦« Ó”ō Ó¦¦Ó¦«Ó¦¼Ó¦¦-Ó¦¦Ó¦«Ó¦¼Ó¦©-Ó”żÓ¦ć Ó”»Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”«Ó¦ć ŌĆśÓ”åÓ”▓Ó”ŠÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”śÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó””Ó¦üÓ”▓Ó”ŠÓ”▓ŌĆÖ Ó”ō ŌĆśÓ”╣Ó¦üÓ”żÓ¦ŗÓ”« Ó”¬Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”üÓ”ÜÓ”ŠÓ”░ Ó”©Ó”ĢÓ”ČÓ”ŠŌĆÖ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ÅÓ”ć Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”¢Ó”©Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤ Ó”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”»Ó”©Ó¦ŹÓ”ż Ó”ĢÓ”┐Ó”×Ó¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó””Ó”¦Ó”┐Ó”Ģ Ó””Ó¦ćÓ¦£Ó”Č Ó”¼Ó”øÓ”░ Ó”¦Ó”░Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”Š Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”åÓ”ĖÓ”øÓ¦ć Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”¦Ó¦ĆÓ”© Ó”ō Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó¦¤Ó”éÓ”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”Ż Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”» Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ćÓźż Ó”ĢÓ¦Ć Ó”ĖÓ¦éÓ”ÜÓ”©Ó”ŠÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”¼Ó¦ć, Ó”ĢÓ¦Ć Ó”åÓ”¦Ó¦üÓ”©Ó”┐Ó”ĢÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”¼Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”Š Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”©Ó”┐Ó”£Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ćÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”Ė Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”żÓ¦üÓ”▓Ó¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”»Ó”Š Ó”¬Ó¦āÓ”źÓ”┐Ó”¼Ó¦ĆÓ”░ Ó”»Ó¦ć-Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ćÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”ĢÓ¦ĆÓ”░Ó¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”░ Ó”ĖÓ”«Ó”żÓ¦üÓ”▓Ó¦ŹÓ”»Óźż Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”ÅÓ”¢Ó”©, Ó”»Ó”¢Ó”© Ó”ÅÓ”ć Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”øÓ”┐, Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”ŚÓ”ż Ó”żÓ”┐Ó”░Ó”┐Ó”Č-Ó”¬Ó”üÓ¦¤Ó”żÓ”┐Ó”░Ó”┐Ó”Č Ó”¼Ó”øÓ”░Ó¦ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ć-Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”Š Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ĢÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”ŁÓ¦ĆÓ”¬Ó¦ŹÓ”ĖÓ”Š Ó”ō Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó”░Ó¦ŹÓ”źÓ¦ŹÓ”»Ó”░Ó¦ć Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”«Ó”ŠÓ”Ż Ó”åÓ”«Ó”░Ó”Š Ó”¬Ó¦ćÓ¦¤Ó¦ćÓ”øÓ”┐, Ó”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”Å-Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó””Ó”ŠÓ¦¤Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”ŠÓ”ō Ó”»Ó”ŠÓ¦¤, Ó”¼Ó”▓Ó”ŠÓ”ō Ó”»Ó”ŠÓ¦¤, Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”Š Ó”ēÓ”ÜÓ”┐Ó”ż Ó”ō Ó”¼Ó”▓Ó”Š Ó”ēÓ”ÜÓ”┐Ó”ż Ó”»Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ĢÓ”░Ó”ŠÓ”ć Ó”ÅÓ”¢Ó”© Ó””Ó¦üÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ¦ćÓ”░Ó”Š Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”▓Ó”┐Ó”¢Ó”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”Å-Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”»Ó”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”ĖÓ”¼Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ”┐Óźż Ó”ÅÓ”¢Ó”ŠÓ”©Ó¦ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Ģ Ó”¦Ó”░Ó¦ć-Ó”¦Ó”░Ó¦ć Ó”ō Ó”¼Ó”ć Ó”¦Ó”░Ó¦ć-Ó”¦Ó”░Ó¦ć Ó”ĖÓ¦ć-Ó”åÓ”▓Ó¦ŗÓ”ÜÓ”©Ó”ŠÓ¦¤ Ó”»Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ”┐ Ó”©Ó”ŠŌĆö Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¦Ó”ŠÓ”©Ó”ż Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”┐Ó”Ģ Ó”ÅÓ”ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¼Ó”©Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ćÓ”░ Ó”ŚÓ”żÓ”┐ Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”╣Ó”ż Ó”╣Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓźż Ó”żÓ”¼Ó¦ü Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¼Ó”©Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ćÓ”░ Ó”ČÓ¦üÓ”░Ó¦üÓ”żÓ¦ćÓ”ć Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”éÓ”£Ó¦ŹÓ”×Ó”Š Ó”ĢÓ”ż Ó”¼Ó”┐Ó”ÜÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”╣Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”»Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”▓Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó”┐ Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓, Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”Š Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ēÓ”▓Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ćÓ”¢ Ó”ģÓ”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”Ż Ó”øÓ”┐Ó”▓ Ó”©Ó”Š Ó”ō Ó”åÓ”░Ó¦ŗ Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”Ģ Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”Š Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”▓Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”┐Ó”ż Ó”øÓ”┐Ó”▓, Ó”¼Ó”▓Ó”ŠÓ”ć Ó”¼Ó”ŠÓ”╣Ó¦üÓ”▓Ó¦ŹÓ”»Óźż
Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”ŠÓ¦¤ Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”░Ó¦ć Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ć Ó”ÜÓ”░Ó¦ŹÓ”ÜÓ”Š Ó”¢Ó¦üÓ”¼ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”śÓ”¤Ó¦ć Ó”©Ó”┐, Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ĢÓ”┐ Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”żÓ¦ćÓ”ō Ó”©Ó¦¤Óźż Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗ-Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ć Ó”żÓ¦ŗ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ¦¤ Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦üÓ”ć Ó”śÓ”¤Ó¦ć Ó”©Ó”┐ Ó”¼Ó”▓Ó”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤Óźż Ó”½Ó”▓Ó¦ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”Ė Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó¦ü Ó”ĀÓ”ŠÓ”¤Ó¦ŹÓ”¤Ó”Š Ó”«Ó”┐Ó”ČÓ”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”¼Ó”▓Ó¦ć Ó”½Ó¦ćÓ”▓Ó”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤ Ó”»Ó¦ć Ó””Ó¦ŹÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ¦ĆÓ¦¤ Ó”«Ó”╣Ó”ŠÓ”»Ó¦üÓ””Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó”░ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬ Ó”ÅÓ”ĢÓ”£Ó”┐Ó”ĖÓ”¤Ó¦ćÓ”©Ó”ĖÓ”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”£Ó”«, Ó”ģÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¼Ó”ĖÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”Ī, Ó”ĪÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŗÓ”ĪÓ”┐Ó”½Ó”┐Ó”ĢÓ¦ćÓ”ČÓ”©, Ó”ĪÓ”┐Ó”ĢÓ”©Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”ĢÓ”ČÓ”©, Ó”¤Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĖÓ”ÜÓ¦üÓ¦¤Ó”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”¤Ó”┐, Ó”¬Ó¦ŗÓ”ĖÓ¦ŹÓ”¤-Ó”«Ó”ĪÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”©Ó”┐Ó”¤Ó”┐, Ó”ĪÓ¦ćÓ”ź Ó”ģÓ”¼ Ó””Ó”┐ Ó”ģÓ”źÓ”░, Ó”«Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”£Ó”┐Ó”Ģ Ó”░Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”▓Ó”ćÓ”£Ó”« Ó”ćÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ””Ó”┐ Ó”ćÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ””Ó”┐ Ó”©Ó”ŠÓ”©Ó”Š Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”åÓ”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ćŌĆö Ó”åÓ”░ Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó¦ŗÓ”ØÓ”ŠÓ”¼Ó¦üÓ”ØÓ”┐Ó”░ Ó”»Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó¦ü-Ó”åÓ”¦Ó”¤Ó¦ü Ó”ĖÓ¦üÓ”¼Ó”┐Ó”¦Ó¦ć Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć Ó”©Ó”Š Ó”żÓ”ŠÓ”ō Ó”©Ó¦¤, Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”żÓ¦ćÓ”ō Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó”øÓ¦ć Ó”©Ó”Š, Ó”▓Ó”┐Ó”¢Ó”żÓ¦ćÓ”ō Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó”øÓ¦ć Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¦Ó”ŠÓ”© Ó”ĢÓ”░Ó¦ŹÓ”«Ó”ČÓ”ŠÓ”▓Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”źÓ”ŠÓ”©Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”░ Ó”śÓ”¤Ó¦ć Ó”ŚÓ¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”▓Ó”ŠÓ”żÓ”┐Ó”© Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ-Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ć, Ó”¬Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó”« Ó”åÓ”½Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ¦¤, Ó”åÓ”░Ó”¼ Ó””Ó¦üÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”░, Ó”¬Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó”« Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”żÓ¦ĆÓ¦¤ Ó””Ó¦ŹÓ”¼Ó¦ĆÓ”¬Ó”¬Ó¦üÓ”×Ó¦ŹÓ”£Ó¦ć Ó”ō Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓźż
Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”» Ó”¼Ó”Š Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”» Ó”»Ó¦ć-Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”«Ó¦īÓ”▓Ó”┐Ó”Ģ Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”©Ó”Š Ó”øÓ”ŠÓ¦£Ó”Š Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”«Ó¦īÓ”▓Ó”┐Ó”Ģ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬ Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”╣Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”©Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ¦¤Ó”ć Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”┐Ó”ĢÓ””Ó¦ćÓ”░Ó”ć Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ¦ćÓ”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”©Ó¦¤Óźż Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó¦ĆÓ”ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”░Ó”ÜÓ”©Ó”ŠÓ”░ Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŁÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”żÓ”┐ Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ć Ó”©Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó”ż Ó”©Ó”Š-Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”ĖÓ¦āÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”© Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”╣Ó”żÓ¦ćÓ”ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”»Ó¦ć Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó¦Ć Ó”¼Ó”Š Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Ģ Ó”»Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”¬Ó””Ó¦ŹÓ”¦Ó”żÓ”┐ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”»Ó”ŠÓ¦¤Ó¦Ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”żÓ¦üÓ”▓Ó”żÓ¦ć Ó”ÜÓ”ŠÓ”© Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ÅÓ”«Ó”©Ó”ō Ó”╣Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”»Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”¼Ó”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”żÓ”┐Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ””Ó”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”żÓ”ŠÓ¦¤ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”Š Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ¦£ Ó”¼Ó”Š Ó”░Ó”╣Ó”ĖÓ¦ŹÓ”» Ó”ŁÓ¦ćÓ”ÖÓ¦ć Ó”ÅÓ¦£Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”© Ó”╣Ó¦¤Ó”żÓ¦ŗÓźż Ó”åÓ”¼Ó”ŠÓ”░, Ó”ÅÓ”ō Ó”żÓ¦ŗ Ó”ĖÓ”żÓ¦ŹÓ”» Ó”»Ó¦ć Ó”»Ó”ż Ó”¼Ó¦£ Ó””Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ČÓ”©Ó”┐Ó”Ģ Ó”ō Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”┐Ó”ĢÓ”ć Ó”╣Ó”©, Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”»Ó”¢Ó”© Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¢Ó¦ŹÓ”»Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”© Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”╣Ó”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”ĢÓ”żÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ””Ó”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”¤ Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬ŌĆö Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”¼Ó”Š Ó”øÓ”¼Ó”┐ Ó”¼Ó”Š Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ”░Ó¦ŹÓ”» Ó”¼Ó”Š Ó”ĖÓ”éÓ”ŚÓ¦ĆÓ”żŌĆö Ó”åÓ”░ Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”åÓ”ĖÓ¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó”¼Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”┐Ó”ż Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó¦ćÓ”░Ó”ć Ó”ĢÓ”ŠÓ”øÓ¦ćÓźż
Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”ŠÓ¦¤ Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”░Ó¦ć Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ć Ó”ÜÓ”░Ó¦ŹÓ”ÜÓ”Š Ó”¢Ó¦üÓ”¼ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”śÓ”¤Ó¦ć Ó”©Ó”┐, Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ĢÓ”┐ Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”żÓ¦ćÓ”ō Ó”©Ó¦¤Óźż Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗ-Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ć Ó”żÓ¦ŗ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ¦¤ Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦üÓ”ć Ó”śÓ”¤Ó¦ć Ó”©Ó”┐ Ó”¼Ó”▓Ó”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤Óźż Ó”½Ó”▓Ó¦ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”Ė Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó¦ü Ó”ĀÓ”ŠÓ”¤Ó¦ŹÓ”¤Ó”Š Ó”«Ó”┐Ó”ČÓ”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”¼Ó”▓Ó¦ć Ó”½Ó¦ćÓ”▓Ó”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤ Ó”»Ó¦ć Ó””Ó¦ŹÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ¦ĆÓ¦¤ Ó”«Ó”╣Ó”ŠÓ”»Ó¦üÓ””Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó”░ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬ Ó”ÅÓ”ĢÓ”£Ó”┐Ó”ĖÓ”¤Ó¦ćÓ”©Ó”ĖÓ”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”£Ó”«, Ó”ģÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¼Ó”ĖÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”Ī, Ó”ĪÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŗÓ”ĪÓ”┐Ó”½Ó”┐Ó”ĢÓ¦ćÓ”ČÓ”©, Ó”ĪÓ”┐Ó”ĢÓ”©Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”ĢÓ”ČÓ”©, Ó”¤Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĖÓ”ÜÓ¦üÓ¦¤Ó”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”¤Ó”┐, Ó”¬Ó¦ŗÓ”ĖÓ¦ŹÓ”¤-Ó”«Ó”ĪÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”©Ó”┐Ó”¤Ó”┐, Ó”ĪÓ¦ćÓ”ź Ó”ģÓ”¼ Ó””Ó”┐ Ó”ģÓ”źÓ”░, Ó”«Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”£Ó”┐Ó”Ģ Ó”░Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”▓Ó”ćÓ”£Ó”« Ó”ćÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ””Ó”┐ Ó”ćÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ””Ó”┐ Ó”©Ó”ŠÓ”©Ó”Š Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”åÓ”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ćŌĆö Ó”åÓ”░ Ó”żÓ”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó¦ŗÓ”ØÓ”ŠÓ”¼Ó¦üÓ”ØÓ”┐Ó”░ Ó”»Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó¦ü-Ó”åÓ”¦Ó”¤Ó¦ü Ó”ĖÓ¦üÓ”¼Ó”┐Ó”¦Ó¦ć Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć Ó”©Ó”Š Ó”żÓ”ŠÓ”ō Ó”©Ó¦¤, Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”żÓ¦ćÓ”ō Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó”øÓ¦ć Ó”©Ó”Š, Ó”▓Ó”┐Ó”¢Ó”żÓ¦ćÓ”ō Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó”øÓ¦ć Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¦Ó”ŠÓ”© Ó”ĢÓ”░Ó¦ŹÓ”«Ó”ČÓ”ŠÓ”▓Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”źÓ”ŠÓ”©Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”░ Ó”śÓ”¤Ó¦ć Ó”ŚÓ¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”▓Ó”ŠÓ”żÓ”┐Ó”© Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ-Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ć, Ó”¬Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó”« Ó”åÓ”½Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ¦¤, Ó”åÓ”░Ó”¼ Ó””Ó¦üÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”░, Ó”¬Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó”« Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”żÓ¦ĆÓ¦¤ Ó””Ó¦ŹÓ”¼Ó¦ĆÓ”¬Ó”¬Ó¦üÓ”×Ó¦ŹÓ”£Ó¦ć Ó”ō Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓźż
Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬ Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć, Ó”åÓ”«Ó”░Ó”Š Ó”▓Ó”┐Ó”¢Ó”┐ŌĆö Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”åÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”ĖÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦üÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”©Ó¦ćÓ”ČÓ”ŠÓ”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”ĖÓ¦ŹÓ”ż Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ”▓Ó¦ć Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░ Ó”ÅÓ”ć Ó”ĢÓ”░Ó¦ŹÓ”żÓ¦āÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”ÅÓ”ć Ó”ĖÓ”¼ Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”░Ó”ō Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ”¼Ó¦ć Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ÅÓ”¤Ó”ŠÓ”ć Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”░Ó¦ŹÓ”żÓ”«Ó”ŠÓ”© Ó”ĖÓ”éÓ”ĢÓ”¤Óźż
Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓ”¤Ó”Š Ó”ÅÓ”¢Ó”ŠÓ”©Ó¦ćÓ”ć Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š Ó”»Ó¦ćÓ”ż, Ó”»Ó¦ć-Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”åÓ”ŚÓ¦ć Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ŁÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”© Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”Č Ó”¼Ó”Š Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐ Ó”øÓ”┐Ó”▓, Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”£Ó”©Ó¦ŹÓ”» Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”░Ó”ÜÓ”©Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”╣Ó”¼Ó¦ćÓźż
Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”Š Ó”ō Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”żÓ¦ŗÓ”▓Ó”ŠÓ”ō Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”©Ó”┐Ó”░Ó”¼Ó”¦Ó”┐ Ó”▓Ó¦£Ó”ŠÓ”ćÓźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓ”¤Ó”ŠÓ¦¤ Ó”©Ó”Š-Ó”¬Ó¦ćÓ¦ŚÓ”üÓ”øÓ¦ć Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”ÅÓ”ć Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓ”¤Ó”Š Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤ Ó”©Ó”ŠÓźż
Ó¦¦Ó¦»Ó¦¼Ó¦¦ Ó”ĖÓ”ŠÓ”▓Ó¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”ŠÓ”ČÓ”┐Ó”ż Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ ŌĆśÓ””Ó”┐ Ó”░Ó¦ćÓ”ÜÓ¦ćÓ”Ī Ó”ģÓ”¼ Ó””Ó”┐ Ó”åÓ”░Ó¦ŹÓ”źŌĆÖ Ó”¼Ó”ćÓ”¤Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”½Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”©Ó”£ Ó”½Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó”© Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”« Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©ŌĆö Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”» Ó”«Ó”©Ó”©Ó”£Ó”ŠÓ”ż Ó”ō Ó”ĖÓ¦āÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”┐Ó”£Ó”ŠÓ”ż Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”” Ó”▓Ó¦üÓ”¤ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”░Ó”ŠÓ”£Ó”©Ó¦łÓ”żÓ”┐Ó”Ģ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”¦Ó¦ĆÓ”©Ó”żÓ”Š Ó”¬Ó¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”ō Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”▓Ó¦üÓ”¤Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”żÓ¦ŹÓ”żÓ”┐ Ó”¼Ó”╣Ó”ŠÓ”▓ Ó”åÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”½Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó”© Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©, Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó”»Ó¦üÓ”Ś Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ŚÓ¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”ō Ó”¬Ó”ŠÓ”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”» Ó”¼Ó”Š Ó”ćÓ¦¤Ó¦ŗÓ”░Ó¦ŗÓ”¬ Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”░ Ó”«Ó”©Ó”© Ó”ō Ó”ĖÓ¦āÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░ Ó””Ó”¢Ó”▓ Ó”óÓ”┐Ó”▓Ó¦ć Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”©Ó”┐Óźż Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”ÅÓ”ć Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”¼Ó”▓Ó”żÓ¦ć Ó”ŚÓ”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”½Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó”© ŌĆśÓ”ēÓ”¬Ó”©Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ¦ŗÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░ŌĆÖ Ó”¼Ó”Š Ó”¬Ó¦ŗÓ”ĖÓ¦ŹÓ”¤-Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓ Ó”¬Ó””Ó”¤Ó”┐ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”© Ó”©Ó”┐Óźż
Ó”ÅÓ”ĪÓ¦ŗÓ¦¤Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”Ī Ó”ĖÓ¦¤Ó”┐Ó””-Ó”ÅÓ”░ ŌĆśÓ”ģÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”©Ó¦ŹÓ”¤Ó”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤ŌĆÖ Ó”¼Ó”ćÓ”¤Ó”┐ Ó”¼Ó¦ćÓ”░Ó¦¤ Ó¦¦Ó¦»Ó¦ŁÓ¦«-Ó”ÅÓźż Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”¬Ó”░ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”»Ó¦ć-Ó”¤Ó¦üÓ”ĢÓ”░Ó¦ŗ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”▓Ó”┐Ó”¢Ó”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”© Ó”ō Ó”▓Ó”┐Ó”¢Ó”┐Ó”ż Ó”»Ó¦ć-Ó”¼Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ¦āÓ”żÓ”ŠÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”▓Ó”┐Ó”¢Ó”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”© Ó”ĖÓ¦ćÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”ĖÓ”éÓ”ĢÓ”▓Ó”© Ó”¼Ó¦ćÓ”░Ó¦¤ Ó¦¦Ó¦»Ó¦»Ó¦¼-Ó”ÅÓźż Ó”¼Ó”ćÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”©Ó”ŠÓ”« ŌĆśÓ”ĢÓ”ŠÓ”▓Ó”ÜÓ”ŠÓ”░ Ó”ģÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”Ī Ó”ćÓ”«Ó”¬Ó”┐Ó”░Ó”┐Ó¦¤Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓Ó”ćÓ”£Ó”«ÓźżŌĆÖ Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”▓Ó”ĢÓ¦ŹÓ”Ę Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ”┐ŌĆö Ó”ĖÓ¦¤Ó”┐Ó”” Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”ÅÓ”ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”ĢÓ¦ŗÓ”źÓ”ŠÓ”ō ŌĆśÓ”¬Ó¦ŗÓ”ĖÓ¦ŹÓ”¤-Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓ŌĆÖ Ó”ČÓ”¼Ó¦ŹÓ””Ó”¤Ó”┐ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”©Ó”©Ó”┐Óźż
Ó”ĢÓ”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó¦©Ó¦” Ó”¼Ó”øÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”¦Ó”ŠÓ”© Ó”ĖÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”ō Ó”½Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó”© Ó”ō Ó”ĖÓ¦¤Ó”┐Ó”” Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”ĘÓ¦ćÓ”░ Ó”¦Ó”© Ó”ō Ó”ĖÓ”éÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ¦āÓ”żÓ”┐ Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”ÜÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ”Š Ó”ēÓ”ĖÓ”ĢÓ¦ć Ó””Ó”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”ÅÓ”ć Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”ÜÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ”Š Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”ćÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”Ė Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”½Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŗ-Ó”░, Ó”¬Ó”ŠÓ”ĀÓ¦ŹÓ”» Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó””Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó””Ó”Š-Ó”░ Ó”ō Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó””Ó¦ćÓ”▓Ó¦ŹÓ”»Ó¦üÓ”£-Ó”ÅÓ”░ Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”ÜÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”░Ó”ŠÓ”▓ Ó”øÓ”┐Ó”▓Óźż
Ó”ŚÓ”ż Ó”ČÓ”żÓ”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó¦»Ó¦”-Ó”ÅÓ”░ Ó””Ó”ČÓ”ĢÓ¦ć Ó”ĢÓ¦¤Ó¦ćÓ”ĢÓ”£Ó”© Ó”¬Ó”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ”┐Ó”ż┬ĀÓ”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”ĘŌĆö Ó”ŚÓ”ŠÓ¦¤Ó”żÓ¦ŹÓ”░Ó¦Ć Ó”ÜÓ”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”¼Ó”░Ó¦ŹÓ”żÓ¦Ć Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¬Ó”┐Ó”ŁÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ģ, Ó”ģÓ”«Ó”┐Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”Š, Ó”£Ó¦ŹÓ”×Ó”ŠÓ”©Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”ŠÓ”Č Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”«Ó¦üÓ”¢ŌĆö Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐ Ó”¬Ó”░Ó¦ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó¦ćÓ”¼Ó””Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”ćÓ”¬Ó”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”¬Ó¦£Ó¦ć Ó”¼Ó”▓Ó”▓Ó¦ćÓ”© Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”£Ó¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”ć Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŁÓ¦ü Ó”ō Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”£Ó”Š Ó”ĢÓ”ŠÓ”ĀÓ”ŠÓ”«Ó¦ŗÓ”░ Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”░Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ¦¤ Ó”©Ó”ŠÓźż
Ó”ÅÓ”ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”«Ó”ŠÓ”ŻÓ¦ćÓ”░ Ó”¬Ó”░ Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó¦ćÓ”¼Ó””Ó¦ćÓ”░ Ó”╣Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ŹÓ”»Ó”ČÓ¦ŗÓ”ŁÓ”© Ó”«Ó”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”┐ Ó””Ó”ŠÓ”üÓ”ż Ó”¢Ó¦ćÓ”üÓ”ÜÓ”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ēÓ”ĀÓ”▓ Ó”ō Ó”ōÓ”üÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”¬Ó¦ŗÓ”ĖÓ¦ŹÓ”¤-Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”£Ó”«-Ó”ÅÓ”░ Ó”¦Ó”ŠÓ”░Ó”ŻÓ”Š Ó”åÓ”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”ż Ó”╣Ó”▓Óźż
Ó”»Ó”ŠÓ”üÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”©Ó”ŠÓ”« Ó”ēÓ”▓Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ćÓ”¢ Ó”ĢÓ”░Ó”▓Ó”ŠÓ”«, Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░Ó”Š Ó”ćÓ”éÓ”▓Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”Ī-Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”żÓ¦ćÓ”ć Ó”ĖÓ¦ŹÓ”źÓ”ŠÓ¦¤Ó¦ĆÓ”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó¦ć Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ćÓ”© Ó”ō Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó””Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ÜÓ”░Ó¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░Ó”Š Ó”»Ó”¢Ó”© Ó”¬Ó¦ŗÓ”ĖÓ¦ŹÓ”¤-Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓ Ó”¼Ó”Š Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░-Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”Č Ó”¦Ó”ŠÓ”░Ó”ŻÓ”ŠÓ”¤Ó”Š Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó”▓Ó¦ćÓ”© Ó”ō Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó”▓Ó¦ćÓ”© Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”¼Ó¦üÓ””Ó¦ŹÓ”¦Ó”┐Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó¦ĆÓ”░Ó”Š Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”«Ó”Ż Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”ÅÓ”«Ó”©Ó”ō Ó”¼Ó”▓Ó”▓Ó¦ćÓ”©ŌĆö Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░Ó”Š Ó”ÅÓ”ć Ó”ĖÓ”¼ Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”¼Ó”▓Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ÜÓ”ŠÓ”ĢÓ”░Ó”┐-Ó”¼Ó”ŠÓ”ĢÓ”░Ó”┐Ó”░ Ó”ĖÓ¦üÓ”¼Ó”┐Ó”¦Ó¦ć Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”ÜÓ”ŠÓ”ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż ŌĆśÓ”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”½Ó¦ćÓ”ČÓ”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓ Ó”ģÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ŗÓ”«Ó¦ŗÓ”ĪÓ¦ćÓ”ČÓ”©ŌĆÖ Ó”ČÓ”¼Ó¦ŹÓ””Ó”¤Ó”┐ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Óźż ŌĆśÓ”źÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”Ī Ó”ōÓ¦¤Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ŹÓ”Ī Ó”ĢÓ¦ŗÓ¦¤Ó”ŠÓ”¤Ó”ŠÓ”░Ó”▓Ó”┐ŌĆÖÓ”░ Ó¦¦Ó¦Ł Ó”¢Ó”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ¦ćÓ”░┬ĀÓ¦©Ó¦¤ Ó”ĖÓ”éÓ”¢Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ¦¤ Ó¦¦Ó¦»Ó¦»Ó¦¼-ӔŠӔ£Ó¦ćÓ”ĖÓ”¬Ó”ŠÓ”░ Ó”ŚÓ”Ė Ó”ĖÓ”¼Ó”ÜÓ¦ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”©Ó¦ŗÓ”éÓ”░Ó”Š Ó”åÓ”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”«Ó”Ż Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©Óźż Ó¦¦Ó¦»Ó¦»Ó¦¬-ӔŠӔČÓ¦ĆÓ”żÓ¦ćÓ”░ Ó¦©Ó¦”-Ó”żÓ”« Ó”ĖÓ”éÓ”¢Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”░ ŌĆśÓ”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”¤Ó”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓ Ó”ÅÓ”©Ó”ĢÓ¦ŗÓ¦¤Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”░Ó”┐ŌĆÖÓ”żÓ¦ć ŌĆśÓ”¬Ó¦ŗÓ”ĖÓ¦ŹÓ”¤-Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓ Ó”ģÓ”░Ó”ŠŌĆÖ Ó”ČÓ”┐Ó”░Ó¦ŗÓ”©Ó”ŠÓ”«Ó¦ć Ó”åÓ”░Ó”┐Ó”¢ Ó”ĪÓ”┐Ó”░Ó”▓Ó”┐Ó”Ģ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”»Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”░Ó¦ŹÓ”¬Ó¦éÓ”Ż Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¼Ó”©Ó¦ŹÓ”¦ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó¦ćÓ”©Óźż
Ó”ÅÓ”ć Ó”ĖÓ”¼ Ó”¼Ó”┐Ó”¬Ó”░Ó¦ĆÓ”ż Ó”åÓ”▓Ó¦ŗÓ”ÜÓ”©Ó”ŠÓ¦¤, Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ČÓ¦ŹÓ”©Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”ĢÓ¦Ć Ó”øÓ”┐Ó”▓?
Ó¦¦.┬ĀÓ”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”░Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”Č Ó”ĢÓ¦ŗÓ”© Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”£Ó¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”░Ó¦ŹÓ”śÓ”ŠÓ”ż Ó”śÓ”¤Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć?
Ó¦©. Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”¼ Ó”¬Ó”░Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”źÓ”┐Ó”żÓ”┐ Ó”ĢÓ”┐ Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ””Ó”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”¤ Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤ Ó”»Ó¦ćÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░-Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”▓Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”Ż Ó”¼Ó”▓Ó¦ć Ó”ÜÓ”┐Ó”©Ó¦ć Ó”©Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤?
Ó¦®.┬ĀÓ”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░-Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”Č Ó”¼Ó”▓Ó”żÓ¦ć Ó”ĢÓ”┐ Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ””Ó”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”¤ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”¬Ó”░Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”źÓ”┐Ó”żÓ”┐ Ó”¼Ó¦ŗÓ”ØÓ”ŠÓ¦¤ Ó”©Ó”Š Ó”ĢÓ¦Ć Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”Ż Ó”åÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó”Š Ó”ō Ó”¬Ó¦āÓ”źÓ”Ģ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ģÓ”¼Ó”ĖÓ¦ŹÓ”źÓ”Š Ó”¼Ó¦ŗÓ”ØÓ”ŠÓ¦¤?
Ó¦¬. Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░-Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”Č Ó”¼Ó”▓Ó”żÓ¦ć Ó”¼Ó¦ŗÓ”ØÓ”ŠÓ¦¤Ó”¤Ó”Š Ó”ĢÓ¦Ć? Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐ Ó”¬Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć? Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó”░ Ó”ŁÓ”┐Ó”żÓ”░Ó¦ć? Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”åÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó”Š?
Ó¦½.┬ĀÓ”¬Ó¦ŗÓ”ĖÓ¦ŹÓ”¤-Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓ Ó”¬Ó””Ó”¤Ó”┐Ó”░ Ó”£Ó¦ŗÓ”░Ó”¤Ó”Š Ó”ĢÓ¦ŗÓ”© Ó”ģÓ”éÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░ ŌĆśÓ”¬Ó¦ŗÓ”ĖÓ¦ŹÓ”¤ŌĆÖ-Ó”ÅÓ”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░ Ó”©Ó”Š ŌĆśÓ”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”£Ó”«ŌĆÖ-Ó”ÅÓ”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░?
Ó”ÅÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”▓Ó¦ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó¦ćÓ”¼! Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ćÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”Ė Ó”ĖÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ć ŌĆśÓ”źÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”Ī Ó”¬Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”£ŌĆÖ Ó”¬Ó¦£Ó”ŠÓ”©Ó¦ŗ Ó”╣Ó¦¤ Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”Ż, ŌĆśÓ”źÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”Ī Ó”¬Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”£ŌĆÖ-Ó”ÅÓ”░ Ó”ģÓ”░Ó¦ŹÓ”ź Ó”ĖÓ”«Ó¦üÓ””Ó¦ŹÓ”░Ó”¬Ó”źÓ¦ć Ó”¬Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó”« Ó”åÓ”½Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”Š Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”£Ó”ŠÓ”╣Ó”ŠÓ”£Ó¦ćÓ”░ Ó”¢Ó¦ŗÓ”▓ Ó”ŁÓ”░Ó¦ŹÓ”żÓ”┐ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó””Ó”ŠÓ”Ė Ó”åÓ”«Ó””Ó”ŠÓ”©Ó”┐Óźż Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”Š Ó”ÅÓ”¤Ó”Š Ó”ćÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”Ė Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”«Ó¦üÓ”øÓ¦ć Ó””Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”ÜÓ”ŠÓ¦¤Óźż
Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó¦ćÓ”¼Ó”░Ó”Š Ó”ÅÓ”¢Ó”© ŌĆśÓ”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐ŌĆÖÓ”░ Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦ć Ó”¼Ó¦ŗÓ”ØÓ¦ć Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ģÓ”źÓ”Ü Ó”¼Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”¤Ó”┐Ó”Č Ó”ĖÓ”░Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”▓Ó”©Ó¦ŹÓ”ĪÓ”©Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”«Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”ć Ó”øÓ”┐Ó”▓, Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”©Ó”ŠÓ”« Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓ Ó”ģÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”½Ó¦ćÓ¦¤Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖÓźż
Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐ Ó”¼Ó”▓Ó”żÓ¦ć Ó”¼Ó¦ŗÓ”ØÓ”ŠÓ¦¤ Ó”£Ó”«Ó”┐Óźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”£Ó”«Ó”┐ Ó”»Ó¦ć Ó””Ó”¢Ó”▓ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”ĖÓ¦ć Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”ŠÓ”ćÓ”£Ó”ŠÓ”░Óźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”£Ó”«Ó”┐Ó”░ Ó”żÓ¦ŗ Ó”ģÓ”¦Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦Ć Ó”åÓ”øÓ¦ć, Ó”«Ó”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”Ģ Ó”åÓ”øÓ¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”ĖÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░-Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”Č Ó”¼Ó”▓Ó”żÓ¦ć Ó”¼Ó¦ŗÓ”ØÓ”ŠÓ¦¤ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”«Ó¦üÓ”╣Ó¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”ż Ó”»Ó”¢Ó”© Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”«Ó”ŠÓ”¤Ó”┐-Ó”£Ó”«Ó”┐Ó”░ Ó”«Ó”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”Ģ Ó”»Ó¦ć Ó”øÓ”┐Ó”▓ Ó”ĖÓ¦ć Ó”£Ó”ŠÓ”©Ó¦ć Ó”ĖÓ¦ć Ó”¼Ó”ĖÓ”¼Ó”ŠÓ”Ė Ó”ĢÓ”░Ó”▓Ó¦ćÓ”ō Ó”ĖÓ¦ć Ó”É Ó”£Ó”«Ó”┐Ó”░ Ó”«Ó”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”Ģ Ó”©Ó¦¤Óźż Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ÅÓ”¤Ó”Š Ó”ŁÓ¦īÓ”żÓ”┐Ó”Ģ Ó”¬Ó”░Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”© Ó”ČÓ¦üÓ”░Ó¦ü Ó”╣Ó¦¤ŌĆö Ó”«Ó”ŠÓ”░Ó”Š Ó”©Ó”Š Ó”ŚÓ”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”ō Ó”¬Ó”░Ó”▓Ó¦ŗÓ”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Óźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó”»Ó”ŠÓ”¬Ó”©Ó”ć Ó”ēÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ”░-Ó”öÓ”¬Ó”©Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ”┐Ó”Ģ Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Óźż Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”ŠÓ”░ Ó”¬Ó”░Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó¦üÓ”╣Ó¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”ż Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ÅÓ”ć Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Óźż Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐ Ó”«Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ż Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”¼Ó”ŠÓ”░ Ó”¬Ó”░Ó¦ćÓ”░ Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”© Ó”©Ó¦¤Óźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”ć Ó”▓Ó”┐Ó”¢Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©ŌĆö Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó”░ Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”öÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”ĢÓ”░Ó”ŠÓźż Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Ģ Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ”żÓ¦ćÓ”ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”© Ó”©Ó”Š Ó”»Ó”┐Ó”©Ó”┐ Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó”░ Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”©Ó¦Ć Ó”øÓ”ŠÓ¦£Ó”Š Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”» Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ĢÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”©Ó¦Ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ĢÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”©Ó¦ĆÓ”ć Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ŁÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó¦üÓ”©Ó”░Ó¦üÓ””Ó¦ŹÓ”¦Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬-Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ĢÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£Óźż Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬-Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”¼Ó”┐Ó”«Ó¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”ż Ó”ČÓ”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¬ Ó”©Ó¦¤Óźż Ó”»Ó¦ćÓ”«Ó”© Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”© Ó”ÅÓ”ĪÓ¦ŗÓ¦¤Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”Ī Ó”ĖÓ¦¤Ó”┐Ó””, Narrative is crucial to my argument here, my basic point being that stories are at the heart of what explores and novelists say about strange regions of the world, they also become the method colonized people use to assert their own identity and existence of their own history.
Ó”ÅÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”»Ó¦ŗÓ”Ś Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”ÜÓ”ŠÓ”ćŌĆö Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó¦ćÓ”░ Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”ēÓ””Ó¦ŹÓ”śÓ”ŠÓ”¤Ó”© Ó”ĢÓ”░Ó”ŠÓ”░ Ó””Ó”ŠÓ¦¤ Ó”ÅÓ”ć Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”© Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ¦ćÓ”░ Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”ĢÓ”ŠÓ”░-Ó”öÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”ĢÓ””Ó¦ćÓ”░Óźż Ó”ĖÓ¦ć-Ó””Ó”ŠÓ¦¤Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ÉÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”Ģ Ó”¼Ó”Š Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”£Ó”¼Ó”┐Ó”£Ó¦ŹÓ”×Ó”ŠÓ”©Ó¦ĆÓ”ō Ó”©Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ŌĆö Ó”öÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”ĢÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ¦ć Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó””Ó”ŠÓ¦¤Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”ģÓ”©Ó”┐Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”»Óźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”ć Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”ČÓ”┐Ó”Ģ Ó”ō Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”┐Ó”Ģ Ó”żÓ”żÓ¦ŹÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŁÓ¦éÓ”«Ó”┐ Ó”øÓ”ŠÓ¦£Ó”Š Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”ČÓ”┐Ó”Ģ Ó”ō Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”┐Ó”Ģ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ŁÓ¦éÓ”«Ó”┐Ó”ĢÓ”Š Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”╣Ó”¼Ó¦ć Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”ĢÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”¬Ó”ŠÓ”üÓ”ÜÓ”Č Ó”¼Ó”øÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”£Ó”ŠÓ”▓Ó”┐ Ó”ĖÓ”░Ó¦ŹÓ”¼Ó”£Ó”©Ó¦ĆÓ”©Ó”żÓ”Š Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”åÓ”©Ó”¼Ó¦ćÓ”© Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”© Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŗÓ”©Ó”┐Ó”░ Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬Ó”ĢÓ”ŠÓ”░-Ó”öÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”ĢÓ”░Ó”Š, Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”ĀÓ¦ŗÓ””Ó¦ŹÓ”¦Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó”¼Ó¦ćÓ”© Ó”¬Ó¦üÓ”░Ó”©Ó¦ŗ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ĢÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ō Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░Óźż Ó”¬Ó¦āÓ”źÓ”┐Ó”¼Ó¦ĆÓ”░ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ė Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”éÓ”ĢÓ”¤ Ó”«Ó¦ŗÓ”ÜÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”£Ó”©Ó¦ŹÓ”» Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó””Ó”┐Ó”ĢÓ¦ćÓ”ć Ó”żÓ”ŠÓ”ĢÓ”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”åÓ”øÓ¦ćÓźż