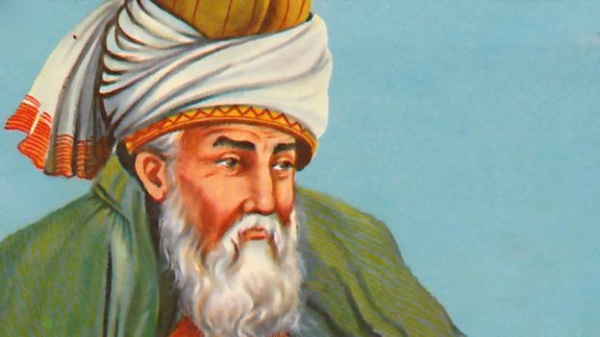Ó”¬Ó”ŠÓ”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”» Ó”£Ó¦ŹÓ”×Ó”ŠÓ”©Ó”ÜÓ”░Ó¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ”░ Ó”ćÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ć Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ¦āÓ”żÓ”┐ Ó”ō Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”» Ó”£Ó”ŠÓ”żÓ”┐Ó”ŚÓ¦ŗÓ”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ¦ĆÓ”░ Ó”£Ó¦ŹÓ”×Ó”ŠÓ”©Ó”¼Ó”┐Ó””Ó¦ŹÓ”»Ó”Š Ó”ģÓ”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ĆÓ”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”¼Ó”Š Ó”ÅÓ¦£Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”ōÓ¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”śÓ”¤Ó”©Ó”Š Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”©Ó¦¤Óźż Ó”åÓ”¦Ó¦üÓ”©Ó”┐Ó”ĢÓ”żÓ”Š Ó”ō Ó”ĖÓ¦ćÓ”ĢÓ¦üÓ”▓Ó”ŠÓ”░Ó”┐Ó”¤Ó”┐Ó”░ Ó”©Ó”ŠÓ”«Ó¦ć Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć, Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”« Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó¦ć Ó”¬Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó”«Ó”┐ Ó”¬Ó”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ”┐Ó”żÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”åÓ”ÜÓ”░Ó”Ż Ó”ÉÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”ĢÓ”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó¦ćÓ”ć Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”åÓ”ĖÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”Š Ó”ō Ó”ćÓ”ēÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”ŠÓ”£Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”½Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖÓ”┐ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐ Ó”£Ó”ŠÓ”▓Ó”ŠÓ”▓Ó”ēÓ””Ó¦ŹÓ””Ó”┐Ó”© Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”»Ó¦ćÓ”ĖÓ”¼ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ”” Ó”ĖÓ”¼Ó”ÜÓ¦ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ”┐ Ó”ĖÓ”«Ó”ŠÓ””Ó¦āÓ”ż Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”åÓ”ĖÓ”øÓ¦ć Ó”ÅÓ”żÓ¦ćÓ”ō Ó”ÅÓ”░ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”żÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”« Ó”śÓ”¤Ó¦ćÓ”©Ó”┐Óźż ӔŠӔ©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć ‘Ó””Ó”┐ Ó”©Ó”┐Ó”ē Ó”ćÓ¦¤Ó”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”ŠÓ”░’ Ó”«Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ŚÓ”ŠÓ”£Ó”┐Ó”©Ó¦ć Ó”░Ó¦ŗÓ”£Ó”┐Ó”©Ó”Š Ó”åÓ”▓Ó¦ĆÓ”░ Ó”ŚÓ¦üÓ”░Ó¦üÓ”żÓ¦ŹÓ”¼Ó”¬Ó¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”Ż Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”¤Ó”┐ ‘Ó”£Ó”¼Ó”ŠÓ”©’-Ó”ÅÓ”░ Ó”£Ó”©Ó¦ŹÓ”» Ó”¼Ó”ŠÓ”éÓ”▓Ó”ŠÓ¦¤ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ”” Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”╣Ó”▓Ó¦ŗÓźż
Ó”¼Ó”øÓ”░ Ó”ĢÓ¦¤Ó¦ćÓ”Ģ Ó”åÓ”ŚÓ¦ć Ó”ĢÓ¦ŗÓ”▓Ó¦ŹÓ”ĪÓ”¬Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”ĪÓ¦ćÓ”░ Ó”ŁÓ¦ŗÓ”ĢÓ”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤ Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”Ė Ó”«Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”¤Ó”┐Ó”© Ó”»Ó”¢Ó”© Ó”ģÓ”ŁÓ”┐Ó”©Ó¦ćÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó¦Ć Ó”ŚÓ¦ŗÓ¦¤Ó¦ćÓ”©Ó¦ćÓ”ź Ó”¬Ó”ŠÓ”▓Ó”¤Ó¦ŹÓ”░Ó¦ŗ-Ó”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”ĪÓ”┐Ó”ŁÓ¦ŗÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”ŻÓ¦ć Ó”¢Ó”ŠÓ”░Ó”ŠÓ”¬ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤ Ó”¬Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”© Ó”ōÓ”ćÓ”ĖÓ”«Ó¦¤ Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”¼Ó”©Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ü Ó”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”ÜÓ”ŠÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ”Š Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”¼Ó”ć Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Óźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”¤Ó”┐ Ó”øÓ”┐Ó”▓ Ó¦¦Ó¦®Ó¦”Ó¦” Ó”ČÓ”żÓ”ŠÓ”¼Ó¦ŹÓ””Ó¦ĆÓ”░ Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó”ĖÓ¦ŹÓ”» Ó”ĢÓ”¼Ó”┐ Ó”£Ó”ŠÓ”▓Ó”ŠÓ”▓Ó”ēÓ””Ó¦ŹÓ””Ó”┐Ó”© Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”▓Ó”«Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”© Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”Ė Ó”ģÓ”©Ó¦éÓ””Ó”┐Ó”ż Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”Š Ó”ĖÓ”éÓ”ĢÓ”▓Ó”©Óźż Ó”«Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”¤Ó”┐Ó”© Ó”¬Ó”░Ó¦ć Ó”ÅÓ”Ģ┬ĀÓ”ĖÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”ŠÓ¦ÄÓ”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ć┬ĀÓ”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©, ‘Ó”ÅÓ”¤Ó”Š Ó”åÓ”ĖÓ”▓Ó¦ć Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó”ĢÓ¦ćÓ”ć Ó”¼Ó””Ó”▓Ó¦ć Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż’ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”▓Ó¦ŹÓ”ĪÓ”¬Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ć-Ó”░ Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”Ģ Ó”ģÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓Ó”¼Ó”ŠÓ”«Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”Ė Ó”ģÓ”©Ó¦éÓ””Ó”┐Ó”ż Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”Š┬ĀÓ”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”╣Ó¦¤, This being human is a guest house/Every morning a new arrival/A joy, a depression, a meanness,/ŌĆŹsome momentary awareness comes/as an unexpected visitor.ŌĆØ
Ó”«Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĪÓ¦ŗÓ”©Ó”Š, Ó”¤Ó”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”ĪÓ”Š Ó”ĖÓ¦üÓ”ćÓ”©Ó”¤Ó”©Ó”ĖÓ”╣ Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ćÓ”░┬ĀÓ”åÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”┐Ó”Ģ Ó”¼Ó¦ŗÓ”ØÓ”ŠÓ”¬Ó¦£Ó”ŠÓ¦¤ Ó”¢Ó¦ŗÓ”░Ó”ŠÓ”Ģ Ó”£Ó¦üÓ”ŚÓ”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Óźż Ó”żÓ”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”©Ó”┐Ó”£Ó¦ćÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”ŠÓ”░Ó”ō Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”ĖÓ¦ŗÓ”ČÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓ Ó”«Ó”┐Ó”ĪÓ”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ¦¤ Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ŚÓ”ŁÓ¦ĆÓ”░ Ó”▓Ó”ŠÓ”ćÓ”©Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”ĘÓ”ĢÓ¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó””Ó”┐Ó”© Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”░Ó”ŻÓ”Š Ó”£Ó¦üÓ”ŚÓ”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ćÓźż┬ĀIf you are irritated by every rub, how will you ever get polished- Ó”ĖÓ¦ćÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐Óźż Ó”ÅÓ”øÓ”ŠÓ¦£Ó”Š Every moment I shape my destiny with a chisel. I am a carpenter of my own soul. Ó”ćÓ”©Ó¦ŹÓ”¤Ó”ŠÓ”░Ó”©Ó¦ćÓ”¤ Ó””Ó¦üÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ¦¤ Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”Ė-Ó”ÅÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó”ć Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ”┐ Ó”øÓ¦£Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ōÓ”ć Ó”▓Ó”ŠÓ”ćÓ”©Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗÓ”ć Ó”ģÓ”¼Ó”ČÓ¦ŹÓ”» Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”ćÓ¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó””Ó¦ŗÓ”ĢÓ”ŠÓ”©Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗÓ”░ Ó”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”ō Ó”¼Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”ŠÓ”©Ó¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”Ā Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ćÓźż Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”Ģ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤ Ó”»Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”░Ó”ŠÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”ŠÓ”£Ó”ŠÓ”░Ó¦ć┬ĀÓ”ĖÓ”░Ó¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”¦Ó”┐Ó”Ģ Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó¦ĆÓ”ż Ó”ĢÓ”¼Ó”┐┬ĀÓ”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”¼Ó”▓Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ćÓźż Ó”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”¦Ó”ŠÓ”░Ó”ŻÓ”ż Ó”░Ó”╣Ó”ĖÓ¦ŹÓ”»Ó”¬Ó¦üÓ”░Ó¦üÓ”Ę, Ó”ĖÓ¦üÓ”½Ó”┐, Ó””Ó”░Ó”¼Ó¦ćÓ”Č Ó”ō Ó”åÓ”▓Ó¦ŗÓ”ĢÓ”┐Ó”ż Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”Ę Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”¼Ó”░Ó¦ŹÓ”ŻÓ”©Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Óźż Ó”ĖÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ģÓ”░Ó¦ŹÓ”źÓ¦ć┬ĀÓ”»Ó””Ó”┐Ó”ō Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”¬Ó”¼Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ¦ćÓ”░Ó”åÓ”© Ó”ō Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ”┐Ó”ż Ó”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”© Ó”żÓ”¼Ó¦üÓ”ō Ó”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”«Ó¦üÓ”ĖÓ”▓Ó”┐Ó”« Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”¢Ó¦üÓ”¼ Ó”ĢÓ”«Ó”ć Ó”ēÓ”▓Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ćÓ”¢ Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Óźż
Ó”«Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”¤Ó”┐Ó”© Ó”»Ó¦ćÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”ģÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓Ó”¼Ó”ŠÓ”«Ó¦ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”żÓ”Š Ó”«Ó¦éÓ”▓Ó”ż Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó¦ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”«Ó”╣Ó”ŠÓ”ĢÓ”ŠÓ”¼Ó¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó¦¼ Ó”¢Ó”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”┐Ó”żÓ”ŠÓ”¼ ŌĆśÓ”«Ó”ĖÓ”©Ó”¼Ó”┐ŌĆÖ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”©Ó¦ćÓ¦¤Ó”ŠÓźż Ó¦½Ó¦” Ó”╣Ó”ŠÓ”£Ó”ŠÓ”░ Ó”▓Ó”ŠÓ”ćÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”«Ó¦éÓ”▓Ó”ż Ó”½Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖÓ”┐Ó”żÓ¦ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”╣Ó”▓Ó¦ćÓ”ō Ó”«Ó¦üÓ”ĖÓ”▓Ó”┐Ó”« Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”ĢÓ”┐Ó”żÓ”ŠÓ”¼ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”©Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š┬ĀÓ”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ÜÓ¦üÓ”░ Ó”åÓ”░Ó”¼Ó”┐ Ó”ČÓ”¼Ó¦ŹÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ÅÓ”øÓ”ŠÓ¦£Ó”Š Ó”ĖÓ”░Ó”ŠÓ”ĖÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”ŠÓ¦ćÓ”░Ó”åÓ”© Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”©Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š┬ĀÓ”©Ó¦łÓ”żÓ”┐Ó”Ģ Ó”ČÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”Š Ó”ĖÓ”«Ó¦āÓ””Ó¦ŹÓ”¦ Ó”¼Ó”╣Ó¦ü Ó”ŚÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬-Ó”ēÓ”¬Ó”ŠÓ”¢Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó¦ćÓ”ō Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”ŠÓ”░ Ó”░Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć (Ó”¼Ó”╣Ó¦ü Ó”¬Ó”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ”┐Ó”ż Ó”ōÓ”ć Ó”ģÓ”ĖÓ”«Ó”ŠÓ”¬Ó¦ŹÓ”ż Ó”ĢÓ”ŠÓ”£Ó”¤Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć ŌĆśÓ”¬Ó”ŠÓ”░Ó”ĖÓ¦ŹÓ”» Ó”ĢÓ¦ŗÓ”░Ó”åÓ”©ŌĆÖ Ó”©Ó”ŠÓ”«Ó¦ćÓ”ō Ó”¼Ó”▓Ó¦ć Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ćÓ”©)Óźż Ó”«Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”░Ó”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”Ī Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”¼Ó”¼Ó”┐Ó””Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓Ó¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖÓ”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”© Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó”ŠÓ”ĪÓ”┐Ó”£Ó¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¬Ó”Ģ Ó”½Ó”ŠÓ”żÓ¦ćÓ”«Ó¦ćÓ”╣ Ó”ĢÓ¦ćÓ”ĖÓ”ŠÓ”ŁÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”£ Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”▓Ó”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©, Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”ŁÓ”¼Ó”ż Ó”ĢÓ”ŠÓ¦ćÓ”░Ó”åÓ”© Ó”«Ó¦üÓ”¢Ó”ĖÓ¦ŹÓ”ź Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©Óźż ӔŠӔĢÓ”ŠÓ”░Ó”ŻÓ¦ć Ó”»Ó”¢Ó”© Ó”¢Ó¦üÓ”ČÓ”┐ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ¦¤ Ó”ĢÓ”ŠÓ¦ćÓ”░Ó”åÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ¦¤Ó”ŠÓ”ż Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó”żÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”©Ó”┐Ó”£Ó¦ć ŌĆśÓ”«Ó”ĖÓ”©Ó”¼Ó”┐ŌĆÖ Ó”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”©Ó¦ŹÓ”źÓ”¤Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć ‘Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ćÓ”░ Ó”ČÓ”┐Ó”ĢÓ¦£Ó¦ćÓ”░ Ó”ČÓ”┐Ó”ĢÓ¦£ Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”ÅÓ”░Ó”ō Ó”ČÓ”┐Ó”ĢÓ¦£’ Ó”ģÓ”░Ó¦ŹÓ”źÓ”ŠÓ¦Ä Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”« Ó”ō ‘Ó”ĢÓ”ŠÓ¦ćÓ”░Ó”åÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”żÓ”ŠÓ”½Ó”┐Ó”ĖÓ”┐Ó”░’ Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”ēÓ”▓Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ćÓ”¢ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”»Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”░Ó”ŠÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó¦ŹÓ”░Ó¦ć Ó”»Ó¦ć Ó”ģÓ”©Ó¦éÓ””Ó”┐Ó”ż Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”Š Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”┐ Ó”╣Ó¦¤ Ó”ÅÓ”żÓ¦ć Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¬Ó”ŠÓ”░Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”╣Ó”ŠÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”ć Ó”ŚÓ¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”░Ó”ŠÓ”¤Ó”ŚÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”Ė Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”¼Ó”¼Ó”┐Ó””Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓Ó¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ĆÓ”© Ó”ĖÓ¦üÓ”½Ó”┐Ó”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”¬Ó”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ”┐Ó”ż Ó”£Ó”ŠÓ”ŁÓ”┐Ó”” Ó”«Ó¦üÓ”£Ó”ŠÓ””Ó¦ŹÓ””Ó¦ćÓ””Ó”┐ Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐ Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”©,┬Ā‘Ó”ćÓ”éÓ”░Ó¦ćÓ”£Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”»Ó¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”Ę Ó”ŁÓ”ŠÓ”▓Ó”ŠÓ¦ćÓ”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ć Ó”żÓ”Š Ó”¢Ó¦üÓ”¼Ó”ć Ó”ĖÓ¦üÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¬Ó”ŠÓ”░ Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”»Ó¦ć Ó”«Ó¦éÓ”▓Ó¦ŹÓ”» Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ĢÓ¦ćÓ”©Ó”Š Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć Ó”ĖÓ¦ćÓ”¤Ó”┐ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”ĖÓ”éÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ¦āÓ”żÓ”┐ Ó”ō Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”« Ó”¼Ó”ŠÓ”” Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£Ó¦ć Ó”¢Ó”░Ó”Ü Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ćÓźż’
Ó”ōÓ”«Ó”┐Ó”” Ó”ĖÓ”ŠÓ”½Ó”┐ Ó”ĢÓ”ŠÓ¦ćÓ”░Ó”åÓ”© Ó”©Ó”Š Ó”¬Ó”ŠÓ”Ā Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”¬Ó”ŠÓ”ĀÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”¼Ó¦ćÓ”▓ Ó”©Ó”Š Ó”¬Ó¦£Ó¦ćÓ”ć Ó”«Ó”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¤Ó”© Ó”¬Ó¦£Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”żÓ¦üÓ”▓Ó”©Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”ģÓ”¼Ó”ČÓ¦ŹÓ”» Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ÜÓ”▓Ó”┐Ó”ż Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó”«Ó”żÓ¦ćÓ”░ Ó”©Ó”ŠÓ”©Ó”ŠÓ”© Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó¦ć Ó”ĖÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”© Ó”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”ÅÓ”¤Ó”┐ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”«Ó¦üÓ”ĖÓ”▓Ó”┐Ó”« Ó”ĢÓ”©Ó”¤Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĖÓ”¤Ó¦ć Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ČÓ¦ŹÓ”© Ó”żÓ¦üÓ”▓Ó”żÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”ōÓ”ć Ó”ĖÓ”«Ó¦¤Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó”┐ Ó”ĖÓ”éÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ¦āÓ”żÓ”┐ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”»Ó”ŠÓ¦¤Ó¦Ć ӔŠӔ¦Ó”░Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”żÓ”¼Ó”┐Ó”░Ó¦ŗÓ”¦Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”»Ó”źÓ¦ćÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤ Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”Ż Ó”ō Ó”ĖÓ¦üÓ”»Ó¦ŗÓ”Ś Ó”øÓ”┐Ó”▓Óźż Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£ Ó”»Ó¦ć Ó”ČÓ¦üÓ”¦Ó¦ü Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”╣Ó”ŠÓ”ż Ó”¦Ó”░Ó”ŠÓ”¦Ó”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó”┐Ó”ż Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓ Ó”ĖÓ¦ćÓ”¤Ó”┐Ó”ć Ó”©Ó¦¤, Ó”ÅÓ”¤Ó”┐ Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó”┐ Ó”¬Ó”ŠÓ”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ÉÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”Ģ Ó”ēÓ¦ÄÓ”ĢÓ”░Ó¦ŹÓ”ĘÓ¦ćÓ”░Ó”ō Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐Ó”¦Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć
Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó¦¦Ó¦® Ó”ČÓ”żÓ”ŠÓ”¼Ó¦ŹÓ””Ó¦ĆÓ”░ Ó”ČÓ¦üÓ”░Ó¦üÓ”░ Ó””Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”░Ó¦ŹÓ”żÓ”«Ó”ŠÓ”© Ó”åÓ”½Ó”ŚÓ”ŠÓ”©Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”£Ó”ŠÓ¦¤Ó”ŚÓ”ŠÓ¦¤ Ó”£Ó”©Ó¦ŹÓ”«Ó”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”╣Ó”Ż Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”¬Ó”░Ó¦ć Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”ĖÓ”¬Ó”░Ó”┐Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”¼Ó”░Ó¦ŹÓ”żÓ”«Ó”ŠÓ”© Ó”żÓ¦üÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”┐Ó”░┬ĀÓ”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó”Š-Ó¦¤ Ó”ŚÓ”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”źÓ”┐Ó”żÓ¦ü Ó”╣Ó”©Óźż Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”¬Ó”┐Ó”żÓ”Š Ó”åÓ”▓Ó¦ćÓ”« Ó”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”© Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”« Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ÜÓ”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”«Ó”©Ó”»Ó¦ŗÓ”ŚÓ¦Ć Ó”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐Ó”ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”« Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”ĖÓ¦üÓ”½Ó”┐Ó”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó””Ó¦ĆÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”Š Ó””Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”ČÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”ŠÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦¤Ó¦ŗÓ”£Ó”©Ó¦ć Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”ĖÓ”┐Ó”░Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ¦¤ Ó”»Ó”ŠÓ”©Óźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”©Ó¦ć Ó”ĖÓ¦üÓ”©Ó¦ŹÓ”©Ó”┐ Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ”ćÓ”©-Ó”ĢÓ”ŠÓ”©Ó¦üÓ”© Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”¬Ó¦£Ó”ŠÓ”ČÓ¦ŗÓ”©Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”© Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ĆÓ¦¤┬ĀÓ”ČÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”Ģ Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó”Š Ó”½Ó¦ćÓ”░Ó”ż Ó”åÓ”ĖÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”ĖÓ¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”©Ó¦ć Ó”ÅÓ”Ģ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¼Ó¦ĆÓ”Ż Ó”¬Ó”░Ó”┐Ó”¼Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”£Ó”Ģ Ó”ČÓ”ŠÓ”«Ó”Ė-Ó”ć-Ó”żÓ”ŠÓ”¼Ó”░Ó”┐Ó”£-Ó”ÅÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”ŠÓ¦Ä Ó”╣Ó¦¤ Ó”żÓ”ŠÓ”░Óźż Ó”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”ŚÓ¦üÓ”░Ó¦ü Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”ōÓ”ć Ó””Ó¦ü’Ó”£Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ŚÓ”ŁÓ¦ĆÓ”░ Ó”¼Ó”©Ó¦ŹÓ”¦Ó¦üÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”Ģ Ó”¼Ó”┐Ó”żÓ”░Ó¦ŹÓ”Ģ Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ”▓Ó¦ćÓ”ō ӔŠӔ¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”ĖÓ”¼Ó”ŠÓ”ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”«Ó”ż, Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”Š Ó”ō Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”ÜÓ”░Ó¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ¦¤ Ó”ČÓ”ŠÓ”«Ó”Ė Ó”ĖÓ¦üÓ””Ó¦ĆÓ”░Ó¦ŹÓ”ś Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼ Ó”¼Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó¦ĆÓ”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”©Ó¦ŹÓ”ź┬Ā”Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ŌĆÖÓ”Ė Ó”ĖÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”¤”-ӔŠӔ¼Ó¦ŹÓ”░Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ī Ó”ŚÓ¦üÓ”Ü Ó””Ó¦ćÓ”¢Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©, Ó”ĢÓ¦ĆÓ”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ¦ćÓ”żÓ”ŠÓ”¼Ó”┐ Ó”ÅÓ”▓Ó¦ćÓ”«Ó”¤Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ČÓ¦ŹÓ”© Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”ČÓ”ŠÓ”«Ó”Ė Ó”ēÓ””Ó¦ŹÓ”»Ó”ż Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”¼Ó”┐Ó”żÓ”░Ó¦ŹÓ”Ģ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”ĢÓ”ŠÓ¦ćÓ”░Ó”åÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ¦¤Ó”ŠÓ”żÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗÓ”░ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¢Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”åÓ”▓Ó¦ŹÓ”▓Ó”ŠÓ”╣Ó”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ÜÓ”░Ó¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ¦¤ Ó”ÅÓ”ĢÓ”ŠÓ”ŚÓ¦ŹÓ”░ Ó”ĖÓ”ŠÓ”¦Ó”©Ó”ŠÓ”░ Ó”ŚÓ¦üÓ”░Ó¦üÓ”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓźż Ó”¢Ó¦ŗÓ””Ó”ŠÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐ Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”©Ó”┐Ó”ŚÓ¦éÓ¦Ø┬ĀÓ”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”«Ó¦ćÓ”░ Ó”©Ó”£Ó”┐Ó”░ Ó”░Ó¦ćÓ”¢Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”żÓ”Š Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”¬Ó¦ćÓ¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”ĖÓ¦üÓ”©Ó¦ŹÓ”©Ó”┐ Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó¦ćÓ”░ Ó”ČÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó”Š Ó”ÅÓ”▓Ó”«Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ¦üÓ”½Ó”┐Ó”¼Ó”ŠÓ””Ó¦Ć Ó”¦Ó”ŠÓ”░Ó”Š Ó”ō Ó”ČÓ”ŠÓ”«Ó”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ŚÓ”ŁÓ¦ĆÓ”░ Ó”ÜÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ”Š Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”¬Ó¦ŹÓ”ż Ó”ČÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”ŠÓ¦¤Óźż
Ó”ĢÓ¦ćÓ”ĖÓ”ŠÓ”ŁÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”£ Ó”£Ó”ŠÓ”©Ó”ŠÓ”©, Ó”ōÓ”ć Ó”ģÓ”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”┐Ó”Ģ (Ó”ČÓ”ŠÓ”«Ó”Ė-Ó”ć-Ó”żÓ”ŠÓ”¼Ó”░Ó”┐Ó”£) Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó”░Ó¦ŹÓ””Ó”ŠÓ¦¤ Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”żÓ¦ÄÓ”ĢÓ”ŠÓ”▓Ó¦ĆÓ”© Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”»Ó””Ó¦ćÓ”░ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”åÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”©Óźż Ó”żÓ”¼Ó¦üÓ”ō Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ¦¤ Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░┬ĀÓ”¼Ó”┐Ó”ČÓ”ŠÓ”▓ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”░Ó”ŠÓ”ŚÓ¦Ć Ó”ŚÓ¦ŗÓ”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ¦Ć Ó”żÓ¦łÓ”░Ó”┐ Ó”╣Ó¦¤Óźż Ó”żÓ”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”ĖÓ¦üÓ”½Ó”┐, Ó”åÓ”▓Ó¦ćÓ”«-Ó”ōÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó”Š, Ó”ćÓ”╣Ó¦üÓ””Ó”┐, Ó”¢Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó”ŠÓ”©, Ó”ÅÓ”«Ó”©Ó”ĢÓ”┐ Ó”ĖÓ¦üÓ”©Ó¦ŹÓ”©Ó”┐ Ó”ĖÓ¦ćÓ”▓Ó”£Ó¦üÓ”Ģ Ó”ČÓ”ŠÓ”ĖÓ”ĢÓ”░Ó”ŠÓ”ō Ó”░Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ŌĆÖÓ”Ė Ó”ĖÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”¤-ӔŠӔŚÓ¦üÓ”Ü Ó”ōÓ”ć Ó”ĖÓ”«Ó¦¤Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”░Ó”ŠÓ”£Ó”©Ó¦łÓ”żÓ”┐Ó”Ģ Ó”śÓ”¤Ó”©Ó”ŠÓ”ÜÓ”ĢÓ¦ŹÓ”░ Ó”ō Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”ČÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”Š┬ĀÓ”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó¦ć Ó”ĢÓ¦ćÓ”«Ó”© Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼ Ó”½Ó¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓ Ó”żÓ”Š Ó”ŁÓ”ŠÓ”▓Ó”ŠÓ¦ćÓ”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó¦ć Ó”ÅÓ”©Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”▓Ó”┐Ó”¢Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©, ‘Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó”¬Ó”░Ó”ŠÓ¦¤Ó”Ż Ó”¬Ó”░Ó”┐Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”£Ó”©Ó¦ŹÓ”« Ó”©Ó¦ćÓ”© Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”ĖÓ”ŠÓ”░Ó”Š Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”© Ó”¬Ó”ŠÓ”üÓ”Ü Ó”ōÓ¦¤Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ż Ó”©Ó”ŠÓ”«Ó”ŠÓ”£ Ó”ō Ó”░Ó¦ŗÓ”£Ó”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”¦Ó”ŠÓ”© Ó”¬Ó”ŠÓ”▓Ó”© Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż’ Ó”ÅÓ”«Ó”©Ó”ĢÓ”┐ Ó”ŚÓ¦üÓ”ÜÓ¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”ćÓ¦¤Ó¦ćÓ”ō Ó”ÅÓ”ĖÓ”¼ Ó”żÓ”źÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó”ŠÓ”ČÓ”ŠÓ”¬Ó”ŠÓ”ČÓ”┐ Ó”ÜÓ¦éÓ¦£Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”ż Ó”«Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ”¼Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£ ”Ó”ĖÓ”ĢÓ”▓ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”┐Ó”ż Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”£Ó”ŠÓ¦¤Ó”ŚÓ”Š Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”░Ó¦ć Ó””Ó”ŠÓ”üÓ¦£Ó”ŠÓ”©Ó¦ŗ Ó”ÅÓ”Ģ ŌĆśÓ”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”«Ó¦ćÓ”░ Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«ŌĆÖ Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć’ Ó”¼Ó”▓Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Óźż Ó”ōÓ”ć Ó”¦Ó”░Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó”ŠÓ”ĀÓ¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”«Ó¦üÓ”ĖÓ”▓Ó”┐Ó”« Ó”ČÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”Š Ó”żÓ”źÓ”Š Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”«Ó¦éÓ”▓ Ó”åÓ”ćÓ”ĪÓ”┐Ó¦¤Ó”Š Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ćÓ”ć Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”¼Ó”ŠÓ”” Ó”¬Ó¦£Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”ōÓ¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”©Ó”Š Ó”░Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”«Ó¦ŗÓ”£Ó”ŠÓ””Ó¦ŹÓ””Ó¦ćÓ””Ó”┐ Ó”»Ó¦ćÓ”«Ó”©Ó”¤Ó”┐ Ó”¼Ó”▓Ó”øÓ¦ćÓ”©, Ó”ćÓ”ēÓ”©Ó”┐Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖÓ”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”£Ó”«Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ¦éÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó”¬Ó”ŠÓ”ż Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”ĢÓ”ŠÓ¦ćÓ”░Ó”åÓ”© Ó”ćÓ”╣Ó¦üÓ””Ó”┐ Ó”ō Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”©Ó””Ó¦ćÓ”░ ‘Ó”åÓ”╣Ó”▓Ó¦ć Ó”ĢÓ”┐Ó”żÓ”ŠÓ”¼’ Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ĆÓ”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”åÓ”£Ó”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó””Ó”┐Ó”©Ó¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”»Ó¦ć Ó”ćÓ”ēÓ”©Ó”┐Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖÓ”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”¤Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”¬Ó¦éÓ”£Ó”Š Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć Ó”ĖÓ¦ćÓ”¤Ó”┐ Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”«Ó¦üÓ”ĖÓ”▓Ó”┐Ó”« Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”ŠÓ”¬Ó”¤ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ćÓ”ć Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż
Ó”ĢÓ¦ŗÓ”▓Ó¦ŹÓ”ĪÓ”¬Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”éÓ”ČÓ¦ŹÓ”▓Ó”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”╣Ó¦ü Ó”åÓ”ŚÓ¦ćÓ”ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”Š Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”” Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š Ó”ČÓ¦üÓ”░Ó¦ü Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ĪÓ”┐Ó”ēÓ”Ģ Ó”ćÓ”ēÓ”©Ó”┐Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖÓ”┐Ó”¤Ó”┐Ó”░┬ĀÓ”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó”┐Ó”Ģ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó”ŠÓ”ĪÓ”┐Ó”£ Ó”ō Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”ÜÓ¦ŹÓ”» Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó”Ģ Ó”ģÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¬Ó”Ģ Ó”ōÓ”«Ó”┐Ó”” Ó”ĖÓ”ŠÓ”½Ó”┐ Ó”¼Ó”▓Ó”øÓ¦ćÓ”©, Ó”ŁÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”¤Ó¦ŗÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”© Ó”¬Ó”┐Ó”░Ó”┐Ó¦¤Ó”Ī Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ćÓ”ć Ó”¬Ó”ŠÓ”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”åÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”┐Ó”Ģ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”ÅÓ”░ Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó”┐ Ó”ČÓ”┐Ó”ĢÓ¦£ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”åÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”¬Ó¦£Ó”Š Ó”ČÓ¦üÓ”░Ó¦ü Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”żÓ”¢Ó”©Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó”Ģ Ó”ō Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”¬Ó”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ”┐Ó”░Ó”┐Ó”Š Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ ‘Ó”«Ó”░Ó¦üÓ”░ Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«’ Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”åÓ”ćÓ”©Ó”┐ Ó”ō Ó”©Ó¦łÓ”żÓ”┐Ó”Ģ Ó”ČÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”Š-Ó””Ó¦ĆÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”╣Ó”ŠÓ”½Ó”┐Ó”£Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”żÓ¦ŗ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”Ģ Ó”ēÓ””Ó¦ŹÓ”¦Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”ĖÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”« Ó”╣Ó”©Ó”©Ó”┐Óźż Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”½Ó”┐ Ó”£Ó”ŠÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©, Ó”żÓ”ŠÓ”░Ó”Š Ó”»Ó¦ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¢Ó¦ŹÓ”»Ó”Š Ó””Ó”ŠÓ”üÓ¦£ Ó”ĢÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”żÓ”Š Ó”╣Ó”▓Ó¦ŗ, ‘Ó”ōÓ”ćÓ”ĖÓ”¼ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐ Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”éÓ”ĖÓ¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”ČÓ¦ć Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ”▓Ó¦ćÓ”ō Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”ŻÓ¦ć Ó”åÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”┐Ó”Ģ Ó”╣Ó”©Ó”©Ó”┐’Óźż Ó”ÅÓ”¤Ó”┐ Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”ĖÓ”«Ó¦¤ Ó”øÓ”┐Ó”▓ Ó”»Ó”¢Ó”© Ó”«Ó¦üÓ”ĖÓ”▓Ó”┐Ó”«Ó””Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ”ćÓ”©Ó”┐ Ó”ēÓ”¬Ó”ŠÓ¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó¦łÓ”ĘÓ”«Ó¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”£Ó”ŠÓ”▓Ó¦ć Ó”åÓ”¤Ó”ĢÓ”ŠÓ”©Ó¦ŗ Ó”╣Ó”żÓ¦ŗÓźż Ó¦¦Ó¦ŁÓ¦«Ó¦” Ó”ĖÓ”ŠÓ”▓ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ÜÓ”▓Ó¦ć Ó”åÓ”ĖÓ”Š Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”åÓ”ćÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”ŠÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”«Ó¦ć Ó”ĢÓ”ż Ó”«Ó¦üÓ”ĖÓ”▓Ó”┐Ó”« Ó”»Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”░Ó”ŠÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó¦ŹÓ”░Ó¦ć┬ĀÓ”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”¼Ó¦ćÓ”Č Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó”¼Ó¦ćÓ”© Ó”ÅÓ”░ Ó”ĖÓ”éÓ”¢Ó¦ŹÓ”»Ó”Š Ó”ĖÓ”éÓ”ĢÓ¦üÓ”ÜÓ”┐Ó”ż Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ”¦Ó”ŠÓ”░Ó”Ż Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”øÓ”┐Ó”▓Óźż Ó”ÅÓ”░ Ó¦¦Ó¦”Ó¦” Ó”¼Ó”øÓ”░ Ó”¬Ó”░ Ó”ÅÓ”ĖÓ¦ćÓ”ō Ó”»Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”░Ó”ŠÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ¦üÓ”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”« Ó”ĢÓ¦ŗÓ”░Ó¦ŹÓ”¤ ‘Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”» Ó”ĖÓ”¼ Ó”£Ó”ŠÓ”żÓ”┐Ó”ŚÓ¦ŗÓ”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ¦ĆÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć, Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”©Ó””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”«Ó¦üÓ”ĖÓ”▓Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó””Ó¦ćÓ”░ Ó”śÓ¦ŗÓ”░ Ó”ČÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó¦üÓ”żÓ”Š’Ó”░ Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”ēÓ”▓Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ćÓ”¢ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”©Óźż Ó¦¦Ó¦«Ó¦»Ó¦« Ó”ĖÓ”ŠÓ”▓Ó¦ć Ó”«Ó”ĖÓ”©Ó”¼Ó”┐Ó”░ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ć Ó”ĖÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”░ Ó”£Ó¦ćÓ”«Ó”Ė Ó”░Ó¦ćÓ”ĪÓ”╣Ó”ŠÓ”ēÓ”Ė Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó¦ćÓ”©, ‘Ó”»Ó”ŠÓ”░Ó”Š Ó””Ó¦üÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”¼Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ś Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”¢Ó¦ŗÓ””Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”Ģ Ó”ŚÓ¦£Ó”żÓ¦ć Ó”ÜÓ”ŠÓ”© Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”åÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”┐Ó”Ģ Ó”ÜÓ”░Ó¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ¦¤ Ó”©Ó”┐Ó”£Ó¦ćÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”▓Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó””Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”ÜÓ”ŠÓ”© Ó”«Ó”ĖÓ”©Ó”¼Ó”┐ Ó”żÓ”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓźż’ Ó”ÅÓ”ĖÓ”¼ Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”ŻÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”ō Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó”ĢÓ¦ć Ó”åÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż
Ó”ĢÓ¦¤Ó¦ćÓ”Ģ Ó”¼Ó¦ŗÓ””Ó¦ŹÓ”¦Ó”Š Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó”ĢÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”ŠÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”«Ó¦ć Ó”ćÓ”éÓ”░Ó¦ćÓ”£Ó”┐Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ¦ĆÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”░Ó”ŠÓ”£Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”╣Ó”ŠÓ”£Ó”┐Ó”░Ó”Š Ó”¬Ó”ŠÓ”ĢÓ”ŠÓ”¬Ó¦ŗÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ż Ó”╣Ó¦¤Óźż Ó”żÓ”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”åÓ”░ ӔŠӔ©Ó”┐Ó”ĢÓ”▓Ó”ĖÓ”©, ӔŠӔ£Ó¦ć Ó”åÓ”░Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó”┐ Ó”ō Ó”åÓ”©Ó”«Ó”ŠÓ”░Ó”┐ Ó”ČÓ”┐Ó”«Ó¦ćÓ”▓ Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”»Ó”żÓ”«Óźż Ó”åÓ”░ Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”«Ó”ŠÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”«Ó¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”¬Ó”ŠÓ”ĀÓ”ĢÓ”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó”żÓ”Š Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¬Ó”ĢÓ”«Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ¦¤ Ó”øÓ¦£Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”¬Ó¦£Ó¦ćÓźż Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó”Ģ Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”©Ó”©, Ó”ÅÓ”¢Ó”ŠÓ”©Ó¦ć Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”ŁÓ¦éÓ”«Ó”┐Ó”ĢÓ”Š Ó”©Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”½Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖÓ”┐ Ó”¬Ó¦£Ó”żÓ¦ć Ó”¼Ó”Š Ó”▓Ó”┐Ó”¢Ó”żÓ¦ć Ó”£Ó”ŠÓ”©Ó”żÓ¦ćÓ”© Ó”©Ó”ŠÓźż┬ĀÓ¦©Ó¦” Ó”ČÓ”żÓ”ĢÓ¦ć Ó”ÅÓ”ĖÓ¦ć Ó¦¦Ó¦» Ó”ČÓ”żÓ”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”© Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ¦ŹÓ”» Ó”åÓ”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”╣Ó”ŠÓ”£Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”© Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐Óźż┬ĀÓ”ÅÓ”░ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ¦ŹÓ”» Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó”¦Ó”░Ó”©Ó¦ćÓ”░Óźż
Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”Ė Ó¦¦Ó¦»Ó¦®Ó¦Ł Ó”ĖÓ”ŠÓ”▓Ó¦ć Ó”¤Ó¦ćÓ”©Ó¦ćÓ”ĖÓ”┐Ó”░ Ó”ÜÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¤Ó¦ŹÓ”¤Ó”ŠÓ”©Ó¦üÓ”ŚÓ”ŠÓ¦¤ Ó”£Ó”©Ó¦ŹÓ”«Ó”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”╣Ó”Ż Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”© Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”ĖÓ¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”©Ó¦ćÓ”ć Ó”¼Ó¦ćÓ¦£Ó¦ć Ó”ōÓ”ĀÓ¦ćÓ”©Óźż Ó¦¦Ó¦»Ó¦ŁÓ¦¦ Ó”ĖÓ”ŠÓ”▓Ó¦ć Ó”ćÓ”éÓ”░Ó¦ćÓ”£Ó”┐ Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”¬Ó”┐Ó”ÅÓ”ćÓ”ÜÓ”ĪÓ”┐ Ó”ĪÓ”┐Ó”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”┐ Ó”©Ó¦ćÓ”© Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”ÅÓ”ĢÓ”ć Ó”¼Ó”øÓ”░ Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”« Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”ć ‘Ó””Ó”┐ Ó”£Ó¦üÓ”Ė’ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”ŠÓ”Č Ó”╣Ó¦¤Óźż Ó”ōÓ”ć Ó””Ó”ČÓ”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó”ČÓ¦ćÓ”Ę Ó””Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ¦ć Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”źÓ”« Ó”£Ó”ŠÓ”©Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”©Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ü Ó”░Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”¤ Ó”¼Ó¦ŹÓ”▓Ó”ŠÓ”ć Ó”åÓ”░Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó”┐-Ó”░ Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”¬Ó”┐ Ó”¦Ó”░Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”©, Ó”ÅÓ”¤Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ØÓ¦üÓ”▓Ó”┐ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”╣Ó”¼Ó¦ćÓźż Ó”ÅÓ”░ Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦ć, Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”© Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”░Ó¦éÓ”¬ Ó””Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”╣Ó”¼Ó¦ć (Ó”żÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”Č Ó”¼Ó”øÓ”░Ó¦ćÓ”░Ó”ō Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ”┐ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤ Ó”¦Ó”░Ó¦ć Ó””Ó”┐ Ó”©Ó”┐Ó”ē Ó”ćÓ¦¤Ó”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”«Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ŚÓ”ŠÓ”£Ó”┐Ó”©Ó¦ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”▓Ó”ŠÓ”ć-Ó”ÅÓ”░ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”Š Ó”øÓ”ŠÓ”¬Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Óźż Ó”¬Ó¦üÓ”░Ó¦üÓ”ĘÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”¦Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”åÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó¦ŗÓ”▓Ó”© Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó¦¦Ó¦»Ó¦»Ó¦” Ó”ĖÓ”ŠÓ”▓Ó¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”ŠÓ”ČÓ”┐Ó”ż Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ”” Ó”¼Ó”ć ‘Ó”åÓ¦¤Ó”░Ó”© Ó”£Ó”© : Ó”ģÓ¦ŹÓ”»Ó”Š Ó”¼Ó¦üÓ”Ģ Ó”ģÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¼Ó”ŠÓ”ēÓ”¤Ó”«Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©’-Ó”ÅÓ”░ Ó”ōÓ”ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ĢÓ”ō Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”¬Ó”ÖÓ¦ŹÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ”” Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”©)Óźż Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”Ė Ó”ĢÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”« Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”¬Ó¦£Ó”ŠÓ”ČÓ¦ŗÓ”©Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”©Ó”©Ó”┐Óźż Ó”¬Ó”░Ó¦ć Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”üÓ”░ Ó”£Ó”░Ó¦ŹÓ”£Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ”Š Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”½Ó¦ŗÓ”©Ó¦ć Ó”©Ó”┐Ó”£Ó¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”¬Ó¦ŹÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”£Ó”ŠÓ”©Ó”ŠÓ”©Óźż Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”¬Ó¦ŹÓ”©Ó¦ć Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”©Ó””Ó¦ĆÓ”░ Ó”©Ó”┐Ó”ĢÓ”¤Ó”¼Ó”░Ó¦ŹÓ”żÓ¦Ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”¼Ó”ŠÓ”üÓ”¦Ó¦ćÓ”░ Ó”ōÓ”¬Ó”░ Ó”ČÓ¦üÓ¦¤Ó¦ć Ó”åÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”ģÓ”ÜÓ¦ćÓ”©Ó”Š Ó”ÅÓ”ĢÓ”£Ó”© Ó”ÜÓ”żÓ¦üÓ”░Ó¦ŹÓ””Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”åÓ”▓Ó¦ŗÓ¦¤ Ó”śÓ¦ćÓ”░Ó”Š Ó”ģÓ”¼Ó”ĖÓ¦ŹÓ”źÓ”ŠÓ¦¤ Ó”ÅÓ”ĖÓ¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”▓Ó”øÓ¦ćÓ”©, ‘Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”żÓ¦ŗÓ”«Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”ŁÓ”ŠÓ”▓Ó”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐’Óźż Ó”ōÓ”ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”åÓ”ŚÓ¦ć Ó”ĢÓ”¢Ó”©Ó¦ŗ Ó””Ó¦ćÓ”¢Ó¦ćÓ”©Ó”©Ó”┐ Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”ĖÓźż Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐ Ó”½Ó”┐Ó”▓Ó”ŠÓ”ĪÓ¦ćÓ”▓Ó”½Ó”┐Ó¦¤Ó”Š-Ó”░ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó”ŠÓ¦ć Ó”ÅÓ”Ģ Ó”żÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”Š Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”«Ó¦ćÓ”▓Ó”©Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó””Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”¬Ó”ŠÓ”© Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐Óźż Ó”ōÓ”ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐Ó”ć Ó”ōÓ”ć Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”«Ó¦ćÓ”▓Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”©Ó¦ćÓ”żÓ”ŠÓźż Ó”¬Ó”░Ó¦ć Ó”ĖÓ¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”©Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”Ė Ó”¬Ó¦£Ó”ŠÓ”ČÓ¦ŗÓ”©Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó””Ó”┐Ó”© Ó”ĢÓ”ŠÓ”¤Ó”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”ČÓ¦üÓ”░Ó¦ü Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”© Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”ŁÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”¤Ó¦ŗÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”© Ó”åÓ”«Ó”▓Ó¦ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”▓Ó”ŠÓ”ćÓ¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”åÓ”¼Ó”ŠÓ”░ Ó”¬Ó¦£Ó¦ć Ó”©Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”ÅÓ”░Ó”¬Ó”░ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”ĪÓ”£Ó”©Ó¦ćÓ”░Ó”ō Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ”┐ Ó”¼Ó”ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó¦ćÓ”©Óźż
Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ”▓Ó”ŠÓ”¬Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”Ė Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć ‘Ó”╣Ó¦āÓ””Ó¦¤ Ó”¢Ó¦üÓ”▓Ó¦ć Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š Ó”░Ó”╣Ó”ĖÓ¦ŹÓ”»’ Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”ēÓ”▓Ó¦ŹÓ”▓Ó¦ćÓ”¢ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”©, Ó”ÅÓ”¤Ó”┐ Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”£Ó”┐Ó”©Ó”┐Ó”Ė Ó”»Ó”Š Ó”åÓ”¬Ó”©Ó”┐ Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”ŠÓ¦¤ Ó”¦Ó”░Ó¦ć Ó”¼Ó”░Ó¦ŹÓ”ŻÓ”©Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó”¼Ó¦ćÓ”© Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ōÓ”ćÓ”ĖÓ”¼ Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”¦Ó”░Ó”ŠÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦¤Ó”ŠÓ”ĖÓ”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”░Ó¦éÓ”¬ Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£Ó¦ć Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦üÓ”¤Ó”Š Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”¦Ó¦ĆÓ”©Ó”żÓ”Š Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐Óźż ӔŠӔ£Ó”©Ó¦ŹÓ”» Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”£Ó¦£Ó”┐Ó”ż Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”¼Ó”ŠÓ”” Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”¼Ó”┐Ó”¢Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ż Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”Š Like This Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”åÓ”▓Ó”ŠÓ”¬ Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤Óźż Ó”åÓ”░Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦üÓ”¤Ó”Š Ó”ĖÓ”żÓ”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ”¤Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”▓Ó”ŠÓ”ćÓ”© Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ”” Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”©, Whoever asks you about the Houris, show (your) face (and say) ŌĆśLike thisŌĆÖ.┬Ā Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó¦ć Ó”¼Ó¦ćÓ”╣Ó¦ćÓ”ČÓ”żÓ”┐ Ó”╣Ó¦üÓ”░Ó””Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”¼Ó”▓Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć, Ó”żÓ”ŠÓ”░Ó”Š Ó”ĖÓ”żÓ¦ĆÓźż Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”Ė Ó”ÅÓ”¢Ó”ŠÓ”©Ó¦ć Ó”ĖÓ”░Ó”ŠÓ”ĖÓ”░Ó”┐ Ó”ČÓ”¼Ó¦ŹÓ””Ó”¤Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”ÅÓ¦£Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ”” Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”©, Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ć Ó”▓Ó”ŠÓ”ćÓ”©Ó”¤Ó”┐ Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć, If anyone asks you how the perfect satisfaction of all our sexual wanting will look, lift your face and say, Like this. Ó”ÅÓ”¢Ó”ŠÓ”©Ó¦ć Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”ŠÓ”¬Ó”¤Ó”ć Ó”╣Ó”ŠÓ”ōÓ¦¤Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ć Ó”ŚÓ¦ćÓ”▓Óźż Ó”ÅÓ”«Ó”©Ó”ĢÓ”┐ Ó”ÅÓ”ĢÓ”ć Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ¦¤ Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”» Ó”£Ó”ŠÓ¦¤Ó”ŚÓ”ŠÓ¦¤ Ó”£Ó¦ćÓ”ĖÓ”ŠÓ”Ė Ó”ō Ó”£Ó¦ŗÓ”ĖÓ¦ćÓ”½ Ó”©Ó”ŠÓ”« Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”© Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”ĖÓźż ӔŠӔ¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”£Ó”┐Ó”£Ó¦ŹÓ”×Ó”ŠÓ”ĖÓ”Š Ó”ĢÓ”░Ó”▓Ó¦ć Ó”¼Ó”▓Ó”▓Ó¦ćÓ”©, ‘Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó”┐ Ó”ČÓ”¼Ó¦ŹÓ”” Ó”ō Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼ Ó”»Ó””Ó”┐ Ó”¼Ó”ŠÓ”” Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”ō Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ”┐ Ó”żÓ”ŠÓ”╣Ó”▓Ó¦ć Ó”ĖÓ¦ćÓ”¤Ó”┐ Ó”ÅÓ”¢Ó”© Ó”«Ó¦üÓ”øÓ¦ć Ó”½Ó¦ćÓ”▓Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó”¼Ó”ŠÓ¦ć Ó”©Ó”ŠÓźż’ Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”¼Ó”▓Ó”▓Ó¦ćÓ”©, ‘Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”ĖÓ”¼Ó”┐Ó”¤Ó”ŠÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”© Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ć Ó”¼Ó¦ćÓ¦£Ó¦ć Ó”ēÓ”ĀÓ¦ćÓ”øÓ”┐Óźż Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”¼Ó¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”▓Ó”ŠÓ”ćÓ”©Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”«Ó¦üÓ”¢Ó”ĖÓ¦ŹÓ”ź Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ”ŠÓ”« Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”ĢÓ”ŠÓ¦ćÓ”░Ó”åÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”ÜÓ¦ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”¼Ó¦ćÓ”▓Ó¦ćÓ”░ Ó”©Ó”┐Ó”ē Ó”¤Ó¦ćÓ”ĖÓ¦ŹÓ”¤Ó”ŠÓ”«Ó¦ćÓ”©Ó¦ŹÓ”¤ Ó”ŁÓ”ŠÓ”▓Ó”ŠÓ¦ć Ó”£Ó”ŠÓ”©Ó”żÓ”ŠÓ”«Óźż’ Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”åÓ”░Ó¦ŗ Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”©, ‘Ó”ĢÓ”ŠÓ¦ćÓ”░Ó”åÓ”© Ó”¬Ó¦£Ó”żÓ¦ć Ó””Ó¦üÓ”░Ó¦éÓ”╣ Ó”▓Ó”ŠÓ”ŚÓ¦ćÓźż’
Ó”»Ó”ŠÓ”░Ó”Š Ó””Ó¦üÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”¼Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”Ś Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”¢Ó¦ŗÓ””Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”Ģ Ó”ŚÓ¦£Ó”żÓ¦ć Ó”ÜÓ”ŠÓ”© Ó”ō Ó”åÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”┐Ó”Ģ Ó”ÜÓ”░Ó¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ¦¤ Ó”©Ó”┐Ó”£Ó¦ćÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”▓Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó””Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”ÜÓ”ŠÓ”© ŌĆśÓ”«Ó”ĖÓ”©Ó”¼Ó”┐ŌĆÖ Ó”żÓ”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”źÓ”Š Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓźż┬ĀÓ”ÅÓ”ĖÓ”¼ Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”ŻÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”ō Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó”ĢÓ¦ć Ó”åÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć
Ó”»Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”░Ó”ŠÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”░ Ó”▓Ó”ŠÓ”¢ Ó”▓Ó”ŠÓ”¢ Ó”¬Ó”ŠÓ”ĀÓ”ĢÓ¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”¬Ó”░Ó”┐Ó”ÜÓ¦¤ Ó”ĢÓ”░Ó”ŠÓ”©Ó¦ŗÓ”░ Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ¦ćÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó¦ć Ó”ōÓ”«Ó”┐Ó”” Ó”ĖÓ”ŠÓ”½Ó”┐Ó”ō Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”»Ó””Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”żÓ¦ŗ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ģÓ”¼Ó””Ó”ŠÓ”© Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ĆÓ”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”© Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”╣Ó”ŠÓ”£Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”Ė Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”░ Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”© Ó”ō Ó”ĢÓ”ŠÓ”£Ó¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐ Ó”»Ó”źÓ¦ćÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤ Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó””Ó”░Ó”” Ó””Ó¦ćÓ”¢Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”ÅÓ”øÓ”ŠÓ¦£Ó”Š Ó”¼Ó”ŠÓ”£Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”åÓ”░Ó¦ŗ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ”” Ó”░Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”»Ó¦ćÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”åÓ”ĖÓ”▓Ó¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”ĢÓ¦ćÓ”ć Ó”¼Ó”ŠÓ”” Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”»Ó¦ćÓ”«Ó”©- Ó””Ó”┐Ó”¬Ó”Ģ Ó”ÜÓ¦ŗÓ”¬Ó”░Ó”Š Ó”ō Ó”ĪÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”▓ Ó”▓Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĪÓ”┐Ó”©Ó”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ”┐ Ó”ģÓ”©Ó¦éÓ””Ó”┐Ó”ż ‘Ó”©Ó”┐Ó”ē Ó”ÅÓ”ćÓ”£ Ó”¼Ó¦üÓ”ĢÓ”Ė’Óźż Ó”ÅÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”©Ó”ŠÓ”«Ó¦ćÓ”ć Ó”¼Ó”ŠÓ”£Ó”ŠÓ”░Ó¦ć Ó”øÓ”ŠÓ¦£Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”¼Ó”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”░Ó”┐Ó”ō Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ć Ó”ÅÓ”żÓ¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”½Ó”▓Ó”┐Ó”ż Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ÜÓ¦ŗÓ”¬Ó”░Ó”Š Ó”åÓ”ĖÓ”▓Ó¦ć Ó”åÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”┐Ó”Ģ Ó”©Ó”ŠÓ”©Ó”ŠÓ”© Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó¦ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”åÓ”ĖÓ”▓Ó¦ć Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”░Ó”ŠÓ”£Óźż Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”ĖÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ĆÓ”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”ō Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”©, Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ČÓ”ŠÓ”¼Ó¦ŹÓ””Ó”┐Ó”Ģ Ó”░Ó¦éÓ”¬Ó”ŠÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”░ Ó”©Ó¦¤Óźż ‘Ó””Ó”┐ Ó”▓Ó”ŠÓ”Ł Ó”¬Ó¦¤Ó¦ćÓ”«Ó”Ė Ó”ģÓ”½ Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐’ Ó”¼Ó”ćÓ¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”ŁÓ¦éÓ”«Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ¦¤ Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©, ”Ó”ÅÓ”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”╣Ó”▓Ó¦ŗ Ó”åÓ”«Ó”░Ó”Š Ó”«Ó¦éÓ”▓ Ó”½Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖÓ”┐ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”┐Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦üÓ”░Ó”┐Ó”ż ‘Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼’Ó”¤Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”ćÓ”éÓ”░Ó¦ćÓ”£Ó”┐Ó”░ Ó”ČÓ”¼Ó¦ŹÓ””Ó¦ć Ó”¦Ó”░Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”© Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ”┐Óźż Ó”żÓ”¼Ó¦ć Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ēÓ¦ÄÓ”ĖÓ”«Ó¦éÓ”▓ Ó”¼Ó”£Ó”ŠÓ¦¤ Ó”░Ó”ŠÓ”¢Ó”ŠÓ”░ Ó”ÜÓ¦ćÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”ŠÓ”ō Ó”øÓ”┐Ó”▓Óźż”
ŌĆśÓ”©Ó”┐Ó”ē Ó”ÅÓ”ćÓ”£ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””ŌĆÖ Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”åÓ”▓Ó¦ŗÓ”ÜÓ”©Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”ŚÓ”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ōÓ”«Ó”┐Ó”” Ó”ĖÓ”ŠÓ”½Ó”┐ Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©, ”Ó””Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ”┐Ó”Ż Ó”ō Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”» Ó”ÅÓ”ČÓ”┐Ó¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”ĖÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó”Š Ó”ō Ó”ćÓ”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”ŠÓ”©Ó”¼Ó¦üÓ”▓ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó”┐Ó¦¤Ó”Š Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”ćÓ”░Ó”ŠÓ”©Ó”£Ó¦üÓ¦£Ó¦ć Ó”«Ó¦üÓ”ĖÓ”▓Ó”┐Ó”« Ó”£Ó¦ĆÓ”¼Ó”©Ó”¦Ó”ŠÓ”░Ó”ŠÓ¦¤ Ó”»Ó¦ć Ó”åÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”┐Ó”Ģ Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”ÜÓ”░Ó”Ż Ó”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”ÅÓ¦£Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ŚÓ”┐Ó¦¤Ó¦ć, Ó”«Ó¦üÓ”øÓ¦ć Ó”½Ó¦ćÓ”▓Ó¦ć Ó”ō Ó”øÓ”┐Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ōÓ”ć Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£Ó”¤Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”ÅÓ”Ģ Ó”¦Ó”░Ó”©Ó¦ćÓ”░ ŌĆśÓ”åÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”┐Ó”Ģ Ó”ēÓ”¬Ó”©Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ”¼Ó”ŠÓ””ŌĆÖ-Ó”ÅÓ”░ Ó”ÜÓ”░Ó¦ŹÓ”ÜÓ”Š Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż” Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”ĢÓ”©Ó”¤Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĖÓ”¤ Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”åÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”┐Ó”ĢÓ”żÓ”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”åÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó”ŠÓ”░ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”ŚÓ”ŁÓ¦ĆÓ”░ Ó”żÓ”ŠÓ¦ÄÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”»Ó”¬Ó¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”Ż Ó”ćÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ”┐Ó”ż Ó”░Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ĪÓ¦ŗÓ”©Ó”ŠÓ”▓Ó¦ŹÓ”Ī Ó”¤Ó¦ŹÓ”░Ó”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó¦ćÓ”░ (Ó”ĖÓ””Ó¦ŹÓ”» Ó”¼Ó”┐Ó””Ó”ŠÓ¦¤Ó¦Ć) Ó”©Ó”┐Ó”░Ó”ŠÓ”¬Ó”żÓ¦ŹÓ”żÓ”Š Ó”ēÓ”¬Ó””Ó¦ćÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”Š┬ĀÓ”£Ó¦ćÓ”©Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”▓ Ó”«Ó”ŠÓ”ćÓ”ĢÓ¦ćÓ”▓ Ó”½Ó¦ŹÓ”▓Ó”┐Ó”©-Ó”ÅÓ”░ Ó”«Ó”żÓ¦ŗ Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ćÓ”ć Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó”ĢÓ¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó”ż ‘Ó”ĢÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”©Ó”ĖÓ”ŠÓ”░’ Ó”╣Ó”┐Ó”ĖÓ¦ćÓ”¼Ó¦ćÓ”ć Ó”åÓ”¢Ó¦ŹÓ”»Ó”Š Ó””Ó”┐Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”ÅÓ”«Ó”©Ó”ĢÓ”┐┬ĀÓ”©Ó¦ĆÓ”żÓ”┐-Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ”¦Ó”ŠÓ”░Ó”ĢÓ”░Ó”Š┬ĀÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”»Ó”©Ó¦ŹÓ”ż Ó”¼Ó”▓Ó”øÓ¦ćÓ”©, Ó”ģÓ”¬Ó”ČÓ¦ŹÓ”ÜÓ”┐Ó”«Ó”┐ Ó”ō Ó”ģÓ”ČÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”żÓ”ŠÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ”░Ó”Š Ó”ĖÓ”ŁÓ¦ŹÓ”»Ó”żÓ”ŠÓ¦¤ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó”ŠÓ¦ć Ó”ģÓ”¼Ó””Ó”ŠÓ”©Ó”ć Ó”░Ó”ŠÓ”¢Ó”©Ó¦ćÓ”©Ó”┐Óźż

Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”åÓ”ĖÓ”▓ Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ¦ćÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó¦ć Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó”ĢÓ¦ć Ó”ŚÓ¦īÓ”Ż Ó”«Ó”©Ó¦ć Ó”ĢÓ”░Ó”øÓ¦ćÓ”© Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”ĖÓźż Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”¼Ó”▓Ó”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”©, ‘Ó”ŚÓ¦ŗÓ”¤Ó”Š Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”£Ó”©Ó¦ŹÓ”»Ó”ć Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”« Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”¼Ó”┐Ó”żÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”┐Ó”ż Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Óźż Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”żÓ¦ŹÓ”» Ó”¬Ó¦ćÓ¦¤Ó¦ćÓ”øÓ”┐ Ó”åÓ”░ Ó”åÓ”¬Ó”©Ó”┐ Ó”åÓ”¬Ó”©Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”żÓ¦ŹÓ”» Ó”¬Ó¦ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”ŚÓ¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©- Ó”ÅÓ”¤Ó”┐ Ó”ÅÓ”ĢÓ””Ó”« Ó”ģÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¼Ó”ĖÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĪÓźż Ó”åÓ”«Ó”░Ó”Š Ó”ĖÓ”¼Ó”ŠÓ”ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”żÓ¦ŹÓ”░Ó¦ć Ó”ÅÓ”ć Ó”¬Ó¦āÓ”źÓ”┐Ó”¼Ó¦ĆÓ”żÓ¦ć Ó”¼Ó”┐Ó”░Ó”ŠÓ”£ Ó”ĢÓ”░Ó”øÓ”┐ Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”åÓ”«Ó”┐ Ó”åÓ”«Ó”ŠÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ”░Ó”ĢÓ¦ć Ó”«Ó¦üÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ż Ó”ĢÓ”░Ó”¼Ó”ŠÓ”░ Ó”ÜÓ¦ćÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó”øÓ”┐ Ó”åÓ”░ Ó”ÅÓ”żÓ¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”Š Ó”ģÓ”ŠÓ”«Ó”ŠÓ”ĢÓ¦ć Ó”ĖÓ”ŠÓ”╣Ó”ŠÓ”»Ó¦ŹÓ”» Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓźż’ Ó”ÅÓ”¤Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”ĖÓ”░Ó”ŻÓ”ō Ó”¼Ó”▓Ó”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤ Ó”ÅÓ”Ģ Ó”ģÓ”░Ó¦ŹÓ”źÓ¦ć, Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”»Ó¦ćÓ”«Ó”© Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ¦¤ Ó”ĢÓ”ŠÓ¦ćÓ”░Ó”åÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ¦¤Ó”ŠÓ”ż Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”£Ó”ŠÓ¦¤Ó”ŚÓ”ŠÓ¦¤ Ó”żÓ”Š Ó”╣Ó¦üÓ”¼Ó”╣Ó¦ü Ó”©Ó”Š Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”©Ó”┐Ó”£Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”żÓ¦ŗ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”ÅÓ”©Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©- Ó”½Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖÓ”┐Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó¦£Ó”żÓ¦ć Ó”ŚÓ”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”ĖÓ”╣Ó”£Ó¦ć Ó”¦Ó”░Ó”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤Óźż Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”½Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĖÓ”┐ Ó”¬Ó”ŠÓ”ĀÓ”ĢÓ”░Ó”Š Ó”ōÓ”ć Ó”ĢÓ¦īÓ”ČÓ”▓Ó”¤Ó”Š Ó”ĖÓ”╣Ó”£Ó¦ćÓ”ć Ó”¦Ó”░Ó”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó”▓Ó¦ćÓ”ō Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”© Ó”¬Ó”ŠÓ”ĀÓ”ĢÓ”░Ó”Š Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó”┐ Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó”ŠÓ””Ó”┐Ó”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”¬Ó”░Ó”┐Ó”ÜÓ”┐Ó”ż Ó”©Ó”©Óźż Ó”ōÓ”«Ó”┐Ó”” Ó”ĖÓ”ŠÓ”½Ó”┐ Ó”ĢÓ”ŠÓ¦ćÓ”░Ó”åÓ”© Ó”©Ó”Š Ó”¬Ó”ŠÓ”Ā Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”¬Ó”ŠÓ”ĀÓ”ĢÓ¦ć Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”¼Ó¦ćÓ”▓ Ó”©Ó”Š Ó”¬Ó¦£Ó¦ćÓ”ć Ó”«Ó”┐Ó”▓Ó¦ŹÓ”¤Ó”© Ó”¬Ó¦£Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”żÓ¦üÓ”▓Ó”©Ó”Š Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”»Ó””Ó”┐Ó”ō Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ÜÓ”▓Ó”┐Ó”ż Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó”«Ó”żÓ¦ćÓ”░ Ó”©Ó”ŠÓ”©Ó”ŠÓ”© Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó¦ć Ó”ĖÓ”©Ó¦ŹÓ””Ó”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”© Ó”øÓ”┐Ó”▓Ó¦ćÓ”© Ó”żÓ”¼Ó¦üÓ”ō Ó”ĖÓ¦ćÓ”¤Ó”┐ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”«Ó¦üÓ”ĖÓ”▓Ó”┐Ó”« Ó”ĢÓ”©Ó”¤Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĖÓ”¤Ó¦ć Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ČÓ¦ŹÓ”© Ó”żÓ¦üÓ”▓Ó”żÓ¦ćÓ”©, Ó”ōÓ”ć Ó”ĖÓ”«Ó¦¤Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó”┐ Ó”ĖÓ”éÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ¦āÓ”żÓ”┐ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”»Ó”ŠÓ¦¤Ó¦Ć ӔŠӔ¦Ó”░Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”żÓ”¼Ó”┐Ó”░Ó¦ŗÓ”¦Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”»Ó”źÓ¦ćÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤ Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”Ż Ó”ō Ó”ĖÓ¦üÓ”»Ó¦ŗÓ”Ś Ó”øÓ”┐Ó”▓Óźż Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£ Ó”»Ó¦ć Ó”ČÓ¦üÓ”¦Ó¦ü Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”╣Ó”ŠÓ”ż Ó”¦Ó”░Ó”ŠÓ”¦Ó”░Ó”┐ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó”©Ó”┐Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó”┐Ó”ż Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ”┐Ó”▓ Ó”ĖÓ¦ćÓ”¤Ó”┐Ó”ć Ó”©Ó¦¤, Ó”ÅÓ”¤Ó”┐ Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó”┐ Ó”¬Ó”ŠÓ”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”ÉÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”Ģ Ó”ēÓ¦ÄÓ”ĢÓ”░Ó¦ŹÓ”ĘÓ¦ćÓ”░Ó”ō Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”©Ó”┐Ó”¦Ó”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”¼ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓźż
Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”ĢÓ”ŠÓ¦ćÓ”░Ó”åÓ”© Ó”ō Ó”╣Ó”ŠÓ””Ó”┐Ó”Ė Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¢Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”░ Ó”ŁÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ”┐Ó”żÓ¦ć Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”Ģ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ÜÓ”▓Ó”┐Ó”ż Ó”¬Ó”ĀÓ”©-Ó”¬Ó”ŠÓ”ĀÓ”©Ó¦ćÓ”░ Ó”¼Ó”┐Ó”░Ó¦üÓ””Ó¦ŹÓ”¦Ó¦ć Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”ČÓ¦ŹÓ”© Ó”żÓ¦üÓ”▓Ó”żÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”ĢÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”£Ó”©Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”┐Ó¦¤ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó”ŚÓ¦üÓ”▓Ó¦ŗÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć,┬ĀOut beyond ideas of rightdoing and wrongdoing, there is a field./I will meet you there. Ó”ģÓ”źÓ”Ü Ó”«Ó¦éÓ”▓ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ¦¤ rightdoing Ó”ģÓ”źÓ”¼Ó”Š wrongdoing Ó”ĢÓ¦ŗÓ”źÓ”ŠÓ”ō Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó¦āÓ”ż Ó”╣Ó¦¤Ó”©Ó”┐Óźż Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”»Ó¦ć Ó”ČÓ”¼Ó¦ŹÓ”” Ó””Ó¦üÓ”¤Ó”┐ Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”żÓ”Š Ó”╣Ó”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ¦ć Ó”ćÓ”«Ó”ŠÓ”© (religion) Ó”ō Ó”ĢÓ¦üÓ”½Ó”░ (infidelity)Óźż Ó”ÅÓ”¼Ó”ŠÓ”░ Ó”ÜÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ”Š Ó”ĢÓ”░Ó¦üÓ”©, Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”¬Ó”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ”┐Ó”ż Ó”ÅÓ”Ģ Ó”¼Ó”▓Ó”øÓ¦ćÓ”©, Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ŁÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”żÓ”┐ Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”åÓ”ÜÓ”ŠÓ”░Ó”¼Ó”┐Ó”¦Ó”┐Ó”żÓ¦ć Ó”ĖÓ¦ŹÓ”źÓ”ŠÓ”¬Ó”┐Ó”ż Ó”©Ó¦¤, Ó”¼Ó”░Ó”é Ó”ĖÓ¦ćÓ”¤Ó”┐ Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”«Ó”ōÓ”┐ Ó”ĖÓ”«Ó”¼Ó¦ćÓ””Ó”©Ó”ŠÓ”░ Ó”ēÓ”ÜÓ¦ŹÓ”Ü Ó”«Ó”ŠÓ”ĢÓ”ŠÓ”«Ó¦ć Ó”ģÓ”¦Ó”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”┐Ó”żÓźż
Ó”ÅÓ”¢Ó”©Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó””Ó”┐Ó”©Ó¦ć Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó”ŠÓ¦ć Ó”«Ó¦üÓ”ĖÓ”▓Ó”┐Ó”« Ó”¬Ó”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ”┐Ó”ż Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ĢÓ¦ŹÓ”żÓ”┐ Ó”¼Ó”Š Ó”ćÓ”«Ó”ŠÓ”«Ó”ĢÓ¦ć Ó”»Ó¦ć Ó”ģÓ”¼Ó”ĖÓ¦ŹÓ”źÓ”ŠÓ”© Ó”©Ó¦ćÓ¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó”ŻÓ¦ć Ó”åÓ”«Ó”░Ó”Š Ó”ēÓ”ŚÓ¦ŹÓ”░Ó”¬Ó”©Ó¦ŹÓ”źÓ¦Ć (Ó”░ŌĆīÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ĪÓ”┐Ó”ĢÓ¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”▓) Ó”¼Ó”▓Ó”┐, Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”żÓ¦ćÓ”«Ó”©Ó”ć Ó”ģÓ”¼Ó”ĖÓ¦ŹÓ”źÓ”ŠÓ”© Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó¦ŁÓ¦”Ó¦” Ó”¼Ó”øÓ”░Ó¦ćÓ”░Ó”ō Ó”¼Ó¦ćÓ”ČÓ”┐ Ó”ĖÓ”«Ó¦¤ Ó”åÓ”ŚÓ¦ćÓźż
Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”¬Ó”ŠÓ”Ā Ó”»Ó¦ć, Ó”ÅÓ”░ Ó”åÓ”ŚÓ¦ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¼Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”ć Ó”øÓ”┐Ó”▓ Ó”©Ó”Š Ó”żÓ”Š Ó”©Ó¦¤Óźż Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”¦Ó”░Ó¦ŹÓ”«Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”åÓ”¦Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ŹÓ”«Ó”┐Ó”ĢÓ”żÓ”Š Ó”ō Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ”┐Ó”ĘÓ¦ŹÓ”ĀÓ”┐Ó”ż Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”ŁÓ”ŠÓ”░Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó¦ŹÓ”»Ó”¬Ó¦éÓ”░Ó¦ŹÓ”Ż Ó”ōÓ”żÓ”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦ŗÓ”ż Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”¬Ó”░Ó¦ŹÓ”Ģ Ó”░Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ÅÓ”ĢÓ”ć Ó”ĖÓ”ÖÓ¦ŹÓ”ŚÓ¦ć Ó”¼Ó¦üÓ””Ó¦ŹÓ”¦Ó”┐Ó””Ó¦ĆÓ”¬Ó¦ŹÓ”żÓ”żÓ”ŠÓ”░ Ó”╣Ó”ŠÓ”£Ó”┐Ó”░Ó”Š Ó”åÓ”øÓ¦ć Ó”»Ó”Š Ó”ģÓ”©Ó¦ŹÓ”» Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Ó¦ŗ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”«Ó¦ćÓ”▓Ó¦ć Ó”©Ó”ŠÓźż Ó”ĖÓ”ŠÓ”½Ó”┐ Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©, ‘Ó”ÉÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”ĖÓ”┐Ó”Ģ Ó”¼Ó”┐Ó”¼Ó¦ćÓ”ÜÓ”©Ó”Š Ó”«Ó”ŠÓ”źÓ”ŠÓ¦¤ Ó”░Ó¦ćÓ”¢Ó¦ć Ó”¼Ó”▓Ó”Š Ó”»Ó”ŠÓ¦¤, Ó”╣Ó”ŠÓ”½Ó”┐Ó”£ Ó”ō Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”¼Ó¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó”żÓ¦ŗ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó”ŠÓ¦ć Ó”«Ó¦üÓ”ĖÓ”▓Ó”«Ó”ŠÓ”© Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”░ Ó”¬Ó”ĢÓ¦ŹÓ”ĘÓ¦ćÓ”ć Ó”ĢÓ”ŠÓ¦ćÓ”░Ó”åÓ”© Ó”¼Ó”ŠÓ”” Ó””Ó”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó”ÅÓ”«Ó”© Ó”ÜÓ”┐Ó”żÓ¦ŹÓ”░Ó”ĢÓ”▓Ó¦ŹÓ”¬ Ó”¼Ó”ŠÓ”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”¼Ó¦ć Ó”░Ó¦éÓ”¬ Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š Ó”ĖÓ”«Ó¦ŹÓ”ŁÓ”¼ Ó”╣Ó¦¤Ó”©Ó”┐Óźż ӔŠӔĢÓ”ŠÓ”░Ó”ŻÓ¦ćÓ”ć Ó”╣Ó”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”░ Ó”ōÓ”ć Ó”ĖÓ”«Ó¦¤Ó¦ćÓ”░ Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”ō Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”ÅÓ”ż Ó”¼Ó”┐Ó”ĖÓ¦ŹÓ”żÓ”░ Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”┐ Ó”¤Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”ŚÓ¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż
Ó”▓Ó¦ćÓ”¢Ó”Ģ Ó”ō Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó”Ģ Ó”ĖÓ”┐Ó”©Ó”ŠÓ”© Ó”åÓ”©Ó”żÓ¦üÓ”© Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©,┬Ā‘Ó”ŁÓ”ŠÓ”ĘÓ”Š Ó”ČÓ¦üÓ”¦Ó¦ü Ó”»Ó¦ŗÓ”ŚÓ”ŠÓ”»Ó¦ŗÓ”ŚÓ¦ćÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”ēÓ”¬Ó”ŠÓ¦¤ Ó”©Ó¦¤Óźż Ó”ÅÓ”¤Ó”┐ Ó”åÓ”ĖÓ”▓Ó¦ć Ó”ĖÓ¦ŹÓ”«Ó¦āÓ”żÓ”┐, Ó”ÉÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó¦ŹÓ”», Ó”ĖÓ”éÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ¦āÓ”żÓ”┐ Ó”ō Ó”ģÓ”ŁÓ”┐Ó”£Ó¦ŹÓ”×Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”Š Ó”ŁÓ”ŠÓ”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ”ŠÓ”░Óźż’ Ó”»Ó”¢Ó”© Ó””Ó¦üÓ”¤Ó”┐ Ó”ĖÓ”éÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ¦āÓ”żÓ”┐Ó”░ Ó”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”¼Ó”┐Ó”©Ó”┐Ó”«Ó¦¤ Ó”śÓ”¤Ó¦ć Ó”żÓ”¢Ó”© Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó”ĢÓ”░Ó”Š Ó”ĖÓ¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”©Ó¦ć Ó”ģÓ”¼Ó”ČÓ¦ŹÓ”»Ó”ć Ó”ÅÓ”ĢÓ”¤Ó”┐ Ó”░Ó”ŠÓ”£Ó”©Ó¦łÓ”żÓ”┐Ó”Ģ Ó”£Ó”ŠÓ¦¤Ó”ŚÓ”Š Ó”źÓ¦ćÓ”ĢÓ¦ć Ó”ĢÓ”ŠÓ”£ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”©Óźż Ó”żÓ”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”¢Ó¦üÓ”üÓ”£Ó¦ć Ó”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó”żÓ¦ć Ó”╣Ó¦¤ Ó”ĢÓ¦ĆÓ”ŁÓ”ŠÓ”¼Ó¦ć Ó”żÓ¦ŹÓ”░Ó¦¤Ó¦ŗÓ””Ó”Č Ó”ČÓ”żÓ”ŠÓ”¼Ó¦ŹÓ””Ó¦ĆÓ”░ Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó”ĖÓ¦ŹÓ”» Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”ĢÓ¦ć Ó”ĖÓ”«Ó”ĖÓ”ŠÓ”«Ó¦¤Ó”┐Ó”Ģ Ó”åÓ”«Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”¬Ó”ŠÓ”ĀÓ”ĢÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”øÓ¦ć Ó”żÓ¦üÓ”▓Ó¦ć Ó”¦Ó”░Ó”Š Ó””Ó”░Ó”ĢÓ”ŠÓ”░Óźż Ó”ĢÓ”┐Ó”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ü Ó”żÓ”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”ŠÓ”£Ó”¤Ó”┐Ó”░ Ó”«Ó¦īÓ”▓Ó”┐Ó”Ģ Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼ Ó”¼Ó”£Ó”ŠÓ¦¤ Ó”░Ó”ŠÓ”¢Ó”ŠÓ”░ Ó””Ó”ŠÓ¦¤Ó”¤Ó”ŠÓ”ō Ó”©Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š Ó”ēÓ”ÜÓ”┐Ó”ż Ó”øÓ”┐Ó”▓ Ó”»Ó”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”ĀÓ”ĢÓ”░Ó”Š Ó”¼Ó¦üÓ”ØÓ”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”© Ó”ČÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó”Š Ó”¼Ó”┐Ó”ĘÓ¦¤Ó”Ģ Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”¬Ó”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ”┐Ó”ż Ó”¼Ó”┐Ó”ČÓ¦ŹÓ”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ”¼Ó”ÜÓ¦ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”¼Ó”╣Ó¦üÓ”▓ Ó”¬Ó”ĀÓ”┐Ó”ż Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦ćÓ”«Ó¦ćÓ”░ Ó”ĢÓ”¼Ó”┐Ó”żÓ”ŠÓ”ō Ó”▓Ó”┐Ó”¢Ó¦ć Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓ”©Óźż
Ó”£Ó”ŠÓ”ŁÓ”┐Ó”” Ó”«Ó¦ŗÓ”£Ó”ŠÓ””Ó¦ŹÓ””Ó¦ćÓ””Ó”┐ Ó”«Ó”ĖÓ”©Ó”¼Ó”┐Ó”░ Ó¦¼Ó”¤Ó”┐ Ó”¢Ó”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ¦ćÓ”░ Ó”¬Ó¦üÓ”░Ó¦ŗÓ”¤Ó”Š Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”ĖÓ¦üÓ””Ó¦ĆÓ”░Ó¦ŹÓ”ś Ó”ĢÓ”ŠÓ”£ Ó”╣Ó”ŠÓ”żÓ¦ć Ó”©Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©Óźż Ó”ÅÓ”░┬ĀÓ¦®Ó”¤Ó”┐┬ĀÓ”¢Ó”ŻÓ¦ŹÓ”Ī┬ĀÓ”ćÓ”żÓ¦ŗÓ”«Ó”¦Ó¦ŹÓ”»Ó¦ć Ó”¼Ó¦ćÓ”░Ó”┐Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ÜÓ”żÓ¦üÓ”░Ó¦ŹÓ”ź Ó”¢Ó”ŻÓ¦ŹÓ”ĪÓ”ō ӔŠӔ¼Ó”ĖÓ”©Ó¦ŹÓ”żÓ¦ćÓ”ć Ó”¼Ó¦ćÓ”░ Ó”╣Ó”ōÓ¦¤Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”źÓ”ŠÓźż Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐Ó”░ Ó”«Ó¦éÓ”▓ Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼ Ó”░Ó”ŠÓ”¢Ó”ŠÓ”░ Ó”ĖÓ”░Ó¦ŹÓ”¼Ó¦ŗÓ”ÜÓ¦ŹÓ”Ü Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó¦¤Ó”ŠÓ”Ė Ó””Ó¦ćÓ”¢Ó”Š Ó”ŚÓ¦ćÓ”øÓ¦ć Ó”»Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”©Ó¦ć Ó”░Ó¦üÓ”«Ó”┐ Ó”ćÓ”ĖÓ”▓Ó”ŠÓ”«Ó”┐ Ó”ō Ó”ĢÓ”ŠÓ¦ćÓ”░Ó”åÓ”©Ó¦ĆÓ¦¤ Ó”¤Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ŹÓ”ĖÓ”¤ Ó”¼Ó”Š Ó”åÓ”░Ó”¼Ó”┐ Ó”ČÓ”¼Ó¦ŹÓ”” Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”¼Ó”╣Ó”ŠÓ”░ Ó”ĢÓ”░Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”© Ó”ĖÓ¦ćÓ”¤Ó”┐ Ó”ÜÓ”┐Ó”╣Ó¦ŹÓ”©Ó”┐Ó”ż Ó”░Ó”ŠÓ”¢Ó”żÓ¦ć Ó”åÓ”ćÓ”¤Ó”ŠÓ”▓Ó”┐Ó”Ģ Ó”ĢÓ”░Ó¦ć Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”żÓ”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”ćÓ¦¤Ó¦ć Ó”ģÓ”©Ó¦ćÓ”Ģ Ó”¤Ó”┐Ó”ĢÓ”Š-Ó”¼Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”¢Ó¦ŹÓ”»Ó”ŠÓ”ō Ó”£Ó¦üÓ¦£Ó¦ć Ó””Ó¦ćÓ¦¤Ó”Š Ó”╣Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ÅÓ”¤Ó”┐ Ó”¬Ó¦£Ó”żÓ¦ć Ó”╣Ó”▓Ó¦ć Ó”¼Ó¦ćÓ”Č Ó”«Ó¦ćÓ”╣Ó”©Ó”żÓ¦ćÓ”░ Ó””Ó”░Ó”ĢÓ”ŠÓ”░ Ó”╣Ó”¼Ó¦ć Ó”ÅÓ”¼Ó”é Ó”ÅÓ”ĢÓ”£Ó”©Ó¦ćÓ”░ Ó”åÓ”░Ó¦ŗÓ”¬Ó”┐Ó”ż Ó”¦Ó”ŠÓ”░Ó”ŻÓ”ŠÓ”░ Ó”¼Ó”ŠÓ”ćÓ”░Ó¦ć Ó”ŚÓ”┐Ó¦¤Ó¦ć Ó””Ó¦ćÓ”¢Ó”ŠÓ”░ Ó”ćÓ”ÜÓ¦ŹÓ”øÓ”ŠÓ”¤Ó”ŠÓ”ō Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ”żÓ¦ć Ó”╣Ó”¼Ó¦ćÓźż Ó”åÓ”░ Ó”ŁÓ”┐Ó”©Ó””Ó¦ćÓ”ČÓ”┐ Ó”ĢÓ”┐Ó”øÓ¦ü Ó”¼Ó”ŠÓ¦ćÓ”ØÓ”ŠÓ”░ Ó”ÜÓ¦ćÓ”ĘÓ¦ŹÓ”¤Ó”ŠÓ”¤Ó”ŠÓ”ć Ó”ģÓ”©Ó¦üÓ”¼Ó”ŠÓ””Ó¦ćÓ”░ Ó”«Ó¦éÓ”▓ Ó”£Ó”ŠÓ¦¤Ó”ŚÓ”ŠÓźż Ó”ĢÓ¦ćÓ”ĖÓ”ŠÓ”ŁÓ”ŠÓ”░Ó¦ŹÓ”£ Ó”»Ó¦ćÓ”«Ó”©Ó”¤Ó”┐ Ó”¼Ó”▓Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓ”©, ‘Ó”¬Ó¦ŹÓ”░Ó”żÓ¦ŹÓ”»Ó¦ćÓ”ĢÓ¦ćÓ”░Ó”ć Ó”åÓ”▓Ó”ŠÓ””Ó”Š Ó”¦Ó”©Ó¦ć Ó”ō Ó”ŁÓ”ŠÓ”¼ Ó”░Ó¦¤Ó¦ćÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ĖÓ”¼Ó”ŠÓ”░Ó”ć Ó”ĖÓ”éÓ”ĖÓ¦ŹÓ”ĢÓ¦āÓ”żÓ”┐ Ó”ō Ó”ćÓ”żÓ”┐Ó”╣Ó”ŠÓ”Ė Ó”åÓ”øÓ¦ćÓźż Ó”ĢÓ¦ŗÓ”©Ó¦ŗ Ó”«Ó¦üÓ”ĖÓ”▓Ó”«Ó”ŠÓ”©Ó¦ćÓ”░Ó”ō Ó”żÓ¦ćÓ”«Ó”©Ó”¤Ó”┐ Ó”źÓ”ŠÓ”ĢÓ”żÓ¦ć Ó”¬Ó”ŠÓ”░Ó¦ćÓźż